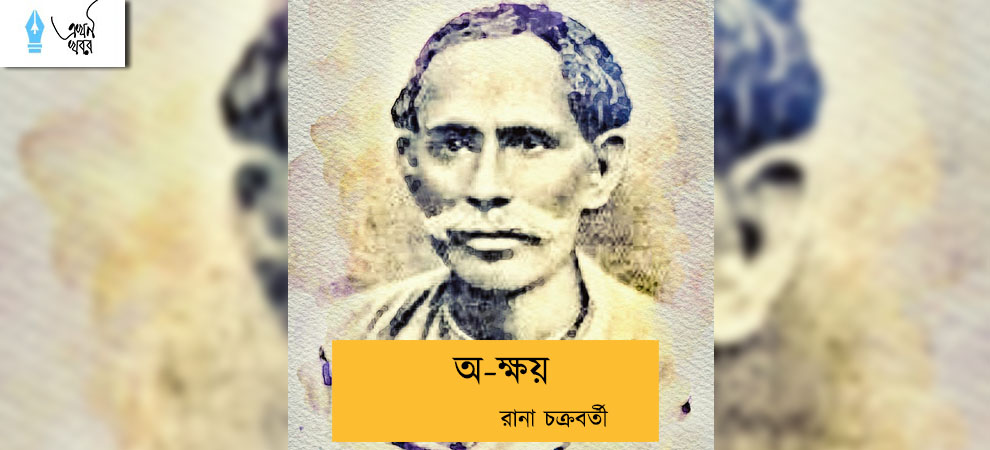তিনি ঈশ্বরের দর কষতেন বীজগণিত দিয়ে
বিজ্ঞানমনস্ক মানুষটি তৈরি করেছিলেন অজস্র বাংলা পরিভাষা। ধর্মান্ধতার সঙ্গে আপস করেননি কখনও। পুরাতত্ত্ব থেকে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে ভাষাতত্ত্ব, বহুসংস্কৃতির পুরোধা ছিলেন তিনি।
‘খগোল-যন্ত্র’ হল দূরবিন। পারিভাষিক শব্দ দূরবীক্ষণ। এই নামটি দিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোলের ক্ষেত্রে আরও অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ তৈরি করেছিলেন তিনি। যেমন, অণুবীক্ষণ, চুম্বক, জ্যোতির্বিদ্যা, দাহ্য পদার্থ, জড়, তড়িৎ, পরিমিতি, ধ্রুবতারা, অঙ্গার, বাষ্প, বজ্র, জোয়ার, রামধনু, সৌরজগৎ, মাধ্যাকর্ষণ, গ্রহণ, সুমেরু, কুমেরু, মানমন্দির, জ্বালামুখী, আগ্নেয়গিরি। এগুলি নমুনা মাত্র। তালিকাটি দীর্ঘ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে পথ দেখিয়েছিল এই পরিভাষা।

চিনি, ময়দা, সুতার কল, কাগজের কল, টাঁকশালে যেতেন অক্ষয়কুমার, যন্ত্রবিজ্ঞান কী ভাবে কাজ করে দেখবেন বলে। সমুদ্রভ্রমণে গিয়ে দূরবিন চোখে পৃথিবীর গোলাকৃতির পরীক্ষা করতেন, জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলোচনা করতেন নানা দেশ নিয়ে। ইচ্ছে করে বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি, অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতি ‘অশুভ’ দিনক্ষণ দেখে ভ্রমণে বেরোতেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ‘পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা’র শরিক হতেন। বাংলা ও ইংরেজি ছাড়াও জানতেন সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু, ফরাসি ভাষা। বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চা ছাড়াও গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, নৃবিজ্ঞান, বিবর্তনতত্ত্ব, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ভারতের পুরাতত্ত্বের চর্চা করেছিলেন।
অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম ১৮২০-র ১৫ই জুলাই। বিদ্যাসাগরের দু’মাস আগে। এবছর তাঁর জন্মের দ্বিশততম বর্ষ। বাঙালি তাঁকে খুব যে মনে রেখেছে, বলা যাবে না। অবশ্য ঘটা করে প্রতি বছর তাঁর ছবিতে ফুলচন্দন দিলে বা পঞ্চধাতুর মূর্তি স্থাপন করলেও খুব কিছু এসে যেত না।
প্রকৃতপক্ষে অক্ষয়কুমার দত্তই ছিলেন বাংলায় বিজ্ঞান সংস্কৃতি গড়ে তোলার মূল কান্ডারি। ১৮৪০ সালের জানুয়ারি মাসে, তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক রূপে নির্বাচিত অক্ষয়কুমার, উক্ত বছরেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। এখানেই তিনি ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা পড়ানোর সময়ে বাংলা ভাষায় ‘ভূগোল’ ও ‘পদার্থবিদ্যা’ নামে দু’টি পাঠ্যপুস্তক লিখে ফেলেন।
১৮৪১ সালে তাঁর লিখিত এই ‘ভূগোল’ই ছিল বাংলায় লেখা প্রথম বিজ্ঞান সম্পর্কিত বই এবং একই সঙ্গে এই বইয়ের মধ্য দিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা ভাষায় প্রথম যতিচিহ্নের প্রবর্তন ঘটান। আর ‘পদার্থবিদ্যা’ (১৮৫৭) ছিল তাঁর লেখা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের (Pure Science)
প্রথম বাংলা বই। বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। আবার, ১৮৪২ সালের জুন মাসে প্রসন্নকুমার ঘোষের সহায়তায় অক্ষয়কুমার ‘বিদ্যাদর্শন’ নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন, তার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালি মননকে বিজ্ঞানচেতনায় সমৃদ্ধ করা। পাশ্চাত্য বেকনীয় দর্শনের গুণগ্রাহী অক্ষয়কুমার দত্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণে তিনি নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন।
১৮৪৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’-য় ব্রিটিশ phrenologist (করোটি পরীক্ষা দ্বারা কোনও ব্যক্তির চরিত্র ও বিবিধ গুণাবলি নির্ণয় করতে পারেন যাঁরা) জর্জ কুম্ব (George Combe)-এর ‘The Constitution of Man Considered in Relation of External Object’ পুস্তকের ভাবধারায় ভারতীয় প্রেক্ষিতে তাঁর লেখা ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’ প্রকাশিত হতে থাকে। পরে এটাই দু’খণ্ডের বই হয়ে প্রকাশিত হয়।
আর তিন খণ্ডে তাঁর লেখা ‘চারুপাঠ’ ছিল তৎকালীন সময়ের এক জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক। সহজ, সরল ভাষায় ছোট ছোট প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ের নানা প্রবন্ধের মাধ্যমে এই বইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি বিজ্ঞানকে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে অনেকটা সম্পৃক্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।
নিজের উপার্জনের প্রায় সব টাকাই তিনি বাংলায় বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার কাজে নিঃস্বার্থে দান করেছিলেন। মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণার কেন্দ্র রূপে তাঁর অকৃত্রিম দানেই গড়ে উঠেছিল আজকের ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স’।
একবার হিন্দু হোস্টেলের এক দল ছাত্র অক্ষরকুমারকে ঈশ্বর-প্রার্থনার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন করল। তিনি বীজগণিতের সমীকরণ দিয়ে দেখালেন:
পরিশ্রম = শস্য।
পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য।
অতএব, প্রার্থনা = শূন্য।
ছাত্ররা এই উপস্থাপনার নাটকীয়তায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাদের মুখে মুখে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এই সমীকরণ। শিক্ষিত মহলেও আলোড়ন উঠল। এই ঘটনার দু’দিন পর মেডিকেল কলেজের ‘ডিমনস্ট্রেটর’ বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের দেখা, নীলমাধববাবু হাসতে হাসতে বলিলেন, ‘‘আপনি ভাল এক সমীকরণ দিয়া শহরটা তোলপাড় করিয়া দিয়াছেন।”
অক্ষয়কুমারের একটি বইয়ের জন্য স্কুলে আগুন লাগাতে চেয়েছিল কিছু লোক। ঢাকার বিক্রমপুরের ঘটনা। ১৮৫১ সাল। সদ্য বেরিয়েছে ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার’ বইটি। বিক্রমপুরের কালীপাড়া স্কুলের এক দল ছাত্র বই পড়ে মুগ্ধ। দেড়শো বছরেরও আগে সেই বইয়ে অক্ষয়কুমার লিখছেন: বিবাহের আগে হবু দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে ভাল ভাবে আলাপ-পরিচয় করে নেবে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য যেন বেশি না থাকে। সংসারে নারী ও পুরুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব সমান। যদি স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং সমাধানের কোনও পথ খুঁজে না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ কাম্য।
তোলপাড় পড়ে গেল সর্বত্র। কালীপাড়া স্কুলের কিছু ছাত্র সভা করে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলেন: ‘আমরা এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়মসকল অবলম্বন করিব।’ ধর্মান্ধ রক্ষণশীল মহলে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিল। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, স্কুলবাড়িটাই পুড়িয়ে দেবেন। তবে এই হুমকিতে অগ্রণী ছাত্রদের প্রতিহত করা যায়নি। অনেকেই গৃহত্যাগী হয়েছিলেন সে দিন। অক্ষয়-জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন: “উপস্থিত বৃত্তান্তটি সঞ্জীবনী-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ঐ সময়ে ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন।” দ্বারকানাথের উপরেও এর প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা কুলীন ছিলেন, পরিবারে প্রায় সবাই বংশানুক্রমে চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে বিবাহ করতেন। দ্বারকানাথ পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে জানিয়েছিলেন, “আমি এক বই দুই বিবাহ করিব না।”
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক করলেন, তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। উপযুক্ত সম্পাদক খুঁজছিলেন। প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল। ‘অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম।’ – জানাচ্ছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৪৩-১৮৫৫, একটানা বারো বছর ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন অক্ষয়কুমার। গ্রাহক সংখ্যা সাতশো ছুঁয়েছিল। বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত প্রথম বক্তব্য বিদ্যাসাগর প্রকাশ করেন এই পত্রিকাতেই। অক্ষয়কুমার নিজে সম্পাদকীয় নিবন্ধে সেই বক্তব্যকে সমর্থন জানান। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন: ‘বঙ্গদেশের সর্বত্র লোকে ঐ কাগজের প্রতিটি সংখ্যার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিত। সেই চুপচাপ, রোগজীর্ণ, কিন্তু অক্লান্তকর্মী মানুষটি তাঁহার ডেস্কের সামনে বসিয়া বেশ কয়েকটি বছর ধরিয়া বাঙালিদের মতামতকে, তাহাদের চিন্তাগত অবস্থানকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন।’
১৮৫৫ সালে ‘তত্ত্ববোধিনী’ সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন অক্ষয়কুমার। কারণ ‘ভয়ানক শিরঃপীড়া’। আষাঢ় মাসের সন্ধ্যা, ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাঘরে উপাসনা চলছে। হঠাৎই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এর দু’দিন পরে, তত্ত্ববোধিনী দফতরে বসে একমনে লেখালিখি করছেন। হঠাৎ মাথায় কেমন একটা জ্বালা, খুব যন্ত্রণাও। সেই শুরু। একটানা কোনও কিছুতে মনোযোগ দিতে পারতেন না আর। সভাসমিতিতে যেতেন না। জোরে আওয়াজ হলে অসহ্য বোধ হত। বাড়িতে আসবাবপত্র টানাটানির শব্দে ক্ষিপ্ত হতেন, বাড়ির কাছে কেউ কাঠ কাটলে তাঁকে পয়সা দিয়ে বলতেন দূরে গিয়ে ওই কাজ করতে।
‘তত্ত্ববোধিনী’ সম্পাদনার অমানুষিক শ্রম থেকে অব্যাহতি নিয়ে বিদ্যাসাগরের অনুরোধে নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিলেন। একটা মাস-মাইনে তো প্রয়োজন। কিন্তু এই কাজটাও করতে পারলেন না। বছর না ঘুরতে ছেড়ে দিলেন অধ্যক্ষের চাকরি। অসুস্থতার খবর পেয়ে জার্মানি থেকে ম্যাক্সমুলার চিঠি লিখেছেন অক্ষয়কুমারকে। ১৮৮৩ সালের ৩১শে অগস্ট লেখা চিঠিতে উদ্বেগ: ‘আপনার অসুস্থতার খবর শুনে খুব দুঃখিত। আশা করি আপনি অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারবেন।’
অসুস্থতা নিয়েই করেছেন ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ বইটির কাজ। হিন্দু ধর্মের নানা শাখাপ্রশাখা, নানান সম্প্রদায়, বিচিত্র আচরণ। অন্যান্য ধর্মও খুব ব্যতিক্রম নয়। এমনই ১৮২টা সম্প্রদায়কে নিয়ে দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই বইয়ে তিনি প্রকাশ্যে ভাববাদী চিন্তাকে আক্রমণ করেছেন। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণকে মানসিক রোগ বলতেও ছাড়েননি। সব থেকে বড় কথা, এই বইয়ের অনেকটাই তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষার ফসল। রোগ-অসুখ তাঁর নিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এক দিন গাড়িতে বেরিয়েছেন, সঙ্গে অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়। পথে এক ধাঙড়কে দেখতে পেয়ে অক্ষয়কুমার গাড়ি থামাতে বললেন। মানুষটি তাঁর পূর্বপরিচিত। ইতিমধ্যে আরও কয়েক জন ধাঙড় সেখানে এসে উপস্থিত। গাড়ি থামিয়ে তাঁদের কাছ থেকে অক্ষয়কুমার শুনলেন ধাঙড় সমাজের রীতিনীতি, দেবদেবীর পূজার্চনার বৃত্তান্ত। এ কথা-সে কথায় অম্বিকাবাবুও দু-একটা প্রশ্ন করলেন। কিন্তু ধাঙড়রা তাঁকে উত্তর দেবে না। অক্ষয়বাবুকে এত খাতির কেন? এক ধাঙড়ের উত্তর: “উনি আমাদের দেশে গিয়াছিলেন, উনি আমাদের (জাতের) ভেদ মারিয়াছেন।”
ক্ষমাপ্রার্থনা করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার। আলাদা আলাদা সময়ে তিনটি পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয় – ১২৯০ বঙ্গাব্দের ১১ই বৈশাখ ‘সোমপ্রকাশ’-এ, ১২৯১-এর ৮ বৈশাখ ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকায় এবং ১৮৮৫-র ১০ই জুন ‘নিউজ় অব দ্য ডে’ সংবাদপত্রে। অনুরাগীরা তাঁকে নানান বিষয়ে চিঠি লিখতেন, তিনি অসুস্থতার জন্য উত্তর দিতে পারতেন না। মনে মনে গ্লানি বোধ করতেন। তাই এই ক্ষমাপ্রার্থনা। আর একটি ‘ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন’ অবশ্য বেশ মজার। “আমার এক ভৃত্য গত শুক্রবার প্রাতঃকালে স্বর্ণালঙ্কারে ও নগদে প্রায় আড়াইশত টাকা হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহাকে বমাল সহিত ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে উচিতমত পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।” ‘সম্বাদ প্রভাকর’-এ ১২৬০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনে গয়নার বিবরণে আছে: হেলে হার ১ ছড়া, কণ্ঠমালা ১ ছড়া, বাজু ২ খানা, বালা ৪ গাছা।
কলকাতা থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে চাইছিলেন। বালিতে জায়গা দেখে বাড়ি করে থাকতে শুরু করলেন। লাগোয়া জমিতে তৈরি করলেন ‘শোভনোদ্যান’ – উদ্ভিদবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্র। ৩৮ রকমের বৃক্ষ, ১৫ রকমের ফুল বা সুদৃশ্য নানা গাছ, ১৬ রকমের মশলাজাতীয় গাছের কথা পাওয়া যায় নানা জনের বিবরণে। অক্ষয়কুমার রচিত তিন খণ্ড ‘চারুপাঠ’ ছাত্রমহলে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। তাই বিদ্যাসাগর এই উদ্যানের নাম দিয়েছিলেন ‘চারুপাঠ চতুর্থ ভাগ’। বাড়ির ভিতরেও তৈরি করেছিলেন একটি ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। সেখানে ছিল বিভিন্ন যুগের প্রস্তরখণ্ডের নমুনা, ফসিল। শরীর সঙ্গ দিত না, তবু কলকাতা জাদুঘরে বা শিবপুর বোটানিক্যাল উদ্যানে যেতেন নিয়মিত। জাদুঘরে লাঠি নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল বলে সঙ্গীর কাঁধে ভর রেখে চলতে হত। সঙ্গীর হাতে থাকত বই। সেখানে ছাপা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু।
বালির বাড়িতেই একা, নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন ‘ধর্ম্মনীতি’র লেখক। পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে দূরত্ব ছিল। অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র রায় তাঁর দেখাশোনা করতেন। ১৮৮৬-র ২৮শে মে, ছেষট্টি বছর বয়সে যখন প্রয়াত হন, তখন তাঁর পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চার বছর বয়স। এই সত্যেন্দ্রনাথই পরে বাংলা কবিতায় ‘ছন্দের জাদুকর’ বলে খ্যাত। পিতামহকে ‘হোমশিখা’ কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করে লিখেছিলেন ‘বঙ্গীয় গদ্যের গৌরবস্থল/ আমার পূজ্যপাদ পিতামহ…’।
বালির দেওয়ানগাজিতলা এলাকায় ভগ্নপ্রায় দোতলা বাড়ি আছে। ইটের পাঁজর বেরোনো সেই বাড়ি ঘিরে গজিয়ে উঠেছে আগাছার জঙ্গল। দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে গাছের শিকড়, লোহার বিম।
এক ঝলক দেখে ‘হানাবাড়ি’ বলে মনে হলেও বালির জি টি রোড সংলগ্ন ওই বাড়িতেই জীবনের শেষ তিরিশটি বছর কাটিয়েছেন ঊনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রবর্তক এবং বাংলায় বিজ্ঞান ভাবনার পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত। তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিনের অবহেলা ও সংস্কারের অভাবে প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থায় ‘শোভনোদ্যান’ নামের সেই বাড়ি।
বালির দেওয়ানগাজিতলা এলাকার ওই বাড়িটিকে ২০০৬ সালের মে মাসে ‘হেরিটেজ’ তকমা দেয় রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। স্থানীয় বাসিন্দারা সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, ওই সময়ে রাজ্য সরকারের তরফে বাড়ির সীমানা পাঁচিলের বাইরে একটি বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখনও দেওয়ানগাজিতলার গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার পথে চোখে পড়ে নীল রঙের সেই ভাঙাচোরা বোর্ড। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বোর্ড লাগানোই সার। তার পরে আর কোনও দিন ওই বাড়ির সংস্কারে প্রশাসনকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি। সম্প্রতি বালির কয়েক জন বাসিন্দা ফের ওই বাড়িটির সংস্কারের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন-নিবেদন শুরু করেছেন।
রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যান, শিল্পী শুভাপ্রসন্ন সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, ‘‘বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আলোচনাও করেছি ওই বাড়ি নিয়ে। অক্ষয়কুমার দত্ত অত্যন্ত গুণী মানুষ ছিলেন। তিনি বাঙালির গর্ব। সেই হিসেবে চেষ্টা করছি যদি কিছু করা যায়।’’ পাশাপাশি তিনি এটাও জানিয়েছিলেন, বাড়িটির সংস্কারের বিষয়ে কমিশনের কাছে কেউ আবেদন করতেই পারেন। সে ক্ষেত্রেও কমিশন ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, যে বাড়ি ১৪ বছর আগেই ‘হেরিটেজ’ তকমা পেয়েছে, সেটির সংরক্ষণের জন্য ফের কেন আবেদন করতে হবে? তাঁদের আরও প্রশ্ন, ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সম্পাদকের দায়িত্বে থাকা অক্ষয়বাবুর বাড়িটি কি রাজ্য প্রশাসন সংরক্ষণ করতে পারত না?
বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়া সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, ‘‘বাড়িটির সংরক্ষণ করে সেখানে সংগ্রহশালা তৈরির জন্য হাওড়া পুরসভাকে বলেছিলাম। কিন্তু পুর বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় আর কিছু হয়নি। এ নিয়ে প্রশাসনের উচ্চ স্তরেও কথা বলব।’’
ইতিহাস বলছে, নিজের লেখা পাঠ্যপুস্তক ‘চারুপাঠ’ থেকে অর্জিত অর্থেই বালিতে ‘শোভনোদ্যান’ নামের বাড়িটি তৈরি করেন অক্ষয়বাবু। ১৮৫৬ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত সেখানেই কেটেছে ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ গ্রন্থের লেখকের। বাড়ির পাশাপাশি অক্ষয়বাবু সেখানে হরেক প্রজাতির গাছের বাগান এবং জীবাশ্ম, প্রবাল ও বিভিন্ন ধরনের পাথরের একটি সংগ্রহশালা তৈরি করেন।
সম্প্রতি বালিতে ওই বাড়িটি দেখতে এসেছিলেন ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ’-এর ভিজিটিং প্রফেসর আশিস লাহিড়ী। তিনি অক্ষয়বাবুর উপরে গবেষণা করছেন। তাঁর কথায়, ‘‘স্বয়ং বিদ্যাসাগর বালির এই বাড়িতে এসেছিলেন। রসিকতা করে তিনি অক্ষয়বাবুকে বলতেন, এটা চারুপাঠের চতুর্থ সংস্করণ। সেই হেরিটেজ বাড়ির এমন বেহাল অবস্থা দেখে খুব কষ্ট লাগছে।’’ জানা যায়, ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর কলকাতায় ‘নর্মাল স্কুল’ স্থাপন করে অক্ষয়বাবুকে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে ওই চাকরি ছেড়ে দেন ‘বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’, ‘ধর্মনীতি’, ‘ভূগোল’ ও ‘পদার্থবিদ্যা’র লেখক।
১৮৮৬ সালের ১৮শে মে ৬৬ বছর বয়সে বালিতেই মারা যান অক্ষয়বাবু। বালির শ্মশানে তাঁর দাহকার্য হলেও সাবেক বালি পুরসভার তখনকার কোনও রেকর্ড এখন আর পাওয়া যায় না। তবে অক্ষয়বাবুকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন বই থেকে জানা যায়, বালি ও কলকাতায় আয়োজিত তাঁর স্মরণসভায় পরিকল্পনা করা হয়েছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণাকে সহজ বাংলায় প্রকাশ করা ওই লেখকের একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করা হবে। পরে অবশ্য কিছুই হয়নি।
বেঁচে থাকতেই ভাববাদের উল্টো পথের এই একলা পথিক লিখেছিলেন –
‘যদি বা আমার কীর্ত্তি স্থায়ী হয়, কিন্তু আমি তো চিরস্থায়ী নই। … মৃত্যুর পরে আমি সে কীর্ত্তি ঘোষণা শুনিতে আসিব না।’
(তথ্যসূত্র:
১- অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ (২০০৯)।
২- অক্ষয়কুমার দত্ত, বিজয় কুমার দত্ত, গ্রন্থতীর্থ (২০১০)।
৩- অক্ষয়কুমার দত্ত আঁধার রাতে একলা পথিক, আশীষ লাহিড়ী, দে’জ পাবলিশিং (২০০৭)।
৪- Akshaykumar Dutta (Makers of Indian literature), Asitakumara Bhaṭṭacharya, Sahitya Akademi (১৯৯৬)।
৫- অক্ষয়কুমার দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৬- আনন্দবাজার পত্রিকা: ১৪ই জুলাই ২০১৯ সাল, ২৮শে জানুয়ারি ২০২০ সাল ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ সাল।)
মতামত লেখকের ব্যক্তিগত