কেউ যদি কখনও লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে হেঁটে চিড়িয়াখানা কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অথবা রেসকোর্স গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর জায়গাটা চিনতে মোটেও অসুবিধা হবে না। পি.জি. হসপিটালের নাম সকলেই জানেন, হালে যেটির নাম সুখলাল কারনানি হাসপাতাল। চৌরঙ্গী রোডের পর ক’পা যেতে না যেতেই বাঁদিকের ফুটপাত ঘেঁষে কারনানি হাসপাতালের লৌহ-ঘের। সেখান থেকেই শুরু হাসপাতালের সীমানা। সেখান থেকে আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে, থামলেই সামনে একটা লাল রঙের তোরণ দেখা যাবে, তাতে এক টুকরো সাদা পাথরের উপরে লেখা আছে কয়েকটা ছত্র। তোরণশীর্ষে রয়েছে কালো পাথরে খোদাই করা একটা আবক্ষ মূর্তি। ঘটনাটা একদিক থেকে কিছুই নয়। কারণ তোরণটা চন্দননগর বা মহীশুরের কোন বিজয় তোরণ নয়। সেখানে লেখা লাইন কয়টিও ক্লাইভ ওয়াটসন বা আউটরাম লরেন্স-এর মত কোন বীরত্ব গাথা নয়। সেখানে লেখা আছে সামান্য কথা। ছোট্ট একটি সংবাদ। বাংলা করে বললে যার মানে দাঁড়ায় – এখান থেকে, এই তোরণটি থেকে মাত্র কয়েকগজ দূরের ঐ ছোট্ট গবেষণাগারটিতে এই ভদ্রলোক একদিন আবিষ্কার করেছিলেন – মশা ম্যালেরিয়ার বাহন।
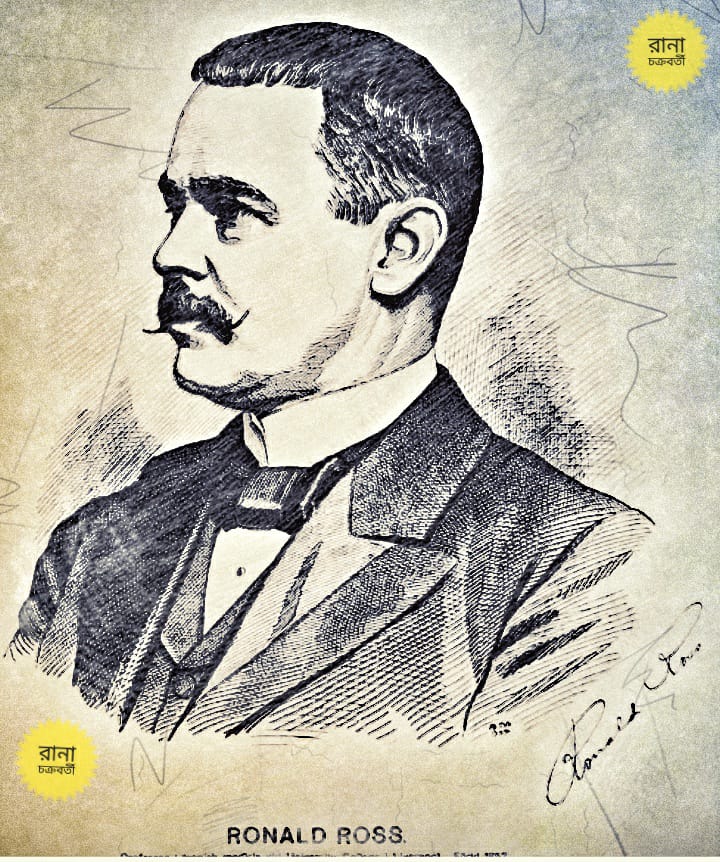
মশা থেকে ম্যালেরিয়া, আজকের বাচ্চারাও হেসে ফেলবে খবরটা শুনে। বর্তমানে কে না জানে মশা ম্যালেরিয়ার বাহন? আবিষ্কারটা তুচ্ছ বলে নয়, ঘটনা এখানে ঘটেছিল বলে। মশা এবং ম্যালেরিয়ার যোগাযোগ না জানে পৃথিবীতে আজ এমন শিক্ষিত লোক নেই। কিন্তু তাঁদের অনেকেরই জানা নেই এই যোগাযোগটা আবিষ্কৃত হয়েছিল কলকাতা শহরে। ‘রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকেতায় আছি’ – কলকাতার সঙ্গে মশার যোগাযোগ অনেকদিনের। এ-শহরে থাকতে হলে মশা মাছি নিয়ে থাকতেই হবে। ঈশ্বর গুপ্ত তা-ই ছিলেন। আমরাও তাই আছি। কিন্তু যাকে বলে সেই থাকার মত থাকা, সে ছিলেন মাত্র একজনই। আপনার সামনে ঐ কাল পাথরের মূর্তিটি যাঁর, তিনিই।
কত সাহেব-ই তো এসেছিলেন কলকাতায়। রাতের পর রাত মশার অত্যাচারে তাঁরা ছটফট করেছেন বিছানায় পড়ে। কখনও ঘরময় ছুটে বেড়িয়েছেন মশা-শিকারের ব্যর্থ-চেষ্টায়। কিন্তু পরিবর্তে এই ছোট্ট কীটটির মৃত্যু-কামড়ে শিকার হয়েছেন নিজেরাই। মুরদের চেয়েও ইংরেজরা বেশি ভয় করত মশাকে। মরে মরে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল নেটিভরা। কিন্তু ইংরেজরা তখনও এভাবে মরতে শেখেনি। ফলে মশা ছিল তাঁদের কাছে আতঙ্ক। কোকিল নিয়ে ইংরেজ কবিরা কবিতা লিখেছেন। কিন্তু ভারতে ইংরেজ কবির অন্যতম বিষয় ছিল সেদিন মশা। ‘মশা’ নিয়ে কত কবিতা কত গান যে আছে ‘অ্যাংলো ইন্ডিয়ান’ সাহিত্যে তার ইয়ত্তা নেই।
সবই হয়েছে গান, গালাগালি, মশারির উদ্ভাবন – ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটি সেটি হলো অনেক, অনেক দিন পরে। অবশেষে স্যার রোনাল্ড রস যেদিন কলকাতায় এলেন সেদিন।
সাধারণত লোকে জানে এনোফেলিস মশা যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেহ থেকে দেহান্তরে বয়ে নিয়ে যায় রোনাল্ড রস এই তত্ত্বটিরই আবিষ্কারক। এ-কারণেই অবশ্য ১৯০২ সালে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিল তাঁকে। ‘মার’ থেকে আরও পঞ্চাশটি সম্মান পদকের কারণও অবশ্যই তাই। কিন্তু জীবনী পড়লে মনে হয় রোনাল্ড রস-এর জীবনে এ আবিষ্কারটা নেহাতই আকস্মিক ঘটনা নয়।
তাঁর জন্ম হয়েছিল ভারতেই – আলমোড়ায়। ১৮৫৭ সালের ১৩ই মে। বারটা ছিল শুক্রবার। একে থার্টিনথ, তার উপর ফ্রাইডে! মা বাবা ভেবেছিলেন ছেলেটা বোধ হয় দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মাল। কিন্তু ক’বছর বাদেই দেখা গেল ব্যাপারটা উল্টো। যাতে হাত দেন রস তাতেই তিনি বিজয়ী। ইচ্ছে ছিল চিত্রকর হবেন। কেমব্রিজ এবং অক্সফোর্ড ড্রয়িং-এর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রমাণ করেছিলেন – ইচ্ছাটা স্বপ্ন মাত্র নয়। লিওনার্দো না হয়ে বিটোফেন? তাও যে একেবারে আকাশ কুসুম কল্পনা তাঁর কাছে, তাও নয়। শেলি বায়রনের কবিতায় রস অহরহ সুর যোজনা করতেন। কবিতাও লিখতেন নিজে। শুধু কবিতা নয়, ছোটগল্প, নাটিকা, এমন কি উপন্যাসও। তাঁর একখানা উপন্যাস ‘চাইল্ড অব ওসান’কে সমালোচকেরা একদিন ঠেলে দিয়েছিলেন ক্ল্যাসিকের তালিকায়। বহু দেশ ভ্রমণকারী রস বহুভাষী ছিলেন। ইতিহাস, দর্শন, গ্রীক এবং রোমান ও ইউরোপীয় সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। কিছুকাল লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি হলো জাহাজে সার্জনের চাকরি এবং অবেশেষে ভারতে ‘আর্মি মেডিক্যাল সার্ভিসে’। ভারতের বাইরে এশিয়া আফ্রিকার বহু দেশে যেমন কাজ করেছিলেন রোনাল্ড রস, তেমনি কাজ করেছিলেন কলকাতা ছাড়াও ভারতের আরও আরও অঞ্চলে। কিন্তু কলকাতার গর্ব – এখানে জনচক্ষে সাফল্যলাভ করেছিলেন অলক্ষুণে শুক্রবারে জাত এই লোকটি।
সেই তোরণটা থেকেই তাকিয়ে দেখা যায় ঐ আটপৌরে বাড়িটিকে। মনে মনে একবার চিন্তা করে দেখুন সেই চিত্রটি। অপরিসর ঘরে সাবেকি যন্ত্রপাতি নিয়ে একাকী সাধনায় মগ্ন আছেন এই বিজ্ঞানী। টিউবে টিউবে রকমারী মশা, নরদেহের রক্ত।
ম্যালেরিয়ায় প্রায় ফি-বছরই কাবু হয় কলকাতা। আবার ওই রোগের উৎস সন্ধানের কৃতিত্বের দাবিদার হিসেবেও শেষ পর্যন্ত জিতেছিল কলকাতাই! ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে একটি মামলায়। নোবেলজয়ী রোনাল্ড রস কোথায় বসে ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন, সেই প্রশ্নে কলকাতাকে প্রায় হারিয়েই দিয়েছিল রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাদের মতে, কলকাতা নয়, ওই কৃতিত্ব আদতে সেকেন্দ্রাবাদের। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৪ সালের ৩১শে জুলাই কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, সেকেন্দ্রাবাদ নয়। রোনাল্ড রস কলকাতায় বসেই ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন।
কিন্তু আদতে মশা আর ম্যালেরিয়া নিয়ে এহেন কাণ্ড কেনই বা হয়েছিল? কেনই বা দুই শহর নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর খুঁজতে আমাদের যেতে হবে অতীতে।
জব চার্নক যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঘাঁটি পত্তন করেছিলেন কলকাতায়, তার একটা কারণ ম্যালেরিয়া এড়ানোর তাগিদ। গোড়ায় গিয়েছিলেন হুগলি। সেখানে মুঘল নবাবের নায়েব-গোমস্তাদের আস্তানা। তাদের খাঁই মেটাতে নাজেহাল হয়ে গেলেন হিজলিতে। সেখানে যেমন বাঘ, তেমনি মশা। ১৬৮৭-র ফেব্রুয়ারি থেকে জুন, তিন মাসে দলের প্রায় দু’শো জন মারা গেল জ্বরে। অতঃপর উলুবেড়িয়া ট্রায়াল দিয়ে এলেন সুতানুটি। গোবিন্দপুর খাল (এখনকার টালি নালা), পূর্বে সল্ট লেক আর উত্তরে ইছাপুর খাল সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুরকে প্রায় একটা দ্বীপ তৈরি করেছে। মুঘল সেনা চট করে আক্রমণ করতে পারবে না। ১৬৯০ সালে পত্তন হল কলকাতার।
চার্নক কি আর জানতেন, এক দিন লাল কাগজে ছেপে পোস্টার পড়বে ‘শত্রুর চাইতে অনেক বেশি সৈন্য মারে ম্যালেরিয়া’? ব্রিটিশ সেনাদের নির্দেশ দেওয়া হবে, ‘তুমি ঢুকছ ম্যালেরিয়া এলাকায়। কম্যান্ডিং অফিসারের নির্দেশ মেনে সব সতর্কতা পালন করো।’ এক সাহেব লিখছেন, ১৭০০ সালে কলকাতায় প্রায় ১২০০ ইংরেজ ছিল, জ্বরের কোপে পরের বছর ৪৬০ জন কবরে। কোম্পানি গিয়ে রানির শাসন এল, তখনও ফোর্ট উইলিয়াম, ব্যারাকপুর, দমদম, আলিপুর – চারটে ক্যান্টনমেন্টে সব চেয়ে বেশি মৃত্যু জ্বরে। গোরা সৈন্য বাঁচাতে জনস্বাস্থ্যের পত্তন কলকাতায়। নেটিভ মরলে তাদেরও মরতে হয়। আর জ্বর তো নেটিভদের লেগেই আছে। নেটিভ হাসপাতালের এক ডাক্তার লিখছেন (১৮৩৩), নেহাত পিলে খুব না ফুললে, আর পেট ছেড়ে না দিলে কেউ জ্বরের জন্য ডাক্তার দেখায় না।
তবে যাতে নেহাত মরে না যায়, তার জন্য পুজো দেয়। খিদিরপুরের ওলাইচণ্ডী মন্দির, পাড়ায় পাড়ায় শীতলা মন্দির মহামারীর উত্তরাধিকার। দু’শো বছর ধরে ‘সিটি অব প্যালেস’ কলকাতা, কংগ্রেসি-স্বদেশী-সন্ত্রাস-হরতালের কলকাতার সঙ্গে গলাগলি বাস করেছে মহামারীর কলকাতা।
দু’শো বছর আগের এই গল্পই ধরুন। ডাকসাইটে ধনী রূপলাল মল্লিকের নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ। বিশপ হেবরের স্ত্রী লিখছেন, সেখানে রইসদের ‘হার্টথ্রব’ বাইজি নিক্কির গান শুনেছেন (পর পর তিন রাতের মুজরোর জন্য যাঁর ‘রেট’ ছিল হাজার টাকা আর দু’খানা কাশ্মীরি শাল), গান শুনতে গিয়ে তিনি মশার কামড়ে তিষ্ঠোতে পারেননি। তাঁর নালিশ, অতিকায় বাড়ির যেটুকু অতিথিরা দেখবে, তা বাদে বাকিটা বিশ্রী নোংরা, জমে-থাকা ময়লা এড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়েছে সাবধানে।
আজ যেমন পঞ্চাশ-লাখি পুজোমণ্ডপে অপূর্ব কারুকাজ দেখে বেরিয়ে আবর্জনার স্তূপ পাশ কাটাতে হয় সন্তর্পণে। দুর্গাদালান থেকে প্রতিমা আজ কর্পোরেশনের রাস্তায়, কিন্তু সর্বজনীন পুজোর কর্তারা ‘রিপ্যাকেজ্ড’ জমিদার। তাই জাঁকজমক আর জঞ্জালের এমন সাবেকি সহাবস্থান। তাই পুজোর পরেই শহরে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়া।
কতগুলো শতাব্দী একত্রে বেঁচে আছে এই শহরে? একশো বছর আগের সরকারি রিপোর্ট বলছে, ক্যাম্বেল হাসপাতালের জলাশয়ে মিলেছে অ্যানোফিলিস মশার লার্ভা। সেই হাসপাতাল এখন নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ। এনআরএস-সহ কলকাতার সব মেডিক্যাল কলেজ আজও মশার আঁতুড়ঘর। দেড়শো বছর আগে যখন বর্ধমানে, নদিয়ায় হাজার হাজার মানুষ মরছিল জ্বরে, জনসংখ্যা নেমে আসছিল অর্ধেকে, তখন কেউ বুঝতে পারছিল না রোগটা কালাজ্বর না ম্যালেরিয়া। তার পর রোনাল্ড রস কলকাতাতে বসেই মশার হুলের মাহাত্ম্য বুঝলেন, উপেন্দ্রনাথ কালাজ্বরের ওষুধ বিক্রি করে লক্ষপতি হলেন। আজ পাড়ায় পাড়ায় প্যাথ ল্যাব। তবু বোঝা যাচ্ছে না, লোকে কিসে মরছে— ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, না কি আর কোনও জ্বর। আজও নিরাময়ের উপায় হাতের কাছে, তবু বিনা চিকিৎসায়, ভুল চিকিৎসায় মরছে মানুষ।
দাদাঠাকুরের শরৎচন্দ্র পন্ডিত ডিএল রায়ের গানে কথা বসিয়েছিলেন,
‘আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু করি নাই কিছু আর
শুধু মাদুরেতে শুয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে কেঁপেছি…’।
বিছের হুলের মতো, এই প্যারডির বিষ শেষ দু’লাইনে লিখিত,
‘আছে সবার উপরে মাথা তব প্রভু, উপেক্ষা কভু ঘৃণা গো
ধর চৌষট্টি হাজার সহিত চাষার অন্তিম নিশ্বাস রেখেছি।’
জ্বরে মৃত্যু চৌষট্টি হাজার। তখনও যোগ হয়নি তেতাল্লিশের মন্বন্তরের তিরিশ লক্ষ মৃত্যু, যখন অনাহারে মৃতপ্রায়দের শেষ ধাক্কা দিয়েছিল ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত। দেশ যে বছর স্বাধীন হয়, সে বছর বিরাশি হাজার বাঙালি মারা যায় ম্যালেরিয়ায়। সে সময়ের একটা রিপোর্টে (১৯৪৪) জানা যায়, মহামারীর সময়ে এন্তার কালোবাজারি হত কুইনিন। আজ ডেঙ্গির বাজারে ব্ল্যাক হচ্ছে রক্তের প্লেটলেট।
তবু তফাত একটু আছে। ‘বিদূষক’ শরৎচন্দ্র বিদেশি শাসককে স্বনামেই খোঁচা দিয়েছেন।
আজও মশা কমেনি, ভয় বেড়েছে।
কেন কলকাতা মশা-মাছি আর জ্বরের আড়ত, তা নিয়ে নানা থিওরি মেলে। সাহেবদের পছন্দের ব্যাখ্যা ছিল হিন্দুদের চরিত্রদোষ। যারা দিনে তিন-চার বার চান করে, তাঁদেরই বাড়ির পাশের রাস্তায় মলমূত্র, গঙ্গায়-খালে মৃতদেহ। নেহাত শেয়াল, হাড়গিলে, কাক-চিল ছিল বলে রক্ষে। শুনে অন্যেরা তেড়েফুঁড়ে বলেন, তোমরাই বা কিসে কম বাপু? শিল্পবিপ্লবের পর লন্ডনের কী হাল ছিল, প্লেগ-পক্সে কত মরেছে, তা নিয়ে আর মুখ খুলিও না। আবার কেউ একটু সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন। আসলে কলকাতা তো কারও দেশ-মুলুক ছিল না। শহরটাই বহিরাগতদের। মজুর, কেরানি, বণিক, জমিদার, সবাই টাকার ধান্দায় এসেছে। যারা দু’পয়সা করেছে, তারা পথঘাট, মন্দির-ইস্কুল নির্মাণ করেছে দেশ-গ্রামে, কলকাতায় নয়। প্রযুক্তিবাগীশের উত্তর, ইংরেজগুলোই মুখ্যু। ভেবেছিল কলকাতার ঢাল গঙ্গার দিকে। আদতে ঢালু সল্ট লেকের দিকটা। ভুলভাল খাল কাটার ফলে নিকাশির বদলে জল দাঁড়িয়ে গেল। জ্বর তাড়াতে সল্ট লেকের জলাজমি ভরাট করে দেওয়া উচিত, উঠেছিল দাবি।
যদি সে দিন সাহেবরা তা মেনে নিত, যদি সিপাহি বিদ্রোহের আগেই ভরে যেত সল্ট লেকের জলাজমি, কলকাতার ম্যাপটা অন্য রকম হত। তা হয়নি, কিন্তু ইতিহাসের গতি ঠিক করেছে জ্বর। তৈরি হল ফিভার হাসপাতাল কমিটি। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্তেরা চাঁদা দিলেন। কলকাতায় জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য চাঁদা সেই প্রথম। মতিলাল শীলের দান-করা জমিতে তৈরি হল মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতাল। কলেজ শুরু ১৮৩৫, হাসপাতাল ১৮৫২ সালে। এশিয়ার প্রথম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। প্রেসিডেন্সি কলেজ যেমন তৈরি করেছিল সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহাদের, তেমনই মেডিক্যাল কলেজ থেকে উঠে এলেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, কেদারনাথ দাস, শম্ভুনাথ দে, সুবোধচন্দ্র মিত্র। বিংশ শতকে বিশ্বের চিকিৎসা মানচিত্রে স্থান পেল কলকাতা।
শুধু কলকাতা কেন? ম্যালেরিয়া নির্ধারণ করেছে বহু শহরের, এমনকী সভ্যতার ইতিহাস। মায়া সভ্যতা উজাড় করেছিল ম্যালেরিয়া। আলেকজান্ডারকে বিষ দেওয়া হয়েছিল, নাকি ভারতের মশা ঢেলেছিল ম্যালেরিয়ার বিষ? তাঁর সাকিন গ্রিস দেশ থেকে রোগ ছড়ায় রোমে। সতেরোজন পোপ মারা গিয়েছেন ম্যালেরিয়ায়। ইতালি ছিল ম্যালেরিয়ার আড়ত, যদ্দিন না মুসোলিনি নামে এক যুদ্ধবাজ ফাসিস্ত শাসক জলা বুজিয়ে ধ্বংস করেন মশার বংশ।
ম্যালেরিয়ার কারণটি যে ‘ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট’ নামের পরজীবী তা ১৮৮০ সালে ফরাসি বৈজ্ঞানিক আলফোনস ল্যাভেরান-এর আবিষ্কার থেকেই জানা গিয়েছিল। কিন্তু এই পরজীবী কী ভাবে মানুষে সংক্রামিত হচ্ছে তখন তা ছিল অন্ধকারে। এই নিয়েই গবেষণায় মগ্ন ছিলেন রোনাল্ড রস। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার এক মানুষ – চিত্রশিল্পী, গণিতবিদ, সুরকার, কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। চিকিৎসক হওয়া কখনই লক্ষ্য ছিল না। বাবার চাপে তাঁর চিকিৎসক হওয়া। আর জীবনের ঘটনাচক্র তাঁকে নিয়ে গেল চিকিৎসা, গবেষণা ক্ষেত্রে। নিজের মেধা ও অধ্যবসার জোরে মোক্ষ অর্জন করলেন সেখানেই। প্রথম বার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস-এর পরীক্ষায় পাশ করতে ব্যর্থ হলেন। বাবার ভ্রূকুটিতে আবারও তাঁকে সেই পরীক্ষার প্রস্তুতিতে থাকতে হল। মাঝের সময়টুকু কাটিয়ে দিলেন এক নিউ ইয়র্ক-লন্ডন জলপথের জাহাজের সার্জেনের চাকরি নিয়ে। পরের বার ১৮৮১ সালে যোগ্যতা পরীক্ষায় পাশ হলেন। প্রথম পোস্টিং হল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে। তাঁর জীবনে ও মনে ম্যালেরিয়া বা মশার একটা জায়গা ছিল। ছোটবেলায় ভারতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখেছেন। তাঁর বাবাও আক্রান্ত হয়ে ছিলেন ম্যালেরিয়ায়।
মাদ্রাজে কাজ করার সময়ে তিনি বেশির ভাগ সময় নিজেকে নিযুক্ত রেখে ছিলেন কুইনাইন দিয়ে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায়। ১৮৮৩-এ বেঙ্গালুরুতে যে বাংলোটি পেলেন তাতে মশার উৎপাত প্রবল। কারণ, খুঁজতে গিয়ে দেখলেন জানলার পাশে বিশাল খোলা জলাধার। তাতে মশার লার্ভা দেখে বুঝলেন এটিই তাদের প্রজননস্থল। সেটি জলমুক্ত করতেই মশার উৎপাত কমে গেল। পরিষ্কার জমা জলকে ‘টার্গেট’ করে মশার প্রজননস্থলকে নির্মূল করার পদ্ধতির তিনিই হবেন পথপ্রদর্শক।
সাত বছর ভারতে থাকার পর রস ১৮৮৮ তে এলেন লন্ডনে। ইতিমধ্যে তাঁর লেখা হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি উপন্যাস – ‘দ্য চাইল্ড অব দ্য ওসেন’, ‘স্পিরিট অফ দ্য স্টর্ম’, ‘দ্য রেভেলস অব ওসেরা’। বুঝতে পারছিলেন তাঁর সাহিত্য রচনার প্রয়াস সার্থকতার মুখ দেখছে না। তিনি পেশাগত দিকটিকেই আঁকড়ে ধরলেন। জনস্বাস্থ্যের উপরে ডিপ্লোমা কোর্স যেমন করলেন, তেমনই মাইক্রোস্কোপ ও ল্যাবরেটরিগত শিক্ষায় দীক্ষিত হলেন। কিন্তু তবুও ভারতে ফিরে কাজে তেমন সাফল্য পাচ্ছিলেন না। এর পরে তাঁর জীবনে ঘটল সেই বিশেষ ঘটনা। ১৮৯৪-এ ছুটিতে লন্ডনে এসে পরিচত হলেন ফাইলেরিয়ার কারণ যে কিউলেক্স মশা তার আবিষ্কারক ও ট্রপিক্যাল ডিজিজ-এর স্থপতি প্যাট্রিক ম্যানসন-এর সঙ্গে। ম্যানসনই রস-এর কাজের অভিমুখ ঠিক করে দিলেন পথপ্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুর মতো। মশা-ই যে ম্যালেরিয়ার বাহক এই দৃঢ় ধারণা তিনি রস-এর মধ্যে সঞ্চারিত করলেন। ১৮৯৫-এর মার্চে ভারতে ফিরে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে শুরু করলেন কাজ। রসের হতাশা, বার বার ব্যর্থতায় ম্যানসন তাঁকে উদ্দীপনা জুগিয়েছেন, প্রেরণা ও সাহস দিয়েছেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ১৭৩টি চিঠির বিনিময় তার প্রমাণ। এরই ফসল ১৮৮৭-এর যুগান্তকারী আবিষ্কার।
১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে সেকেন্দ্রাবাদের বেগমপেট-এর হাসপাতালে তার আগের দু’বছর ধরে ইংরেজ চিকিৎসক-বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছিলেন। মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে বেশিরভাগ সময় কেটে যাচ্ছিল তাঁর। সেকেন্দ্রাবাদে আগস্টে দুঃসহ গুমোট গরম। মশা ব্যবচ্ছেদ করে মাইক্রোস্কোপের নীচে প্রধানত তার পাকস্থলীর কোষে ম্যালেরিয়া পরজীবির সন্ধান করে চলেছিলেন রস। তিনি পরে জানিয়েছিলেন, প্রথমে কাজে অসুবিধে হচ্ছিল না, কিন্তু বার বার ব্যর্থতা পর্যুদস্ত করে ফেলছিল তাঁকে। হাসপাতালের ঘরটি ছিল ছোট, গরম আর অন্ধকার। ছাদের কার্নিসের নীচ দিয়ে কোনও মতে আলো আসত। পাখা ব্যবহার করা যেত না। কারণ, তা হলে হাওয়া উড়িয়ে দেবে ব্যবচ্ছেদ করা মশাগুলিকে। আই ফ্লাই নামের ছোট ছোট মাছির ঝাঁক মহানন্দে রসের কানে, চোখের পাতায় এসে চরম জ্বালাতন করত। কখনও কখনও দু’-একটা ‘স্টেগোমিয়া’ মশা কামড়ে তাদের বন্ধুদের মৃত্যুর জন্য রসের উপরে শোধ নেওয়ার চেষ্টা চালাত। রসের কপাল ও হাতের ঘামে মরচে পড়ে গিয়েছিল মাইক্রোস্কোপের স্ক্রুগুলি, তার শেষ অবশিষ্ট আই-পিসটিতেও চিড় ধরেছিল।
মশার কামড়েই যে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে এটা বুঝতে পেরেও রোনাল্ড রস তা প্রমাণ করতে বার বার ব্যর্থ হচ্ছিলেন। কারণ, তার পরীক্ষিত মশাগুলি ম্যালেরিয়া বাহক প্রজাতির ছিল না। অবশেষে তিনি পেলেন বিশেষ ‘বিন্দুচিহ্নিত ডানাওয়ালা’ মশাকে। সহকারীদের সাহায্যে তাঁকে রক্ত পরীক্ষার জন্য বা মশার কামড় খাওয়ার জন্য লোক জোগাড় করতে হত। ১৬ই অগস্ট ওই বিশেষ মশাকে তিনি ব্যবহার করলেন হুসেন খাঁ নামে ম্যালেরিয়ায় সংক্রমিত এক রোগীর উপরে। অন্য বার হুসেন খাঁ এক আনা পেলেও সেবার পেয়েছিলেন দশ আনা। এর পরে ২০শে অগস্ট-এর সকাল। সেদিন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দিন হয়ে থাকবে। সকাল সাতটায় রোনাল্ড রস হাসপাতালে গিয়ে রোগী দেখলেন, তাঁর ডাকের চিঠিপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, তার পরে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ করে শুরু করলেন তাঁর কাজ। দুপুর একটায় পেলেন তাঁর বহু দিনের সাধনার ফল। সংক্রমিত মশার পাকস্থলীর দেওয়ালে পেলেন ম্যালেরিয়া পরজীবী। তিনিই ঘোষণা করেছিলেন – ২০শে অগস্ট হোক ‘বিশ্ব মশা দিবস’। ১৮৯৭ সালের ২০শে আগস্ট ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন সার্জন। প্রথমে খবরটা শুনতে পেয়েছিলেন সহকর্মীরা। তারপর ক্রমে বিশ্ববাসী। মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার লক্ষ লক্ষ জ্বর-কাতর রোগী কাঁপতে কাঁপতে খবর পেয়েছিল পৃথিবীতে ম্যালেরিয়ার মৃত্যুদূতকে চিহ্নিত করে ফেলেছেন জনৈক মানবহিতৈষী।
রোনাল্ড রস উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে কখনও সহযোগিতা পাননি। গবেষণা, সহকারী নিয়োগ ইত্যাদির জন্য অর্থ ব্যয় তাঁকে নিজেকেই করতে হয়েছিল। আর বারবার পেয়েছিলেন বদলি হয়ে যাবার নির্দেশ।
এমনকি, এই আবিষ্কারের কিছু দিন পরে তাঁকে বদলি হতে হয়েছিল রাজস্থানের মরুভূমি লাগোয়া গ্রামে, সেখানে ম্যালেরিয়া এক বিরল অসুখ। সেখানে তিনি পাখির উপরে ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। অনেক চেষ্টায় অবশেষে তিনি ১৮৯৮ সালেট ২৯শে জানুয়ারি কলকাতায় আসতে পারলেন। কলকাতার পিজি হাসপাতালে (এখনকার শেঠ সুখলাল করোনানি হাসপাতাল) শুরু হল তাঁর গবেষণা। তিনি পাখির উপরে গবেষণা করে দেখালেন যে মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়া পরজীবী বড় হয়ে জমা হচ্ছে মশার স্যালাইভারি গ্লান্ডে। তার পরে দংশনের সঙ্গে সংক্রামিত করছে সেই পরজীবী। কোথায়? না, কলকাতায়। সেই তোরণ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে – হাসপাতালের ঐ ছোট্ট ঘরটিতে।
রোনাল্ড রস তাঁর আবিষ্কারের জন্য ১৯০২ সালে পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। তিনি শুধু ব্রিটেনেরই নন, কলকাতা তথা ভারতের প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রাপক। তাঁর ও তাঁর কাজের প্রতি সম্মানে পিজি হাসপাতালে এক স্মারক স্তম্ভ স্থাপিত হয় ১৯২৭ সালে। এটির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন রোনাল্ড রস নিজেই।
মশাবাহিত রোগ বাংলায় নতুন নয়। আগে আধুনিক প্রযুক্তি ছিল না বলে রোগের ঠিক শনাক্তকরণ সম্ভব ছিল না। মশাবাহিত প্রতিটি রোগ সম্পর্কেই জনসচেতনতা দরকার। আমরা ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষ, ‘রেতে মশা দিনে মাছি’ নিয়েই আমাদের বাস করতে হবে। দরকার শুধু ঠিক জ্ঞান, আর ঠিক রোগের ঠিক চিকিৎসা। সঙ্গে মশারির নিত্য ব্যবহার।
(তথ্যসূত্র:
১- Ronald Ross: Malariologist and Polymath: A Biography, E. R. Nye & Mary E. Gibson, Palgrave Macmillan (১৯৯৭)।
২- Dr Ronald Ross mosquito, Malaria, India and the Nobel Prize; B.K. Tyagi, Scientific Publishers (২০১৯)।
৩- The Making of a Tropical Disease: A Short History of Malaria, Randall M. Packard, Johns Hopkins University Press.)
মতামত লেখকের ব্যক্তিগত






