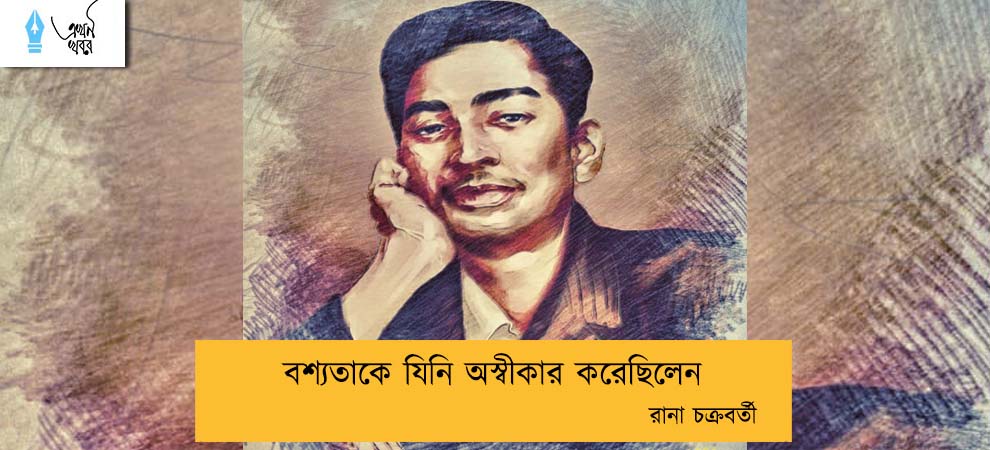১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে, কলকাতার রেড এড কিওর হোম থেকে নিজের মাসতুতো ভাই ও বন্ধু শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন –
“ভূপেন,
… এবার আমার কথা বলি। তিন সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভুগছি। গত এক সপ্তাহ ধরে পার্টির হাসপাতালে কাটাচ্ছি- আরো কতদিন কাটাতে হবে কে জানে। যদিও অঞ্চলটা পার্ক-সার্কাস তবুও দাঙ্গা সংক্রান্ত ভয় নেই। একরকম বৈচিত্রহীন ভাবেই দিন কাটছে, যদিও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। অনন্ত সিং গণেশ ঘোষ ছাড়া পেয়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন— সেই একটা বৈচিত্র্য। সেদিন ডাইনিং রুমে খাচ্ছি এমন সময় কমরেড জোশী সেই ঘরে ঢুকে আমাদের খাওয়া পরীক্ষা করলেন। এটাকেও বৈচিত্র্য বলা যেতে পারে।
তবে কাল আমার জীবনে সব থেকে স্মরণীয় দিন গেছে। মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তাঁরা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর একজন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। গণেশ ঘোষ বললেন— ‘আমি আপনাকে ভীষণভাবে চিনি।’ অম্বিকা চক্রবর্তীও অন্যান্য বন্দীরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন— আমি তো আনন্দে মুহ্যমান প্রায়।
সত্যি কথা বলতে কি এতখানি গর্বিত কোনো দিনই নিজেকে মনে করি নি। ফ্রান্সে আর আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যেদিন শুনলাম সেদিনও এত সার্থক মনে হয় নি আমার এই রোগজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটি ঘণ্টা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বরের এই সন্ধ্যা আমার কাছে অবিস্মরণীয়।হাসপাতালের ছককাটা দিন ধীর মন্থর গতিতে কেটে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে সকালের ঝকমকে রোদ্দুরকে দুপুরে দেবদারু গাছের পাতায় খেলা করতে দেখি। ঝিরঝির ক’রে হাওয়া বয় সারাদিন। রাত্রিরে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়, ডালহাউসী স্কোয়ারের অপিসে বসে কোনো দিনই অনুভব করতে পারবি না এই আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। এখন দুপুর— কিন্তু চারিদিকে এখন রাত্রির নৈঃশব্দ: শুধু মাঝে মাঝে মোরগের ডাক স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, এটা রাত্রি নয়-দিন।
রেডিও, বই, খেলাধুলো— সময় কাটানোর অনেক উপকরণই আছে, আমার কিন্তু সবচেয়ে দেবদারু গাছে রোদের ঝিকিমিকিই ভাল লাগছে। উড়ে যাওয়া বাইরের খণ্ড খণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে বাতাসকে মনে হয় খুবই উপভোগ্য। এমনি চুপ ক’রে বোধহয় অনেক যুগ অনেক শতাব্দী কাটিয়ে দেওয়া যায়। যাক আর নয়। অসুস্থ শরীরের চিঠিতে আমার ভয়ঙ্কর উচ্ছ্বাস এসে পড়ে, কিছু মনে করিস নি। মেজদার মুখে শুনলাম— তুই নাকি প্রায়ই “স্বাধীনতা” কিনে পড়ছিস? শুনে খুব আনন্দ হল। নিয়মিত “স্বাধীনতা” রাখলে আরো খুশী হবো….
সুকান্ত”
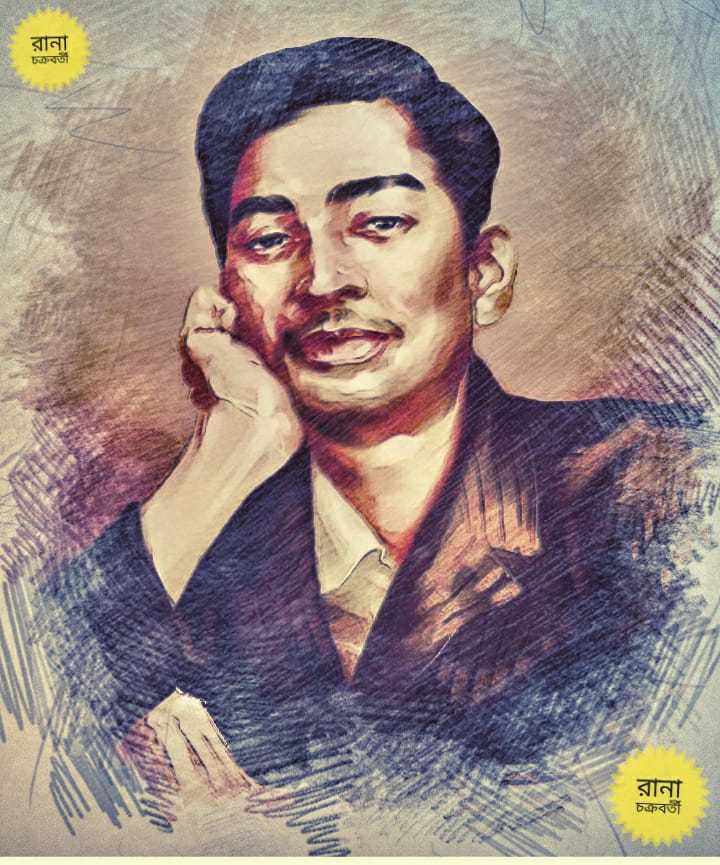
২২শে চৈত্র ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন –
“… আজকাল রাত একটায় যদি কলকাতা ভ্রমণ কর তাহলে তোমার ভয়ঙ্কর সাহস আছে বলতে হবে। শুধু চোর-গুণ্ডার নয়, কলকাতার পথে এখন রীতিমত ভূতের ভয়ও করা যেতে পারে। সন্ধ্যার পর কলকাতায় দেখা যায় গ্রাম্য বিষণ্ণতা। এই আলোকময়ী নগরীকে আজকাল স্মরণ করা কঠিন; যেমন একজন বৃদ্ধা বিধবাকে দেখলে মনে করা কঠিন তার দাম্পত্য-জীবন। আর বিবাহের পূর্বে বিবাহোন্মুখ বধূর মতো কলকাতার দেখা দিয়েছে প্রতীক্ষা-অন্য দেশেরা বিবাহিতা সখীর মতো দেখবে ঘটিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি।
আজ আমার ভাইয়েরা চলে গেল মুর্শিদাবাদ – আমারও যাবার কথা ছিল, কিন্তু আমি গেলাম না মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার এক দুঃসাহসিক আগ্রহাতিশয্যে, এক ভীতি-সংকুল, রোমাঞ্চকর, পরম মুহূর্তের সন্ধানে। তবু আমার ক্লান্তি আসছে, এই অহেতুক বিলম্বে।”
বাংলা সাহিত্যের এক প্রিয়তম নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য, তাই বাঙালির ঘরে শোভা পায় ‘সুকান্ত সমগ্র’, কন্ঠে ধ্বনিত হয় তাঁর বলিষ্ঠ কবিতা –
“পুর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি” …
অথবা –
“এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার” …
কিংবা –
“কলম, তুমি কাহিনী লেখো, তোমার কাহিনী কি
দুঃখে জ্বলে তলোয়ারের মতন ঝিকিমিকি?” …
“সুকান্তর কবিতা সুকান্তকে ছাড়া আর কাউকে মানাবে না” – কথাটা বলেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তেমনি একুশটি বসন্তে ঘেরা ক্ষুদ্র অথচ বিশাল জীবনটিও একান্তই সুকান্তর। যদিও রবীন্দ্রনাথের অনুভুতিতে কবিকে তাঁর জীবনচরিতে পাওয়া যায় না কিন্তু প্রসঙ্গত মনে পড়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের অভিমত কবিতা বুঝে লাভ থাকলেও কবিকে বুঝে আরও লাভ, তাই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। ব্যক্তি মানুষ সুকান্তকে জানতে হলে এবং তাঁর তরুণ মনের গুঞ্জরণ শুনতে হলে তাঁর ‘পত্রগুচ্ছ’ পড়াটা জরুরি।
কবিতার পাশাপাশি সুকান্ত গল্প ও প্রবন্ধও লিখেছেন, যা তাঁর তদানীন্তন যুগ ও কালের দর্পণ। একজন সার্থক লেখক তাঁকেই বলা যায় যিনি লেখায় লেখায় তৎকালীন জীবনের প্রতিফলন ঘটিয়েও, সাহিত্য শিল্পকে শাশ্বত পর্যায়ে তুলতে পারেন। সুকান্তর লেখায় বারবার তারই প্রতিফলন ঘটে যা তাঁর লেখাকে দেশ-কালের সীমানা পার করে Classic-এর পর্যায়ে উন্নীত করে। তাঁর লিখিত একমাত্র প্রবন্ধ ‘ছন্দ ও আবৃত্তি’ প্রকাশিত হয়েছিল ‘অরণি’ সাপ্তাহিকে ১৯৪৪ সালে। ছন্দকে জানা, বোঝা ও অনুভব করা, এমনকি বাংলা ছন্দের ইতিহাস জেনে, তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা একজন তরুন কবির পক্ষে অভাবিত, কিন্তু সুকান্তর পক্ষে তাই অনায়াস।
কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর ভাব ও ভঙ্গি স্বচ্ছ, সাবলীল – তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের প্রথম রাগিণী শুনেছিলেন এবং আপনার অপরিমিত প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে তৈরি করেছিলেন সাহিত্যের এক চিরন্তন সাঁকো – যা চিরস্থায়ী এবং কালোত্তীর্ণ। তাঁর রানার ছুটে চলে দিন থেকে দিনান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে তার যে – ‘সময় হয়েছে নতুন খবর আনার’। কিন্তু সুকান্ত শুধু স্বপ্ন দেখান না পথ ও নির্দেশ করেন, সে পথে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের আগুন, ভাঙে শৃঙ্খল, কঠিন হয় প্রতিজ্ঞা, ধ্বসে পড়ে অত্যাচারীর প্রাসাদের ভিত।
… “এ দাসত্ব ঘুচে যাক, এ কলঙ্ক মুছে যাক আজ,
কাজ কর – কাজ
মজুর দেখ নি তুমি? হে কলম দেখো নি বেকার?
বিদ্রোহ দেখনি তুমি? রক্তে কিছু পাও নি শেখার?……
কলম! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট, হোক অবশেষে;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়লে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম
আনো দিকে দিকে” ….
সুকান্ত ভট্টাচার্য; যার সময়কাল ১৯২৬ থেকে ১৯৪৭। মাত্র ২১ বছর। বঙ্গদেশে ২১ বছর বয়সে অনেক কবি প্রতিষ্ঠা পাওয়া তো দূরের কথা কবিতা লেখাই শুরু করেননি। ইংরেজকবি পার্সি বিশি শেলি (১৭৯২-১৮২২) ৩০ বছর এবং জন কিটস (১৭৯৫-১৮২১) ২৬ বছর বেঁচে ছিলেন। এদিক দিয়েও সুকান্তই বিশ্বসাহিত্যের একমাত্র কবি যিনি সবচেয়ে অল্প সময়ে কবিজীবন অতিবাহিত করেছেন। এই অতি অল্প সময়ে তিনি বাংলাসাহিত্যকে দিয়ে গেছেন এক অসাধারণ রত্ন ভান্ডার; যার মধ্যে আমরা পাই দেশপ্রেম, সমাজের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দূর্দশার চিত্র ও প্রতিবাদী চেতনা।
স্কুলজীবনে মাত্র নয় বছর বয়সে সুকান্তের প্রথম লেখা একটি গল্প হাতে লেখা পত্রিকা ‘সঞ্চয়’তে প্রকাশ পায়। সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালে লেখেন নাটক ‘ধ্রুব’। এই নাটকে তিনি অভিনয়ও করেন। সেই থেকে কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। সাংবাদিকতায় অসাধারণ মেধার পরিচয় রাখেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন ১৯৪৪ সালে। পরে দলটির মুখপত্র ‘দৈনিক স্বাধীন’ সম্পাদনা কাজে যোগ দেন। ১৯৪১ সালে যোগ দেন কলকাতা রেডিওতে।
“দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে লিখি কথা,
আমি যে বেকার পেয়েছি লেখার স্বাধীনতা…”
যেকোনো কলমসৈনিকের কলম ছুটিয়ে চলার অনুপ্রেরণা হিসেবে এ দু’টি কথা অনেক ইন্ধন জোগায়। ক্ষণজীবীতা যে কেবল ক্ষণজীবী প্রভাই ছড়ায় না, তার অনবদ্য দৃষ্টান্ত কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর কর্ম তাঁর বয়সকে, এমনকি তাঁর জীবনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং তাঁর এই অতিক্রান্ত প্রতিভা আজো দেদীপ্যমান বাংলা সাহিত্যে।
সুকান্তের পিতা নিবারন ভট্টাচার্য ও মা সুনীতি দেবী। তিনি জন্মেছিলেন ১৯২৬ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁর মাতামহের বাড়িতে – ৪৩, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলকাতায়। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার উনশিয়া গ্রামে। সুকান্তের পিতা ছিলেন সারস্বত লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী, যেটি ছিল একাধারে বইয়ের প্রকাশনা ও বিক্রয়কেন্দ্র। বিত্তের দিক দিয়ে সচ্ছলতা তাঁদের গৃহে কখনো আসেনি। সুকান্ত তাঁর ভাইদের মধ্যে ছিলেন দ্বিতীয়; অন্যরা হলেন মনমোহন, সুশীল, প্রশান্ত, বিভাস, অশোক ও অমিয়। সুকান্ত তাঁর বড় ভাই মনমোহন ভট্টাচার্য ও বৌদি সরযূ দেবীর সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলেন।
সুকান্তের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি ছিলেন তাঁর রাণীদি, সেসময়ের ‘রমলা’ খ্যাত জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক মণীন্দ্রলাল বসুর ‘সুকান্ত’ গল্পটি পড়ে রাণীদিই তাঁর নাম রেখেছিলেন ‘সুকান্ত’। সুকান্তের সবচেয়ে কাছের নারী ছিলেন তাঁর এই জেঠতুতো বোন। ছোট্ট সুকান্তকে গল্প-কবিতা শুনিয়ে তাঁকে সাহিত্যের প্রথম ছোঁয়া তিনিই দেন। হঠাৎ করে একদিন রাণীদি মারা গেলে সুকান্ত প্রচন্ড ধাক্কা খান, এর কিছুদিন পর তাঁর মাও চিরবিদায় নেন। একের পর এক মৃত্যুশোক যেন সুকান্তকে করে তুলেছিলো নিঃসঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতর … কবিতাই ছিল তাঁর একাকীত্বের সঙ্গী।
প্রেম কি সুকান্তের জীবনে আসেনি? ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তি’তে বন্ধু অরুণাচল বসু’কে লেখা একটা চিঠি সেই ইঙ্গিত করছে। চিঠিতে অবশ্য সুকান্ত তাঁর প্রিয় বন্ধুকে ‘প্রভূতআনন্দদায়কেষু’ বলে উল্লেখ করেছিলেন, কারণ এই সময় অরুণাচল বসুর সঙ্গে অর্থহীন অথচ বেশ ভারী ভারী শব্দ বানানোর খেলা চলছিল সুকান্তর। তখন কোনো কোনো লেখক অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দকে বাংলায় চালু করার চেষ্টা করছিলেন – তার প্রতি এটা ছিল দু’জনের কটাক্ষ। তিনি লিখেছিলেন –
‘‘… তুই আমাকে গ্রহ-বিচ্ছিন্ন উল্কার সঙ্গে তুলনা করেছিস- কিন্তু গ্রহটা কু গ্রহ, যেহেতু তার আগ্রহ আমায় নিক্ষেপ করা কোনো এক প্রশংসা-মুখর ক্ষেত্রে। যাই হোক, তোর এই চিঠিটা যেন নতুন জন্মের আভাস দিয়ে গেল। এখন শোন, যে “আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছে দান” তার পরিচয় :-এই পরিচয়পত্রের প্রারন্তেই তোর কাছে ক্ষমা চাইছি, তোর কাছে একদিন ছলনার প্রয়োজন হয়েছিল বলে। কিন্তু আর নয়, এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আর কপটতার আশ্রয় নিলুম না এই জন্যেই যে, কথাটা গোপন হলেও ব্যথাটা আর গোপন থাকতে চায় না, তোর কাছে- উলঙ্গ, উন্মুক্ত হয়ে পড়তে চায়। এ-ব্যাপারটা আমার প্রাণের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যে, তোর কাছেও তা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আবেগের বেগে সংযমের কঠিনতা গলে তা পানীয়রূপে প্রস্তুত হল তোর কৌতূহলে। তুই এ-প্রেমে ফেনায়িত কাহিনী-সুরা কি পান করবি না?- এই সুরার মূল্য যে শুধু সহানুভূতি ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস।
… কে তুই চিনিস, -যদি ‘না চিনি না’ বলিস তবে তাকে চিনিয়ে দিচ্ছি, সে উপক্রমণিকার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সর্বোপরি সে আমার আবাল্যের সঙ্গিনী, সঙ্গিনী ঠিক নয়, বান্ধবী। যখন আমরা পরস্পরের সমুখে উলঙ্গ হতে দ্বিধা বোধ করতাম না, সেই সুদূর শৈশব হতে সে আমার সাথী। সব কিছু মনে পড়ে না, তবু এইটুকু মনে পড়ে যে, আমরা একত্র হলে আনন্দ পেতুম এবং সে আনন্দ ছিল নানারকমের কথা বলায়। একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, আমাদের উভয়ের দেখা হত, কোনো কারণে, প্রায়ই। সে আমায় শ্রদ্ধা করত এবং আমার সান্নিধ্যে খুশি হত। একবার আমাদের উভয়কেই … যেতে হয়, সেখানেই আমরা আরো অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ি এবং আমি সেখান থেকেই লাভ করি ওর সান্নিধ্যের আকর্ষণ।
তখন আমার বয়স ১১, তার ৯। তারপর আমাদের দেখা হতে লাগল দীর্ঘদিন পরে পরে। … সেখানে আমি ঘনঘন যেতে লাগলুম। … ওর আকর্ষণে অবশ্যি নয়। বাস্তবিক আমাদের সস্পর্ক তখনও অন্য ধরনের ছিল, সস্পূর্ণ অকলঙ্ক, ভাই- বোনের মতোই। তখন ওকে নিয়ে যেতাম পার্কে বেড়াতে, উপক্রমণিকার বাড়ি ওকে পৌঁছে দিতাম দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। একত্রে আহার করতাম, পাশাপাশি শুয়ে বই পড়ে শোনাতাম ওকে, রাত্রেও পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোতাম। ঘুমের মধ্যে ওর হাতখানি আমার গায়ে এসে পড়ত, কিন্তু শিউরে উঠতাম না, ওর নিঃশ্বাস অনুভব করতাম বুকের কাছে। তখনো ভালবাসা কি জানতাম না আর ওকে যে ভালবাসা যায় অন্যভাবে, এ তো কল্পনাতীত। কোনো আবেগ ছিল না, ছিল না অনুভূতির লেশমাত্র। শেষে একদিন, যখন সবে এসে দাঁড়িয়েছি যৌবনের সিংহদ্বারে, এমনি একদিন, দিনটার তারিখ জানি না, পাশাপাশি শুয়েছিলাম, ঘুমিয়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি ভোর হচ্ছে আর সেই ভোরের আলোয় দেখলাম পার্শ্ববর্তিনীর মুখ। সেই নব প্রভাতের পাণ্ডুর আলোয় মুখখানি অনির্বচনীয়, অপূর্ব সুন্দর মনে হল। কেঁপে উঠল বুক, যৌবনের পদধ্বনিতে। হঠাৎ দেখি ও চাইল আমার দিকে চোখ মেলে, তারপর পাশ ফিরে শুল। আর আমি যেন চোরের মতো অপরাধী হয়ে পড়লাম ওর কাছে। লজ্জায় সেই থেকে আর কথা বলতে পারলাম না-আজ পর্যন্ত। … জিজ্ঞাসা করল, সুকান্ত কথা বলছে না কেন আমার সঙ্গে? … বহুবার চেষ্টা করল আমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে-কিন্তু আমারই বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল ওর ওপর, কেন জানি না (আমার বয়স তখন ছিল ১৩/১৪)।
এই বিতৃষ্ণা ছিল বহুদিন পর্যন্ত। আমিও কথা বলি নি। তারপর গত দু বছর আস্তে আস্তে যা গড়ে উঠেছে, সে ওর প্রতি আমার প্রেম। নতুন করে ভালবাসতে শুরু করলাম ওকে। বহুদিন থেকেই উপক্রমণিকাকে নিয়ে … রা আমাকে ঠাট্টা করত। আমার কাছে হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করল, উপক্রমণিকাকে তোর সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। আমি আপত্তি করলেও খুব বেশী আপত্তি করলাম না। এই জন্যে যে, ভেবে দেখলাম, আমার এই নব যৌবনে ভাল একজনকে যখন বাসতেই হয়ে তখন … এর চেয়ে বৈধ উপক্রমণিকাকে হৃদয়দান, সুতরাং সম্মত হওয়াই উচিত।
কেন জানি না, … নিজে আমাদের সঙ্গে মিলন সংঘটনের দায়িত্ব নিল। উপক্রমণিকাও একবার আমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজী হয়েও রাজী হল না। আমিও দু’তিনবার ওর প্রেমে পড়ে শেষে মোহমুক্ত হলাম তুই চলে যাবার পর। অর্থাৎ সম্প্রতি কয়েক মাস। এখন … কেই সস্পূর্ণ ভালবাসছি। … কে ভালবাসা যায় তা জানলাম, … প্রতি আমার এক নির্দোষ চিঠি এক বৌদির কাছে সন্দেহিত হওয়ায়। চিঠিটায় উচ্ছ্বাস ছিল সন্দেহ নেই, তাতে ছিল ওর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। কিন্তু তাতে সন্দেহ করা যায় দেখে বুঝলুম আমি ওকে ভালবাসতে পারি। যদিও আমার বোন ছিল না বলে ওর ভাইফোঁটা নিয়েছি দু’বার, আমাদের কথা বন্ধ হওয়ার পরও। আমি ওকে এখন ভালবাসি পরিপূর্ণ ও গভীরভাবে। ওর কথা আরও লিখব পরের চিঠিতে।’’
১৭ই এপ্রিল ১৯৪২ সালে আরেকটা চিঠিতে অরুণাচল বসুকে সুকান্ত লিখেছিলেন –
‘‘আশানুরূপেষু,
অরুণ, আজ আবার চিঠি লিখতে ইচ্ছে হল তোকে। আজকের চিঠিতে আমার কথাই অবিশ্যি প্রধান অংশ গ্রহণ করবে। এ জন্যে ক্ষুব্ধ হবি না তো? কারণ আজকে আমি তোকে জানাব আমার সমস্যার কথা, আমার বিপ্লবী অন্তর্জগতের কথা। এই চিঠির আরম্ভ এবং শেষ … তাঁর কথাতেই পরিপূর্ণ থাকবে। একবার যখন আদি-অন্ত জানতে কৌতূহল প্রকাশ করেছিস, তখন তোর এ চিঠি ধৈর্য ধরে পড়তেই হবে এবং আমার জন্যে মতামত আর উপদেশ পাঠাতে হবে।
আজকে এইমাত্র … তাঁর কথা ভাবছিলুম, ভাবতে-ভাবতে ভাবলুম তোকেই ডাকা যাক পরামর্শ এবং সমস্যা-সমাধানের জন্যে। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করব, আমার এই প্রেমের ওপর আস্থা ও সহানুভূতি তোর মনের কোণে বাসা বেঁধেছে কি? যদি না-বেঁধে থাকে, তবে এই চিঠি পড়া এখানেই বন্ধ করতে পারিস। যদিও তুই একবার আমাকে কৌতূহল জানিয়ে আমার মনের চোরা-কুঠুরীর দ্বার ইতিমধ্যেই ভেঙে দিয়েছিস, তবুও তোকে জিজ্ঞাসা করছি, আমার এই সমস্যার ওপর তোর কিছুমাত্র দরদ জেগেছে কি না। যদি জেগে থাকে তবে শোন:
আমার প্রধান সমস্যা, আমি আজও জানি না ও আমায় ভালবাসে কি না। কতদিন আমি ভেবেছি, ওর কাছে গিয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করব, এই কথার উত্তর চাইব; কিন্তু সাহস হয় নি। একদিন এগিয়েও ছিলাম, কিন্তু ওর শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে আমার কথা বলবার শক্তি হারিয়ে গেছল, অসাড়তা লাভ করেছিল চেতনা। ভাল ও আমায় বাসে কি জানি না, তবে সমীহ করে, এটা ভালরকম জানি।
আবার সন্দেহ হয়, হয়তো ও আমায় ভালবাসে এবং আমি সে ওকে ভালবাসি এটা ও জানে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে অনুভব করি ওর প্রেমহীনতা।
বাস্তবিক আমার প্রেমের বেদনা অভিনব। হয়তো আমি যে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি দেখি সেই সিঁড়ি দিয়েই ও নামছে, অবতরণকালীন ওর ক্ষণিক দৃষ্টি আমার চোখের ওপর পড়ে আমার বুকে স্নিগ্ধমধুর শিহরণ জাগিয়ে যায়। একটু আনন্দ, কিন্তু পরক্ষণেই বেদনায় মুষড়ে পড়ি। একটি ঘরে অনেক লোক, তার মধ্যে আমি যখন কথা বলি, তখন যদি দেখি ও আমার মুখের দিকে চেয়ে আমারই কথা শুনছে, তাহলে আমার কথা বলার চাতুর্য বাড়ে আরও বেশী, আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ি, এমনি ওর প্রতি আমার প্রেম। কিন্তু বড় ব্যথা।
বছর খানেক আগে আমার ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ঘটেছিল এবং আমিও সে সুযোগ অপব্যয়িত করি নি। অবিশ্যি ইতিপূর্বেই … তাঁর চেষ্টায় অস্বাভাবিকভাবে কথা বলার চেষ্টা আমাদের করতে হয়েছিল। ঘটনাটা তোকে একবার বলেছি, তবু বলছি আর একবার: একটা সভা-মতো করা হল, তাতে উপস্থিত থাকল …। সেই সভায় আমাদের কথা বলতে হল। প্রথমে সে তো লজ্জায় কথা বলতেই চায় না, শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করল, সিগারেট খাওয়ার অপকারিতা কী? আমি এতক্ষণ উদাস হয়ে (অর্থাৎ ভান করে) ওদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলুম, এইবার অতিকষ্টে জবাব দিতে থাকলুম। কিন্তু সেদিন আর আলাপ এগোয় নি।
এদিকে আমি উপলব্ধি করলুম ওর সঙ্গে কথা বলার অমৃতময়তা। তারপর থেকে ওর সঙ্গে আমার কথা বলার তৃষ্ণা অসীম হয়ে দেখা দিল এবং তৃষ্ণা আজও দূরীভূত হয় নি।
এর মাস খানেক পরে এল আর এক সুযোগ। আমাদের বেলেঘাটায় এল ও, কোনো কারণে। সারাদিন ও রইল কিন্তু কোনো কথা বললাম না ওর সঙ্গে। কিন্তু সন্ধ্যার পর এমন এক সময় এল যখন আমরা দুজনেই একটি ঘরে একা পড়ে গেলাম। দুইজনেই শুনছিলাম রেডিও। রেডিওতে গান হচ্ছিল, “প্রিয় আজো নয়, আজো নয়।” কিন্তু গানটাকে আমি লক্ষ্য করি নি এবং লক্ষ্য করার মতো মনের অবস্থাও তখন আমার ছিল না। কারণ কাছে, অতি কাছে ও বসেছিল, বোধহয় অন্যদিকে চেয়ে নিবিষ্ট মনে গানই শুনছিল, আর আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম ওকে, অত্যন্ত সুন্দর পোশাক-সজ্জিতা ওকে আমার বড় ভাল লাগল। ভেবে দেখলাম এক ঘরে থেকেও দুজনে কথা না বলা লোকচক্ষে নিতান্ত অশোভন। তাই অনেকক্ষণ ধরে মনে বল সঞ্চয় করে ডাকলুম – “…”! কিন্তু গলা দিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ কম্পিত স্বর বেরুল, ও তা শুনতে পেল না। এবার বেশ জোর দিয়েই ডাকলুম, ও তা শুনতে পেল। চমকে উঠে আমার দিকে চাইল। এবং আমিও এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত মুখস্থ করা কথাটা কোন রকমে বলে ফেললাম, “ইচ্ছে হলে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পার।”
ও মাথা নীচু করলে, কিছুই বললে না। মনে হল ও যেন রীতিমত ঘামছে। সেদিন আমার জীবনের শুভদিন ছিল, প্রাণভরে সেদিন ওর কথা পান করেছিলাম। তারও মাস খানেক পরে এসেছিল শেষ শুভদিন – সেদিন আমাদের কলকাতার প্রায় মাইল খানেক পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। মোটরে করে আমরা উপক্রমণিকার বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর ইচ্ছা ছিল, আমার সঙ্গে ও সেদিন উপক্রমণিকার আলাপ করিয়ে দেবে। সৌভাগ্যবশত: মোটরটা আমাদের সেখানে নামিয়েই ফিরে যায়। আর আমারও ফিরতি পথে দুজনের সঙ্গ অনুভব করলুম। সেদিন নেশা লেগে গিয়েছিল ওর সঙ্গে চলতে, কথা বলতে। মনে করে দেখ, কলকাতার রাজপথে একজন সুন্দরী-সুবেশা মেয়ের পাশে–পাশে চলা কি কম সৌভাগ্যের কথা! ওর পাশে চলে, ওর এত কাছে থেকে, যে আনন্দ সেদিন আমি পেয়েছি, তা আমার বাকী জীবনের পাথেয় থাকল। ও এখন বিমান আক্রমণের ভয়ে চলে গেছে সুদুর … তে। আর আমি তাই বিরহ-বিধুর হয়ে তোকে চিঠি লিখছি আর ভাবছি রবীন্দ্রনাথের দুটো লাইন –
“কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া
দুরে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া”
আমার দ্বিতীয় সমস্যা আরও ভয়ঙ্কর। যদি আমার আত্মীয়রা জানতে পারে একথা, তবে আমার লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না। বিশেষত, আমার বিশ্বাসঘাতকতায় … নিশ্চয়ই আমার সংস্পর্শ ত্যাগ করবে। অতএব এখন আমার কি করা কর্তব্য চিঠি পাওয়া মাত্র জানাস।
ইতি-
সুকান্ত ভট্টাচার্য”
সুকান্ত শৈশব কাটিয়েছেন বাগবাজারের তাঁদের নিবেদিতা লেনের বাড়িটিতে এবং সেখানকারই কমলা বিদ্যামন্দিরে তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভর্তি করা হয়। কমলা বিদ্যামন্দিরেই সুকান্তের সাহিত্যেও হাতেখড়ি হয়। বলা হয়ে থাকে, ‘উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়’ … সুকান্তের ক্ষেত্রেও এর ব্যাত্যয় ঘটেনি। শৈশবেই তাঁর সাহিত্যানুরাগ স্পষ্ট হতে থাকে, তাঁর প্রথম ছোটগল্প ছাপা হয় বিদ্যালয়েরই একটি পত্রিকা- ‘সঞ্চয়’ এ। স্থানীয় প্রাথমিক স্কুল কমলা বিদ্যামন্দিরে পড়ার সময় সেখানকার চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্ররা মিলে একটি হাতে লিখা পত্রিকা বের করে। সুকান্ত এই পত্রিকার নাম দেন “সঞ্চয়”, এতে তিনি নিজেও একটি হাসির গল্প লিখেন। ছেলেবেলাতে সুকান্ত অভিনয়েও পারদর্শীতা দেখান। স্কুলের নাটক “ধ্রুব”তে তিনি নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৯৪১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যান। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সুকান্ত রেডিওতে গল্পদাদুর আসর নামে এক অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করে প্রশংসা লাভ করেন সবার। কবিতাটি ছিল –
“এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।
এখনো স্বগত ভাবাবেগে,
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।” …
(রবীন্দ্রনাথের প্রতি, সুকান্ত ভট্টাচার্য, ছাড়পত্র।)
বাংলা সাহিত্যের মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী এবং প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রথম মুদ্রিত লেখা প্রকাশিত হয় বিজন কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘শিখা’ পত্রিকায় – বিবেকানন্দের জীবনী। শিখা পত্রিকায় সেসময় প্রায়ই সুকান্তের লেখা ছাপা হতো।
কমলা বিদ্যামন্দিরে লেখাপড়ার পাট চুকবার পর সুকান্ত ভর্তি হন বেলেঘাটা দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ে। সাম্যবাদে বিশ্বাসে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯৪২ সালে যোগ দেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে। সুকান্ত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ১৯৪৪ সাল থেকে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মাধ্যমে। ১৯৪৪ সালেই ‘ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’ এর প্রকাশনায় তিনি ‘আকাল’ নামে একটি সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন। ১৯৪৪ সালে সুকান্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৫ এর আগে তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে যান। ফলে ১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হন। সুকান্তের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অবসান হয় সেখানেই।
ছোটবেলা থেকেই বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন তাঁর একদম পছন্দ ছিলো না। জীবনের প্রতিটি অংশেই সুকান্ত যেন অনিয়মকে তাঁর নিয়ম করে নিয়েছিলেন। একদিকে পার্টির কাজ, অন্যদিকে কলমযুদ্ধ, অভাব অনটন … সব মিলিয়ে অনিয়মের স্রোত তার রুগ্ন শরীর মেনে নিতে পারেনি; যক্ষ্মারোগ বাসা বাঁধে এই অনিয়মের ফাঁকে ফাঁকে। সুকান্ত সূর্যের কাছে ‘রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেটিকে’ উত্তাপ দেবার জন্য পরম আকুতি জানিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু কখনো নিজেকে রক্ষার জন্য কারো কাছে হাত পাততে পারেননি। যে নিজেকেই মানবতার, আর্তের রক্ষক নিযুক্ত করেছে তাঁকে রক্ষা করবে কে? কেউ পারেনি, তাই সুকান্ত তাঁর জীবনাঙ্কের সবটুকু বেঁচে যেতে পারেননি। তাঁর রাজনৈতিক জীবন, তাঁর সাহিত্য জীবন এমনভাবে ‘ব্যক্তি সুকান্ত’কে গ্রাস করে নিয়েছিলো যে তাঁর ব্যক্তিজীবনকে থেমে যেতে হয় অকাল মৃত্যুতে।
সুকান্তের লেখনী গভীরভাবে প্রভাবিত হতো তাঁর সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে। চারপাশের মানুষকে নিয়ে সুকান্তের যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছিলো, তাই তিনি ঢেলে দিতেন কলমে-কাগজে। তাঁর অনুভূতিগুলো এতই প্রখর ছিলো যে তা প্রকাশ করতে গিয়ে কলম হয়ে উঠতো তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর। ‘ছাড়পত্র’ কাব্যগ্রন্থের ‘হে মহাজীবন’ কবিতাটিতে সুকান্ত পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটির সাথে তুলনা করেছেন, এ যেন আপামর জনতার ক্ষুধারই আক্ষরিক রূপ। পদ্য কী করে গদ্যের চেয়েও বেশি সত্য হয়ে ওঠে, সুকান্ত তো তা বারবারই দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর মূর্তমান কবিতায়। কবিতা যে শুধু অদেখা, অছোঁয়া বা বিমূর্তই নয় – সুকান্তের কবিতার মূর্ততা যে কোনও পাঠক-পাঠিকা তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়েও অনুভব করতে পারবেন।
“…পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার কর বশ্যতাকে।
চলো শুকনো হাড়ের বদলে সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে গজিয়ে উঠুক সিংহের কেশর, প্রত্যেকের ঘাড়ে” …
একজন লেখক অবশ্যই একজন ভালো পাঠক, এই বৈশিষ্ট্যটিও ছিল কবি সুকান্তের। অনেক বই পড়তেন তিনি। সুকান্তের প্রিয় বইয়ের তালিকায় বিভূতিভুষণ বন্দোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ বইটির স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। বইটি সম্পর্কে সুকান্ত বলেছিলেন, “ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সমান আদরে এই বই সকলের ঘরে রাখা উচিত”। সুকান্তের মনে সবসময়ই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি গভীর অনুরাগ কাজ করতো। একবার তো তিনি কলকাতায় মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে চলে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্য!
কলকাতা রেডিওতে প্রচারিত ‘গল্পদাদুর আসর’ অনুষ্ঠানটিতে সুকান্ত ছিলেন একজন নিয়মিত সভ্য, আনন্দবাজার পত্রিকার সভ্যতালিকাতেও ছিল সুকান্তের নাম। তাঁর বাল্যকালের সকল কাহিনীতেই দেখা মেলে তাঁর বন্ধু অরুণাচল বসুর, যিনি নিজেও একজন কবি। এও বলা যায় যে তাদের প্রথম সাহিত্যচর্চা ঘটেছিলো একসাথেই। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁদের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় একটি হাতে লেখা পত্রিকা – ‘সপ্তমিকা’। শিক্ষক নবদ্বীপচন্দ্রের স্মৃতিকথন থেকে সুকান্ত ও অরুণাচল বসুর ‘শতাব্দী’ নামে একটি যৌথ কবিতার কথাও জানা যায়। অরুণাচলের মা সরলা দেবীর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন সুকান্ত।
সুকান্ত ভট্টাচার্য কানে একটু কম শুনতেন ঠিকই, কিন্তু সর্বহারার আর্তচিৎকার শুনতে একদম ভুল করেননি! সুকান্তের কবিতার সহজ সরলতা অনেককে আশ্চর্য ও মুগ্ধ করেছে, সেই সরলতার সমগ্র তাৎপর্য সকলের কাছে ধরা পড়েনি; কারণ আমরা শুধু প্রকাশভঙ্গিটাই বুঝতে চাই – বার্তাটি নয়!
সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু সুকান্তের বর্ণনা দিয়েছেন এমন করে, “গর্কীর মতো, তাঁর চেহারাই যেন চিরাচরিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কানে একটু কম শোনে, কথা বেশি বলেনা, দেখামাত্র প্রেমে পড়ার মতো কিছু নয়, কিন্তু হাসিটি মধুর, ঠোঁট দু’টি সরল”। বুদ্ধদেব বসু সুকান্তের কথা আরো বলেছেন, “যে চিলকে সে ব্যঙ্গ করেছিলো, সে জানতো না সে নিজেই সেই চিল; লোভী নয়, দস্যু নয়, গর্বিত নিঃসঙ্গ আকাশচারী, স্খলিত হয়ে পড়লো ফুটপাতের ভিড়ে, আর উড়তে পারলো না, অথবা সময় পেলো না। কবি হবার জন্যই জন্মেছিলো সুকান্ত, কবি হতে পারার আগে তাঁর মৃত্যু হল”।
কবিতার পৃষ্ঠায় সুকান্তই সূর্যকে বলতে পেরেছিলেন, “হে সূর্য তুমি ত জানো আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!”, সিগারেটকে আহবান জানাতে পেরেছিলেন ‘হঠাৎ জ্বলে উঠে বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে’ মারতে, ‘যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছ এতকাল’; সুকান্ত কেঁদেছেন ডাকঘরের রানারের দুঃখে – ‘পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া!’
কলকাতা শহরকে নিয়ে এক অদ্ভূত আতিশয্য কাজ করতো সুকান্তের মাঝে, কলকাতাকে এক রহস্যময়ী নারী ভেবে ভালবেসেছেন তিনি। কলকাতা তার প্রেয়সী, কলকাতা তাঁর হারিয়ে যাওয়া মা। তার বাইরের কোনো জগত ছিলো না, যা ছিল তা এই কলকাতাতেই। সুকান্তের জগত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো কলকাতার অলিতে গলিতে। তিনি বাঁচতে চাইতেন কলকাতাকে নিয়ে, কলকাতার মৃত্যু তাঁর জীবনেরও ইতি টানবে এই বিশ্বাস ছিলো সুকান্তের …। একটা চিঠিতে (২৪শে পৌষ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু ও কবি অরুণাচল বসুর কাছে প্রিয় শহর কলকাতাকে নিয়ে লিখেছিলেন –
‘‘ … কলকাতাকে আমি ভালবেসেছিলাম, একটা রহস্যময় নারীর মতো, ভালবেসেছিলাম প্রিয়ার মতো, মায়ের মতো। তার গর্ভে জন্মানোর পর আমার জীবন এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উষ্ণ-নিবিড় বুকের সান্নিধ্যে; তার স্পর্শে আমি জেগেছি, তার স্পর্শে অমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না, আমার পৃথিবী আমার কলকাতার মধ্যেই সস্পূর্ণ। একদিন হয়তো এ পৃথিবীতে থাকব না, কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি যে কলকাতায় বসে কলকাতাকে উপভোগ করছি! সত্যি অরুণ, বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হব। “মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।” কিন্তু মৃত্যু. ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদিন সে ষড়যন্ত্র করছে সভ্যতার সঙ্গে। তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে।
আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে। শুধু তখন থাকব না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবু তো জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম। … এই আমার আজকের সান্ত্বনা। তুমি চলে যাবার দিন আমার দেখা পাও নি কেন জান? শুধু আমার নির্লিপ্ত উদাসীনতার জন্যে। ভেবে দেখলাম কোনো লাভ নেই সেই দেখা করায়, তবু কেন মিছিমিছি মন খারাপ করব? …’’
সুকান্তের জীবন ও কাব্য ছিলো একই সুরে গ্রথিত ও একই মন্ত্রে অনুরণিত। তাই কোন এক অংশকে আলাদা করে বলা যায় না … বলতে হলে সমান্তরালভাবে, একসাথেই বলতে হয়। সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কোন বইই প্রকাশিত হবার পর দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ‘ছাড়পত্র’, এবং এরপর অন্যগুলোও।
কবির বয়স যখন মাত্র ২১ তখন পার্টি ও সংগঠনের কাজে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে দুরারোগ্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৯৪৭ সালের ১৩ই মে কলকাতায় যাদবপুর টি বি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।
৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৭ সালে নিজের জীবনের শেষ চিঠিটা লিখেছিলেন সুকান্ত, নিজের জনৈক বন্ধুকে, যাদবপুর টিবি হাসপাতাল থেকে। তাঁর শেষ পত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি কতটা একা ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন –
‘‘বন্ধুবরেষু,
সাতদিন কেটে গেল এখানে এসেছি। বড় একা ঠেকছে এখানে। সারাদিন চুপচাপ কাটাতে হয়। বিকেলের প্রতীক্ষায় থাকি, যদি কেউ আসে। সুভাষদা নিয়মিত আসছেন না, কেবল আমার জ্যাঠতুতো দাদাই নিয়মিত আসছেন। আপনি কবে আমার সঙ্গে দেখা করছেন? এখানে এলে “লেডী মেরী হার্বাট” ব্লকে আমার খোঁজ করবেন, আমার বেডের নম্বর ‘এক’। শিয়ালদা দিয়ে ট্রেনে অথবা কলেজ স্ট্রিটের মোড় থেকে ৮ এ বাসে করে আসতে পারেন।
–সুকান্ত ভট্টাচার্য’’
চিঠিতে ‘সুভাষদা’ হলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।
কবির জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছিল কলকাতার বেলেঘাটার ৩৪ হরমোহন ঘোষ লেনের বাড়ীতে। সেই বাড়িটি এখনো অক্ষত আছে। পাশের বাড়ীটিতে এখনো বসবাস করেন সুকান্ত ভট্টাচার্য একমাত্র জীবিত ভাই বিভাস ভট্টাচার্য।
সুকান্তর অকালমৃত্যুর পর জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন,
“… যে কবির বাণী শোনবার জন্যে কবিগুরু কান পেতেছিলেন সুকান্ত সেই কবি। সৌখিন মজদুরি নয়, কৃষাণের জীবনের সে ছিল সত্যকার শরিক, কর্মে ও কথায় তাঁদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল তাঁর, মাটির রসে ঋদ্ধ ও পুষ্ট তাঁর দেহমন। মাটির বুক থেকে উঠে এসেছিল।”
◆ কাব্যগ্রন্থ ~
ছাড়পত্র (১৯৪৭)
পূর্বাভাস (১৯৫০)
ঘুম নেই (১৯৫০)
◆ ছড়া ~
মিঠে কড়া (১৯৫২)
◆ সংগীত ~
গীতিগুচ্ছ
গীতিআলেখ্য
অভিযান
সূর্য-প্রণাম
◆ অগ্রন্থিত গান ~
বর্ষ-বাণী
যেমন ক’রে তপন টানে জল
জনযুদ্ধের গান
আমরা জেগেছি আমরা লেগেছি কাজে
শৃঙ্খল ভাঙা সুর বাজে পায়ে
◆ অগ্রন্থিত গল্প ~
ক্ষুধা
দুর্বোধ্য
ভদ্রলোক
দরদী কিশোর
কিশোরের স্বপ্ন
◆ প্রবন্ধ ~
ছন্দ ও আবৃত্তি
পত্রাবলী
পত্র-গুচ্ছ
◆ অগ্রন্থিত কবিতা ~
ভবিষ্যতে
সুচিকিৎসা
পরিচয়
আজিকার দিন কেটে যায়
চৈত্রদিনের গান
সুহৃদ্বরেষু
পটভূমি
ভারতীয় জীবনত্রাণ-সমাজের মহাপ্রয়াণে
নব জ্যামিতির ছড়া
জবাব
চরমপত্র
মেজদাকে: মুক্তির অভিনন্দন
পত্র
মার্শাল তিতোর প্রতি
ব্যর্থতা
দেবদারু গাছে রোদের ঝলক
(তথ্যসূত্র:
১- সুকান্ত ভট্টাচার্য: পাঠ ও পুনর্পাঠ, শান্তনু কায়সার, রূপসী বাংলা প্রকাশ (২০১৫)।
২- কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, লুৎফর চৌধুরী, হাতেখড়ি।
৩- উইকিপিডিয়া।)
মতামত লেখকের ব্যক্তিগত