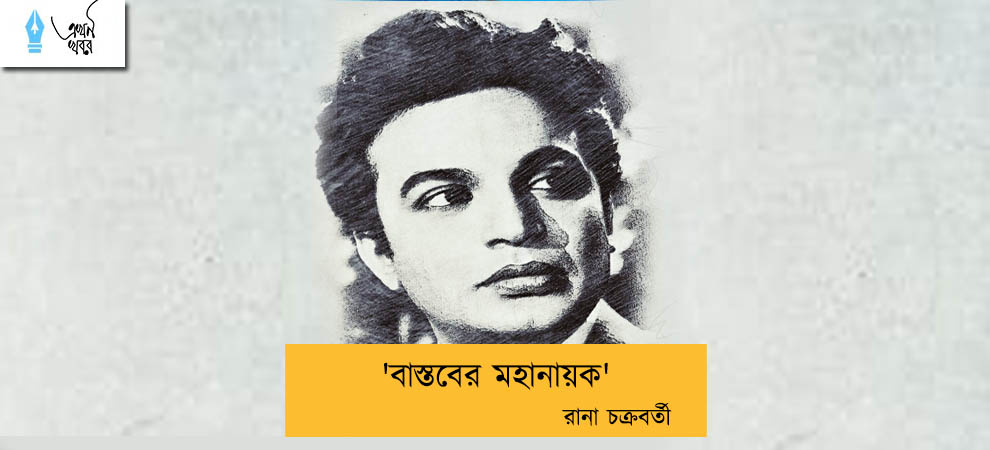১৯৫৩ সাল।
সাহিত্যিক শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর ‘শ্যামলী’ উপন্যাস নিয়ে তৈরি হল ‘শ্যামলী’ নাটকটি। নায়ক উত্তমকুমার, নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। দেখা গেল, শুধু জনপ্রিয়তা নয়, এই নাটক বাংলা থিয়েটারেই এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। অন্য দিকে ১৯৫৬ সালে এই নাটককেই পর্দায় নিয়ে এলেন পরিচালক অজয় কর। উত্তমকুমার ও কাবেরী বসু অভিনীত এই চলচ্চিত্রটি দর্শকদের কাছে হয়ে গেল আর এক বিস্ময়। একে একে নিরুপমা দেবীর লেখা উপন্যাস থেকে তৈরি হতে থাকল ‘অন্নপূর্ণার মন্দির’, ‘দেবত্র’, ‘বিধিলিপি’র মতো চলচ্চিত্র। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনি যেমন বাংলার চলচ্চিত্রকারদের কাছে ছিল নিশ্চিত সাফল্যের আশ্বাস, একই কথা বলা হত নিরুপমা দেবীর ক্ষেত্রেও। দুঃখের বিষয়, এই জনপ্রিয়তা তিনি দেখে যেতে পারেননি।
স্টারে ‘শ্যামলী’ নাটকটিতে অভিনয় করার পরে উত্তমকুমারের নাম হয়ে গিয়েছিল শ্যামল। না, নামটি সাধারণ অনুরাগীবৃন্দ দেননি। দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়! এ নাটক দেখে বিধানচন্দ্র এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে নাটক শেষে গ্রিনরুমে গিয়ে উত্তমকে জানিয়ে আসেন যে এরপর থেকে তিনি উত্তমকে ‘শ্যামল’ বলেই ডাকবেন।
নাটকে অবশ্য উত্তমকুমার অভিনীত চরিত্রটির নাম ছিল অনিল। নিরুপমা দেবী লিখিত কাহিনীতে এ চরিত্রটি আধুনিক–মনস্ক, সংস্কারমুক্ত এক যুবা, যে এক অসহায় বোবা মেয়েকে বিয়ে করছে, সেই মেয়েই শ্যামলী। চরিত্রটি করতেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। শত প্ররোচনাতেও অনিল অগ্নিসাক্ষী করা স্ত্রী শ্যামলীকে ছাড়তে রাজি নয়। আবার এই নাটকে অনিলের মা সরলার চরিত্র করতেন নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী। যাঁকে উত্তম ‘সরযূ মা’ বলে ডাকতেন। শোনা যায়, এ নাটক দেখার পর বহু মহিলা দর্শকই বলতেন, আমার যদি উত্তমের মতো একটা ছেলে থাকত।
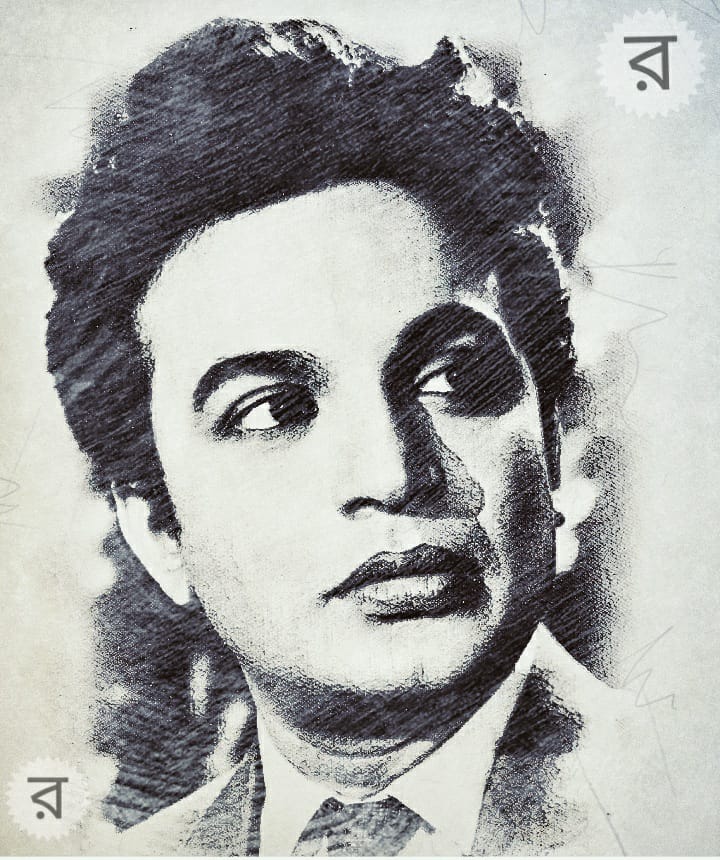
‘শ্যামলী’ প্রথমবার মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৩–র দুর্গাপুজোর ভেতর। ১৫ অক্টোবর তখন পুজোতে নতুন নাটক নামত ‘বোর্ড’ মানে বাণিজ্যিক থিয়েটারে। তখনও পর্যন্ত উত্তমের হিট বলতে দুটোই ছবি— ‘বসু পরিবার’ আর ‘সাড়ে ৭৪’। দায়িত্ববান স্বামী আবার একই সঙ্গে নিষ্ঠাবান পুত্র— এমন একটি রসায়নে ভেজা চরিত্র অনিল, সন্দেহ নেই উত্তমের ‘পারিবারিক হিরো’র কেরিয়ারে বাড়তি আঁচ জুগিয়েছিল। এ নাটকে ৪৮৪ রজনী নায়ক সাজতেন উত্তম। টানা তিন বছর জুড়ে। যখন শো করা বন্ধ করেন, তখন তিনি বাংলা ছবির ‘সুপারস্টার’।
পাঁচশো রজনী পূর্ণ হতে তখন আর মাত্র ১৬টি শো বাকি। সপ্তাহে চারটি করে শো হত এ নাটকের। মানে আর এক মাস শো হলেই ‘মাইলস্টোন’টি ছুঁড়ে ফেলত ‘শ্যামলী’। তখনও এ সৌভাগ্য কোনও নাটকের হয়নি। অথচ এমন সময়ে কেন এ নাটক ছাড়লেন উত্তম?
সে সময়ে একটি ‘গুজব’ বাজারে উড়ছিল। উত্তমের সঙ্গে নায়িকা সাবিত্রীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। রটেছিল পারিবারিক অশান্তির জেরে নাকি মঞ্চ ছাড়লেন উত্তম। কিন্তু যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা হল মঞ্চেই উত্তমের অসুস্থ হয়ে পড়া। শো কোনওরকমে শেষ করেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। বন্ধু ডাক্তার লালমোহন মুখোপাধ্যায় পরীক্ষা করে বোঝেন উত্তমের ‘প্যারাটাইফয়েড’ হয়েছে। এতে শরীর এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে উত্তমের যে মঞ্চের ধকল নেওয়া আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে ‘শ্যামলী’র অনিল বদলায়। উত্তমের জায়গায় আসেন নবকুমার। নবকুমার ছিলেন মঞ্চের নামী অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর ছেলে। বেশ কিছু সিনেমাও করেছেন। কিন্তু ওই চরিত্রে উত্তম ছাড়া আর কাউকেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না দর্শক। ফলে, টিকিট বিক্রি কমল। উত্তম সে খবর পেয়ে ‘স্টার থিয়েটার’–এর প্রতি মমত্ববশতঃ ফিরে আসেন বটে আবার এ নাটকে, তবে তা সামান্য কিছুদিনের জন্য।
আর তখন উত্তমকে ঘিরে যে পাগলামি শুরু হয়েছে অনুরাগীদের, তার চাপ আছড়ে পড়ত হলে উত্তমের ঢোকা–বেরনোর সময়ে। সবাই উত্তমকে একটু ছুঁতে চান। ফলে পুলিস পিকেট করে ঢোকা–বেরনো করতে হত। ‘শ্যামলী’ আর বেশিদিন চলেনি। পরে ‘শ্যামলী’ সিনেমায় বানান অজয় কর।
স্টার থিয়েটারে উত্তমের যোগদান নিয়ে দুটো ঘটনার কথা জানা যায়।
এক, অ্যামেচার থিয়েটারের ব্যাপারে কয়েকটি বিরক্তির কথা উত্তম একবার জহর গাঙ্গুলিকে বলেন, তখন তাঁরা বিখ্যাত নাটক থেকে তৈরি চিত্রনাট্য ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’–এর শুটিং করছেন। জহরবাবু উত্তমকে পরামর্শ দেন, বাণিজ্যিক থিয়েটারে যোগ দিতে। বলেন, এখানে একেবারে সরাসরি দর্শকের হাটে অভিনেতা নিজের অভিনয় ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার পরিমাপ করে নিতে পারেন। স্টার কর্তৃপক্ষকেও তিনি উত্তমের কথা বলেন।
দুই, উত্তমকে স্টারে আনার ব্যাপারে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়েরও একটা ভূমিকা ছিল। ছবি বিশ্বাস তখন স্টার থিয়েটার ছেড়ে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন। এই দুই থিয়েটারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বজনবিদিত। ছবিবাবু তখন করছেন মিনার্ভায় ‘ঝিন্দের বন্দী’। নিজে প্রধান দ্বৈত চরিত্রে আর ময়ুরবাহনের চরিত্রে আনবেন ভাবছেন উত্তমকে। এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে স্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সাবিত্রী উত্তমকে আনান ‘শ্যামলী’–তে।
‘শ্যামলী’তে অভিনয় করতেন উত্তমের একদা অভিনয়–শিক্ষক সন্তোষ সিংহও। নাট্যকার ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। যিনি এর আগে উত্তমের ‘স্ট্রাগলিং’ পিরিয়ডেই ফিল্মের সেটে তাঁকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন দুর্গাদাসের পরে বাঙালি নতুন নায়ক পেতে চলেছে। রঙমহলের সফল নাট্যকার দেবনারায়ণ সেই প্রথম এসেছেন স্টারে। নতুন চ্যালেঞ্জ তাঁর সামনে। আর বহু খরচ করে সেই প্রথম মঞ্চে ‘রিভলবিং ডিস্ক’ লাগিয়েছেন স্টারের মালিক সলিল মিত্র (এ জন্য এই নাটকের বুকলেটের প্রচ্ছদে থাকত একটি ঘূর্ণায়মান বৃত্তের ছবি।) ফলে খরচ তোলার চ্যালেঞ্জ সলিলবাবুর সামনেও।
সব চ্যালেঞ্জই উতরে দিয়েছিলেন উত্তমকুমার।
বিজ্ঞাপনে যাঁর নামের পাশে ‘ফিল্ম’ কথাটা ব্র্যাকেটে লেখা থাকত। ঘনিষ্ঠদের কেউ কেউ বিজ্ঞাপনে তাঁর নামটা দু–একজনের পরে যাচ্ছে বলে অনুযোগ করলে, ঈষৎ হেসে উত্তম বলতেন, বিজ্ঞাপনটা না দেখে কাজটা দেখ। ‘শ্যামলী’ চলত বৃহস্পতি–শনি–রবি। এর আগে বুধবার করে অন্য একটি নাটক চালাত স্টার কর্তৃপক্ষ। তাকে বলা হত মধ্য–সাপ্তাহিক নাটক। ‘শ্যামলী’র জনপ্রিয়তায় মধ্য–সাপ্তাহিক নাটক বন্ধ হয়ে গেল স্টারে। আরও একটি প্রথা বদলাল। শনি–রবির টিকিটের থেকে দাম কম থাকত বৃহস্পতিবার। একে বলা হত ‘চিপ থিয়েটার’। ‘শ্যামলী’ এসে বৃহস্পতিবারের টিকিটের দামও সমান করে দিল।
স্টার ছাড়বার সময় ‘শ্যামলী’র স্ক্রিপ্টটি সেখানে অফিসঘরে রেখে আসেন দেবনারায়ণবাবু। স্টারে যখন আগুন লাগে, ভস্মীভূত হয়ে যায় সেটাও।
উত্তমের গ্রুপ থিয়েটার ‘শ্যামলী’ শুধু উত্তমের বাণিজ্যিক মঞ্চে অভিষেক ঘটায়নি, ঘটিয়েছিল আরও দুজনের। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মজার কথা হল, এটা অনেকেই জানেন না, এঁরা তিনজনেই এর আগে একই দলে থিয়েটার করেছেন। সে দলের নাম ‘কৃষ্টি ও সৃষ্টি’। দলের মহলাঘর ছিল শ্যামবাজারে। দর্পণা সিনেমার পাশের গলিতে। অফিস সেরেই দৌড়ে আসতেন উত্তর কলকাতায়। মহলায়। বন্ধু শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌলতে এই দলে আসা তাঁর। দলের আগে নাম ছিল ‘হুজুগে সঙ্ঘ’। পরে নাম বদলে ‘কৃষ্টি ও সৃষ্টি’। এই দলে উত্তম আর সাবিত্রীর একসঙ্গে প্রথম নাটক ছিল ভানু চট্টোপাধ্যায়ের (বন্দ্যোপাধ্যায় নন) ‘আজকাল’। সাবিত্রী তখন ‘উত্তর সারথী’ নামের এক দলের প্রযোজনায় অভিনয় করেন ‘নতুন ইহুদি’ নাটকে। তাতে অভিনয় করেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ভানুবাবুই একদিন বন্ধু উত্তমকে নিয়ে এলেন স্টেজ রিহার্সাল দেখাতে। তখন অরুণ চট্টোপাধ্যায় উত্তমকুমার হননি। সাবিত্রীর অভিনয় মুগ্ধ করল তাঁকে। সাবিত্রী দেবীর বাবার সঙ্গে কথা বললেন তাঁকে দলে পাওয়ার জন্য। বাবা বললেন মেয়েকে মহলায় নিয়ে যেতে হবে এবং পৌঁছে দিতে হবে কাউকে, স্বয়ং উত্তম বা অরুণই সেই দায়িত্ব নিলেন।
এই দলেই এরপর সাবিত্রী–উত্তম একসঙ্গে করেছেন ‘কঙ্কাবতীর ঘাট’। যাতে অভিনয় করতেন উত্তমের আরেক বন্ধু সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। করেছেন ‘কানাগলি’। এ নাটকে শেষ দৃশ্যে এত তন্ময় হয়ে অভিনয় করতেন উত্তম, শোনা যায় মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন! ফলে ‘শ্যামলী’তে দুজনের সাফল্য ছিল আসলে অবাণিজ্যিক থিয়েটারেরই জয়।
উত্তম–সাবিত্রী আরেকবার অবাণিজ্যিক থিয়েটারে একসঙ্গে নেমেছেন। আর তা ‘শ্যামলী’–তেই! আর সে নাটক করা নিয়ে স্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উত্তমের সম্পর্ক ভাঙে ভাঙে আর কি! নাটক তখন সবে শত রজনী পার করেছে।
উত্তমের পাড়ার নাট্যদল ছিল লুনার ক্লাব। এখানেই নাটক নিয়ে তাঁর পরীক্ষা–নিরীক্ষার হাতেখড়ি। উত্তম পুরনো নাটক দেখতেন, বয়স্কদের সঙ্গে করতেনও, কিন্তু পুরনো থিয়েটারের ধরাবাঁধা ছক, লম্ফঝম্ফ আর কৃত্রিম স্বরক্ষেপণে অভিনয় তাঁর না–পসন্দ ছিল। চাইতেন সহজ স্বাভাবিক অভিনয়। যা ধরা আছে সত্যজিৎ রায়ের ‘নায়ক’ সিনেমার ভেতর এক মঞ্চাভিনয়ের দৃশ্যে। আর তাই সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে এই ‘লুনার ক্লাব’ গড়া। এখানে ‘সাজাহান’ নাটকে উত্তম হয়েছেন দিলদার, ‘কর্ণার্জুন’–এ শ্রীকৃষ্ণ, ‘দুই পুরুষ’–এ সুশোভন।
তা, এই লুনার ক্লাবের সে বছর সিলভার জুবিলি। উত্তম ঠিক করলেন ‘শ্যামলী’ হবে। সাবিত্রী থাকবেন, উত্তম নিজে থাকবেন। আর থাকবেন তাঁর বন্ধুরা। কথাটা জানতে পেরে সলিল মিত্র দুই পরিচালক শিশির মল্লিক আর যামিনী মিত্রকে দিয়ে বারণ করালেন। কিন্তু উত্তম বললেন এ নাটক করতে না দিলে তিনি দরকারে স্টার ছেড়ে দেবেন। সরযূবালা উত্তমের পাশে দাঁড়ালেন। আর দাঁড়ালেন টেকনিশিয়ানেরা। ‘শ্যামলী’ হল শেষমেশ লুনার ক্লাবে।
১৯৬৮–তে দেবনারায়ণ গুপ্তকে ফোন করে উত্তম চেয়েছিলেন আরেকবার স্টারে ফিরে আসতে। বলেছিলেন একটা নাটক লিখতে যাতে তাঁর চার–পাঁচটা ‘এন্ট্রি’ থাকবে। সে নাটক অবশ্য হয়নি।
কিন্তু উত্তম তাঁর নাট্যক্ষুধা মিটিয়ে নিয়েছিলেন নবগঠিত ‘শিল্পী সাংসদ’–এর মাধ্যমে। প্রতি বছর নাটক নামত এই ব্যানারে। নাট্য–শিল্পীদের সংবর্ধনা দেওয়া হত। কোনও কারণে টাকা তোলার দরকার হলেই নাটক নামত।
১৯৭২ সালে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তিতে ‘শিল্পী সংসদ’ পর পর তিন সন্ধ্যায় নামাল তিনটি নাটক। বিশ্বরূপা মঞ্চে। তিনটিরই পরিচালক উত্তমকুমার। ‘চারণকবি মুকুন্দ দাস’, ‘সাজাহান’ (এতে নাম ভূমিকায় ঠাকুরদা মিত্র, ঔরঙ্গজেব মহেন্দ্র গুপ্ত আর দিলদারে বিকাশ রায়), ‘চরিত্রহীন’। তিনটিই ‘ক্লাসিক’ নাটক। এর কোনওটাতে অভিনয় করেননি অবশ্য উত্তম। তবে সে খেদ মিটল পরের বার। ‘আলিবাবা’ নাটকে। এ নাটকে জয়শ্রী সেন মর্জিনা। আর দু’দৃশ্যের মজার চরিত্র বাবা মুস্তাফা স্বয়ং উত্তমকুমার। রবীন্দ্রসদনে শো হল। নাটককে ভালবেসে রোমান্সের রাজা তখন মঞ্চে কুৎসিতদর্শন এক বৃদ্ধ মুচি! চমকে গিয়েছিল দর্শক।
মনে পড়ে ১৯৬৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত, লেখক ও সাহিত্যিক শঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি পরিচালক পিনাকী ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘চৌরঙ্গী’ চলচ্চিত্রে কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী শ্রী মান্না দে’র গাওয়া ‘বড় একা লাগে এই আঁধারে’ গানটি?
পিনাকীবাবু প্রথমে আপত্তি করেছিলেন ‘বড় একা লাগে’ গানটিতে, কিন্তু তারপর উত্তমকুমারের অনুরোধে সে-গান রেকর্ড হয়। গান তো রেকর্ড হল, শ্যুটিংও হল। কিন্তু তা সত্বেও পরিচালক পিনাকী মুখার্জি বলেছিলেন, ‘না, এ গানটা সিচুয়েশনের সঙ্গে যাচ্ছে না। সিনটা ফেলে দিতে হবে।’
সকলের মাথায় হাত। কিন্তু পরিচালকের উপরে কথা বলা যায় না। আর কথা বলবেনই বা কে?
গানটি রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন স্বয়ং মহানায়ক।
গায়ক মান্না দে সমেত অন্যান্যদের মন খারাপ দেখে মহানায়ক উত্তম কুমার বলেছিলেন, ‘সবাই চুপচাপ থাকুন। ওই একই সেটে আমার অন্য সিন যেদিন শ্যুট হবে, এই গানটা আমি আর একবার শ্যুট করিয়ে নেব। পরিচালককে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার।’
যে কথা সেই কাজ। গানটি দ্বিতীয়বার শ্যুট হয়েছিল। উত্তমকুমার নিজে অনেক সাজেশন দিয়ে কাজটি করিয়েছিলেন।
গানটির রেকর্ডিং হয়েছিল ১৯৬৭-তে, নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর স্টুডিওতে। প্রায় বাতিল হওয়া সেই গান আজও সমান জনপ্রিয়। বাংলা চলচ্চিত্রের গানের জগতে এক ইতিহাস।
ভাগ্যিস মহানায়ক ছিলেন।
সত্তরের দশকের শেষাশেষি।
খ্যাতির মধ্য গগনে তখন উত্তমকুমার। এক দিন হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বললেন, ‘দূর আর ভাল লাগছে না!’
শুনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন সৌমিত্র।
তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন ‘‘বুড়োর রোলগুলো করতে হবে না? কোত্থেকে হবে, এখন থেকেই ভাল না লাগলে? আপনি আর আমি বুড়ো না হলে ইন্ডাস্ট্রিতে ভাল বুড়ো পাওয়া যাবে না!’’
শুনে হাসতে শুরু করেন উত্তম।
না! উত্তমের আর বুড়ো হয়ে ওঠা হয়নি।
যেদিন তিনি চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন, ঠিক তার দুই দিন পরে, ১৯৮০ সালের ২৬শে জুলাই, তাঁর স্মৃতিচারণে আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘নায়ক’ স্রষ্টা শ্রী সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন,
“উত্তমকুমারকে যখন প্রথম ছবিতে দেখি তখনও আমি নিজে ছবির জগতে আসিনি। নতুন একটি হিরোর আবির্ভাব হয়েছে বলে শুনছিলাম, ছবিটিও নাকি ভাল, তাই স্বাভাবিক তাগিদেই গেলাম ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ দেখতে। নির্মল দে-র ছবি, পরিচ্ছন্ন পরিচালনা, আঁটসাট চিত্রনাট্য। এই বিশেষ পরিচালকের কাজ ভাল লেগেছিল বলেই পরে দেখলাম ‘বসু পরিবার’ ও ‘চাঁপাডাঙার বউ’। তিনখানা ছবি পর পর দেখে, মনে হল উত্তমকুমারের অভিনয় ও ব্যক্তিত্বে সত্যিই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের দুর্গাদাস, প্রমথেশ, ধীরাজ, জহর গাঙ্গুলী প্রমুখের কাজের সঙ্গে এর বিশেষ মিল নেই। মনে হল ছেলেটি হলিউডের ছবি-টবি দেখে। অভিনয়ে থিয়েটারের গন্ধ নেই, চলায়-বলায় বেশ একটা সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য। ক্যামেরা বস্তুটিকে যেন বিশেষ তোয়াক্কা করে না। তার উপরে চেহারায় ও হাবেভাবে বেশ একটা মন টেনে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। উত্তমকুমারের ভবিষ্যৎ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।
এর দশ-বারো বছর পর উত্তমকুমারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আসে আমার। ইতিমধ্যে উত্তম-সুচিত্রার রোম্যান্টিক জুটি দর্শকদের মন জয় করেছে। লেখক পরিচালক প্রযোজক দর্শক সকলের চাহিদা চলে গেছে প্রেমের গল্পের দিকে। ‘অগ্নিপরীক্ষা’ বা ‘হারানো সুর’ দেখে এটা বুঝেছিলাম যে এই জুটির সাফল্যের পিছনে লেখক প্রযোজক পরিচালক দর্শক সমালোচক ফিল্ম-পত্রিকা সম্পাদক ইত্যাদি সকলের যতই অবদান থাকুক না কেন, এদের দু’জনের মধ্যেই এমন সব গুণ বর্তমান, যার রাসায়নিক সংমিশ্রণে সোনা ফলতে বাধ্য। শুধু উত্তমের কথা বলতে গেলে এটা বলা যায় যে, নায়িকার সান্নিধ্যে এলেই অনেক নায়কের মধ্যেই সিঁটিয়ে যাওয়ার ভাবটা ক্যামেরায় অব্যর্থ ভাবে ধরা পড়ে, উত্তমকুমারের মধ্যে সেটি নেই। বরং প্রেমের দৃশ্যে এঁর অভিনয় খোলে সবচেয়ে বেশি। নারী-পুরুষের সম্পর্ক যেখানে চিত্রকাহিনির অন্যতম প্রধান উপাদান, সেখানে এটা যে কত বড় গুণ সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।
‘নায়ক’-এর গল্প আমি লিখি উত্তমকুমারের কথা ভেবেই। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এক অভিনয়-পাগল যুবক ছবিতে নেমে তরতরিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। এই অবস্থায় এই যুবকের মনে কী ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, তার মূল্যবোধে কী পরিবর্তন হতে পারে, এও ছিল গল্পের বিষয়।
চিত্রনাট্য শুনে উত্তম খুশি হয়। তার একটা কারণ হতে পারে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে কাহিনির সাদৃশ্য। আলোচনা করে বুঝলাম যে গল্পের গভীরে প্রবেশ করতে না চাইলেও, বা না পারলেও, তাঁর চরিত্রটি কীভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে সেটা উত্তম মোটামুটি বুঝে নিয়েছে। তাঁকে আগেও বলে রেখেছিলাম যে, সে যে ধরনের প্রেমের গল্পে অভিনয় করতে অভ্যস্ত, এটা সে ধরনের গল্প নয়। সুতরাং তাঁকে গতানুগতিক পথ কিছুটা ছাড়তে হবে। এতে যে প্রেম আছে, তা প্রচ্ছন্ন। এতে নায়কের দোষ-গুণ দুই আছে, এবং তা যে শুধু অন্তরে তা নয়। তাঁকে বললাম যে তোমার গালে যে সাম্প্রতিক পানবসন্তের দাগগুলি রয়েছে, সেগুলি ক্যামেরায় বোঝা যাবে, কারণ তোমাকে মেকআপ ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।
এই সব প্রস্তাবে তাঁর সামান্য প্রাথমিক দ্বিধা উত্তম সহজেই কাটিয়ে উঠেছিল।
এটা বলতে পারি যে— উত্তমের সঙ্গে কাজ করে যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম, তেমন তৃপ্তি আমার এই পঁচিশ বছরের ফিল্ম জীবনে খুব বেশি পাইনি। উত্তম ছিল যাকে বলে খাঁটি প্রোফেশনাল। রোজকার সংলাপ সে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে কাজে নামত। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা ছিল সহজাত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর দখল ছিল ষোলো আনা। ফলে স্বভাবতই তাঁর অভিনয়ে একটা লালিত্য এসে পড়ত। রোজই দিনের শুরুতে সেদিনকার বিশেষ কাজগুলি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক আলোচনার পর আমাকে নির্দেশ দিতে হত সামান্যই। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, নিছক নির্দেশের বাইরেও সে মাঝে মাঝে কিছু সূক্ষ্ম ডিটেল তাঁর অভিনয়ে যোগ করত যেগুলি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব অবদান। এই অলংকরণ কখনই বাড়াবাড়ির পর্যায় পড়ত না; এটা সব সময়েই হত আমার পক্ষে একটা অপ্রত্যাশিত উপরি প্রাপ্তি। বড় অভিনেতার একটা বড় পরিচয় এখানেই। ‘নায়ক’-এর পর ‘চিড়িয়াখানা’ ছবিতে উত্তমের সঙ্গে কাজ করেও একই তৃপ্তি পেয়েছি। ‘চিড়িয়াখানা’ ছিল নায়িকা-বর্জিত ছবি, ফলে বলা যেতে পারে উত্তমের পক্ষে আরও বড় ব্যতিক্রম।
আজ কাগজে পড়ে জানলাম যে উত্তমকুমার নাকি আড়াইশোর উপর ছবিতে অভিনয় করেছিল। এর মধ্যে অন্তত দুশো ছবি যে অচিরেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যে দেশে সৎ অভিনেতার সদ্ব্যবহার করতে জানা লোকের এত অভাব, সেখানে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শিল্পীর বিচার সবসময়ই হয় তার শ্রেষ্ঠ কাজের উপর। উত্তমের অভিনয়ের পরিধি যে খুব বিস্তৃত ছিল তা নয়, কিন্তু তার এই নিজস্ব পরিধিতে ক্রমান্বয়ে ত্রিশ বছর ধরে সে যে নিষ্ঠা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেল, তার তুলনা নেই। তাঁর অভাব পূরণ করার মতো অভিনেতা আজ কোথায়?”
মহানায়কের দক্ষতা নিয়ে এর থেকে বড় শংসাপত্র আর কি হতে পারে? যেভাবে জুহুরী হীরা চেনে, সেইভাবেই চলচ্চিত্র জগতের এক কিংবদন্তি চিনেছিলেন আরেক কিংবদন্তি কে।
কিন্তু আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে শ্রী সত্যজিৎ রায়ের করে যাওয়া প্রশ্নটি আজও প্রাসঙ্গিক,
‘তাঁর অভাব পূরণ করার মতো অভিনেতা আজ কোথায়?’
(তথ্যসূত্র:
১- আজকাল পত্রিকা, ২১শে জুলাই ২০১৮ সাল।
২- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে জুলাই ২০১৯ সাল।
৩- ১৯৮০ সালের ২৬ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় উত্তমকুমার স্মরণে শ্রী সত্যজিৎ রায়ের লিখিত নিবন্ধ।
৪- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪শে জুলাই ২০১৭ সাল।
৫- আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই জুন ২০১৭ সাল।)
মতামত লেখকের ব্যক্তিগত