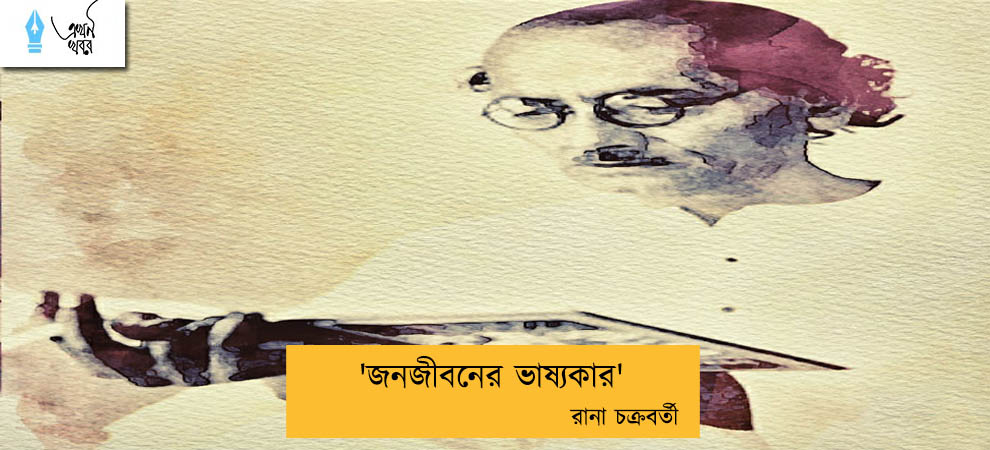“খাসিয়া পাহাড় পার হয়ে রূপনাথ নামের এক গুহা অতিক্রম করে পঁচিশ ক্রোশ পশ্চিমে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়বে একটি উপত্যকা। সেই উপত্যকার মাঝেই রয়েছে অনেক কাল আগের পুরনো এক বৌদ্ধ মঠ। সেই মঠের কোনো এক জায়গায় এক রাজা শত্রুদের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন তার সমস্ত ধন-সম্পদ। কথিত আছে, সেই ধনরত্ন এখনো উদ্ধার হয়নি। রাজা তার সম্পদ কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন কেউ নাকি তার সন্ধান বের করতে পারেনি। সে মঠে নাকি সারাজীবন ধরে খুঁজলেও রাজার সেই সম্পদ কারো খুঁজে বের করার জো নেই। সে সন্ধান দিতে পারেন কেবল এক সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসীর ঝোলাতে রয়েছে একটি মড়ার মাথার খুলি আর তাতেই রয়েছে লুপ্ত ধনরত্ন খোঁজ পাওয়ার সন্ধান…”

এই গল্পের প্লট আমাদের অনেকেই চেনা। গল্পটি বিখ্যাত সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘যকের ধন’ গল্পের অংশবিশেষ। বাংলা সাহিত্যে ছোটদের জন্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লেখার সূত্রপাত ঘটে এই গল্পের মধ্য দিয়ে, পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে যা এক জনপ্রিয় ধারা হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের হাত ধরেই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীগুলো পাঠকদের এক অন্য জগতে নিয়ে যায়।
হেমেন্দ্রকুমার রায় বাংলা শিল্পজগতে এক বর্ণময় চরিত্র। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি এবং গীতিকার। কিশোর সাহিত্যে তাঁর ছিল অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা।
তর্কের বিষয় ‘প্রাচ্য চিত্রকলা’। যুযুধান, সেই চিত্রধারার ‘গোঁড়া সমর্থক’ এক যুবক এবং এক ভদ্রলোক। খানিক বাদেই যুবকটি উৎসাহের বশে ‘বাড়াবাড়ি’ করে ফেললেন। আর উল্টো দিকের ‘মধুর মৃদুহাস্য-রঞ্জিত মুখ’ থেকে ভেসে আসতে থাকল ‘কৌতুকের ইঙ্গিত’। ইঙ্গিতে প্রিয় চিত্রধারার ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দেওয়া চলছে! ধারণা হল, ভদ্রলোক এই চিত্রধারার ‘সমর্থক’ নন, বরং ‘এক জন বিশিষ্ট শত্রু’।
ওই যুবক সম্পর্কে ভদ্রলোকের মূল্যায়ন— ‘তিনি কবি, গল্পলিখিয়ে, সাহিত্যিক এবং বাঙালী’। শেষের শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত এই যুবকের জন্য। সে দিনের যুবকটির পিতৃদত্ত পরিচয় ‘প্রসাদ রায়’। পরে ‘ভারতী’তে তিনিই ‘প্রসাদদাস’। তিনিই আমাদের ‘হেমেন্দ্রকুমার’, আবার কখনও বা ‘মেঘনাদ গুপ্ত’।
তর্কের উল্টো দিকের ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তর্কের আসরের এমন ‘সংলাপী রবীন্দ্রনাথ’কে হেমেন্দ্র চিনতে পারলেন। কারণ, তিনি রবীন্দ্র-কথিত ‘বাঙালী’। আরও বেশি করে, কলকাতার নগরজীবনের নিবিষ্ট কথক।
হেমেন্দ্রকুমার রায় ১৮৮৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল ‘প্রসাদদাস রায়’। তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৯০৩ সালে বসুধা পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প ‘আমার কাহিনী’ প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ সালে নতুন রূপে প্রকাশিত ‘ভারতী’ পত্রিকায় তিনি যোগ দেন এবং সেখানে তাঁর নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। এছাড়া ১৯২৩ সালে ‘মৌচাক’ পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন এবং এ পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন ধরনের লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে।
রাত-দিনের যে কলকাতার সঙ্গে যাপন, সেই শহরেই জন্ম হেমেন্দ্রের। কিন্তু এই শহরের রামধনুতে যে যন্ত্রণার রং, তা-ও যেন মর্মে লাগে হেমেন্দ্রের। সেই রং, যা ক্রমে মানুষকে একলা করে।
স্ত্রী মারা যান মাত্র ৪২ বছর বয়সে। ক্যানসারে আক্রান্ত স্ত্রী মৃত্যুর কিছু দিন আগে যত্ন করে মশারি টাঙিয়ে বিছানা করেছিলেন। স্ত্রীর হাতে করা বিছানাটি আগলে রাখলেন হেমেন্দ্রকুমার, ১৯৬৩-র ১৮ এপ্রিল, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। এই আগলে রাখার সময়কালটা দীর্ঘ ২৪ বছর। হয়তো ওটুকুই স্ত্রীর সঙ্গে থাকা! আবার বড় ছেলে অলকের সাফল্যে খুশি হয়েছেন হেমেন্দ্র। এই দম্পতির তিন মেয়ের ছোটটিও মারা যান অল্প বয়সে।
শুধু পরিবারের শোক-তাপে দগ্ধ হওয়া নয়, যা হেমেন্দ্র ভালবাসেন, সেই সব কিছুর সঙ্গেই বিচ্ছেদের চালচিত্র ফুটে উঠল ধীরে ধীরে…
যে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কেটেছে, সেই মানুষটিই যখন ‘উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল’ লিখলেন, মতান্তর ঘটল। বইয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে ‘যথেষ্ট অন্যায্য মতামত’-এর বিরুদ্ধে কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন হেমেন্দ্র। ফল, সম্পর্কে চিড় ধরা। যদিও শ্রদ্ধায় চিড় ধরেনি কোনও দিন।
আসলে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ মাত্রেই খুব সংবেদনশীল হেমেন্দ্রকুমার। তার সাক্ষী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও। শরৎচন্দ্র যদি জানতে পারেন কেউ তাঁর ‘শিষ্যস্থানীয়’, তা হলে ভালবেসে তাঁকে একটি ফাউন্টেন পেন দিতেন। সে কথা হেমেন্দ্রকুমারকে মজা করে বললেনও শরৎচন্দ্র। কিন্তু হেমেন্দ্রের জবাব, ‘আপনি আমার শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু আমার গুরু রবীন্দ্রনাথ। আর কাউকে তো গুরু বলে মানতে পারব না।’
তবে ব্যক্তি ও মানুষ শরৎচন্দ্রের প্রতি তিনি যে ঋণী, তা-ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন হেমেন্দ্রকুমার। জানিয়েছেন, শরৎচন্দ্র এক দিন একটা ভূতের গল্প বললেন। সেই গল্প এমনই যে, রাতে একলা বাড়ি ফেরাটাও নাকি কঠিন হয়ে পড়ে। ‘সেই গল্পটি আমি আমার ‘যকের ধন’ উপন্যাসে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছিলুম’, জানান হেমেন্দ্রকুমার। সঙ্গে এ-ও স্বীকার করেন, শরৎবাবুর মুখের ভাষার অভাবে গল্পের অর্ধেক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।
আসলে এই সৌন্দর্য-নষ্ট বারবার ব্যথা দিয়েছে হেমেন্দ্রকে। যে বাড়ির অলিন্দ হেমেন্দ্রকে বৌদ্ধিক তৃপ্তি দিয়েছে, সেই ঠাকুরবাড়ির ‘আনন্দের হাট’-ও ক্রমে ম্লান হয়ে এল। আর ও পথ মাড়ালেন না লেখক। ‘ঠাকুরবাড়ি আজ নিরালা, নিস্তব্ধ’, আক্ষেপ হেমেন্দ্রকুমারের গলায়।
রবিঠাকুরের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী তখন ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদক। তরুণ প্রসাদদাস রায় এ সময় নিয়মিত লেখক হিসেবে ভারতীতে লিখে চলেছেন। একদিন এই তরুণ লেখক সম্পাদকের কক্ষে গিয়ে বঙ্কিম যুগের বাঙালিদের নিয়ে একটি ধারবাহিক প্রবন্ধ লিখতে সম্পাদকের কাছে অনুমতি চাইলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রসাদ সম্পর্কে বেশ অবগত ছিলেন। তিনি এই তরুণ লেখককে লেখার অনুমতি দিলেন। তবে ‘প্রসাদ দাস রায়’ নামে লেখাটি ছাপা হবে না বলে সম্পাদক তাঁকে আগেই জানিয়ে দেন। সম্পাদক লেখককে এই লেখার জন্য একটি ছদ্মনাম বেছে নিতে বললেন। বয়সে তরুণ বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে লেখাটি নিয়ে প্রতিবাদ আসতে পারে ভেবে ভীত ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।
সম্পাদকের কথামতো ‘প্রসাদ দাস রায়’ ছদ্মনামেই ধারাবাহিকভাবে লিখে চললেন একের পর এক প্রবন্ধ। তাঁর এই প্রবন্ধগুলো বেশ প্রশংসিত হতে লাগলো সুধি মহলে। শেষে ছদ্মনামেই এত বিখ্যাত হয়ে গেলেন যে বাবার দেয়া ‘প্রসাদ’ নামটি হারিয়ে গলে চিরতরে। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল ‘হেমেন্দ্রকুমার রায়’।
অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পর্বগুলি চমৎকার।
কলকাতায় ‘সরকারি চিত্র-বিদ্যালয়ে’র আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনী চলছে। সেখানে ভিড়, পাশ্চাত্যের ছবিরই। ভিড়েরই এক কোণে আচমকা দেখা যায় ‘জলীয় রঙে আঁকা’ কয়েকটি ছবি। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন শিল্পরসিক হেমেন্দ্রকুমার। খুলে গেল যেন ‘এক অজানা সৌন্দর্যলোকের বন্ধ দরজা’। ছবিটির স্রষ্টা যে অবনীন্দ্রনাথ!
এই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ সম্ভবত লেখার সূত্রেই। ‘ভারতী’ পত্রিকায় হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ। স্বর্ণকুমারী দেবী জানালেন, লেখার সঙ্গে অজন্তার দু’-একটি ছবি দরকার। তার জন্য অবনীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হতে হবে।
হেমেন্দ্রকুমার গেলেন পূর্ব পরিচিত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। পেরিয়ে এলেন রক্ষী-সজ্জিত দরজা। তার পরে একটি ঘর। ঘরের দেওয়ালে হাতে আঁকা ছবি। সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে বৈঠকখানা। অত্যন্ত পরিপাটি। সব শুনে অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ‘আপনার ঠিকানাটা রেখে যান।’ দু’দিন পরেই হেমেন্দ্রকুমারের বাড়িতে সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত দু’খানি ছবির প্রতিলিপি পৌঁছে দেন।
হেমেন্দ্র ঠিক করলেন, অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছবি আঁকা শিখবেন। এক প্রদর্শনীতে সোজা অবনীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে আবদার, ‘প্রাচ্য চিত্রকলার শিক্ষার্থী হতে চাই।’ অবনীন্দ্রনাথও খুশি। বললেন, ‘এখন আপনার মত ছাত্রই আমার দরকার— যাঁরা এক সঙ্গে তুলি আর কলম চালাতে পারেন। আঁকুন দেখি একটি পদ্মফুল।’ হেমেন্দ্রকুমার আঁকলেন, ‘কিম্ভূতকিমাকার’ পদ্মফুল। তা দেখে সহাস্য অবনীন্দ্র-উক্তি, ‘আপনার চেয়েও যাঁরা খারাপ আঁকতেন, তাঁরাও আমার হাতে এসে উৎরে গিয়েছেন। আপনারও হবে।’
শিল্পীজীবন খুব একটা গড়ায়নি হেমেন্দ্রের। যদিও শিল্পরুচির পাঠটা মিলেছে। সেই পাঠেই চিনতে পারা শিল্পী-বন্ধু যামিনী রায়কে। ‘কলালক্ষ্মীর আশীর্বাদ’ পাওয়া যামিনী অর্থকষ্ট সত্ত্বেও ‘লোকপ্রিয় পদ্ধতি’তে আঁকেন না। এই সততা তৃপ্তি দিয়েছিল হেমেন্দ্রকে।
শুধু আঁকা নয়, একটুখানি লেখার আবদার নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের কাছে বারবার গিয়েছেন ‘রংমশাল’ পত্রিকার সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার। আর অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘কাগজ-কলম নিয়ে বসো। আমি বলি, তুমি লিখে নাও।’ সঙ্গে দিয়েছেন লেখা নিয়ে পরামর্শও, ‘হেমেন্দ্র, প্রথমে যা মনে আসবে, তাই লিখো। তবেই লেখা হবে স্বাভাবিক।
স্বাভাবিকই লিখেছেন হেমেন্দ্রকুমার। তবে অস্বাভাবিক গতিতে। পনেরো বছর বয়সে ‘আমার কাহিনী’ বুনে হেমেন্দ্রকুমারের আত্মপ্রকাশ। তার পরে অজস্র গোয়েন্দা গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিলেখ, গান, প্রবন্ধ রচনা করলেন বা করতেই হল।
লেখালেখির একপর্যায়ে হেমেন্দ্রকুমার ‘মৌচাক’ পত্রিকার সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্মতি নিয়েই ছোটদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিখতে শুরু করেন। এই পত্রিকায় তাঁর প্রথম অ্যাডভেঞ্চার গল্প ‘যকের ধন’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই গল্পের সাফল্যের পর থেকেই ‘মৌচাক’ পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠলো অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্য গল্প। অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা গল্পের কারণে ‘মৌচাক’ পত্রিকার জনপ্রিয়তা দেখে সমকালীন অন্যান্য নামীদামী লেখকেরা এ ধরনের গল্প লিখতে উৎসাহিত হন।
একটি গুপ্ত সংকেতের অর্থ উদ্ধার করে দুর্গম জঙ্গল এবং পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার জমজমাট এক গল্প হেমেন্দ্রকুমারের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ‘যকের ধন’। গল্পের নায়ক দুই উদ্যমী তরুণ কুমার এবং বিমল। মৌচাকে প্রকাশিত হেমেন্দ্রকুমারের দ্বিতীয় কাহিনী ছিল কল্পবিজ্ঞানের, নাম ছিল ‘মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন’। মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীদের পৃথিবী আক্রমণ এবং মঙ্গলগ্রহ অভিযান ছিল গল্পটির বিষয়বস্তু। এভাবে তিনি লিখে গেছেন জনপ্রিয় সব অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী।
হেমেন্দ্রকুমারের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর মধ্যে তার প্রিয় বিষয় ছিল গোপন সংকেত, কঠিন ধাঁধাঁ বা জটিল হেঁয়ালির সমাধান করে গুপ্তধনের অনুসন্ধান। এ ধরনের কাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ‘যকের ধন’, ‘আবার যকের ধন’, ‘যক্ষপতির রত্নপুরী’, `সূর্যনগরীর গুপ্তধন’ ইত্যাদি। তাঁর কাহিনীর নামই মূলত পাঠককে আকৃষ্ট করতো। তাঁর এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর পেছনে ছিল শুধুমাত্র অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার আর বিপদসঙ্কুল পথকে সাহস আর বিক্রমের সাথে জয় করার এক দুঃসাহসী প্রচেষ্টা।
তাই বিমলের মুখে শোনা যায়,
“গুপ্তধনের ওপরে আমাদের কোনো লোভ নেই, আমরা খালি চাই বিপদকে! সে বিপদ হবে যত ভয়ানক, আমাদের আনন্দ হবে তত বেশি!” সঙ্গী কুমারও বলেছে, “বিপদ না থাকলে মানুষের জীবনটা হয় আলুনি আলুভাতের মতন।”
কুমার এবং বিমল ছাড়াও হেমেন্দ্রকুমার তার গল্পে আরো যেসব নায়ক চরিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সত্যসন্ধানী জয়ন্ত। জয়ন্ত এবং তার বন্ধু মানিককে নিয়ে লেখা হেমেন্দ্রকুমারের প্রথম উপন্যাস ‘জয়ন্তের কীর্তি’। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
হেমেন্দ্রকুমারের আরেকটি গোয়েন্দা সিরিজ ছিল হেমন্ত-রবিন। জয়ন্ত-মানিকের মতোই এটা সে সময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই গোয়েন্দা হেমন্ত যেন লেখক নিজেই। তিনি শুধুমাত্র গোয়েন্দাই নন, বুদ্ধিমান বিজ্ঞানীও। সহকারী বন্ধু রবিনের সহায়তায় এক দুষ্টু বিজ্ঞানীর কারবার ফাঁস করেছিলেন ‘অন্ধকারের বন্ধু’ গল্পে। এসব গল্পে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের দেখা মেলে, তা হলো সতীশ বাবু নামের একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের।
হেমেন্দ্রকুমার বিদেশী রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীর যথেষ্ট খোঁ খবর রাখতেন, যা তাঁর লেখায় বেশ স্পষ্ট। বিদেশের নানা ক্রিমিনোলজি এবং ফরেনসিক সায়েন্স বিষয়ক নানা আবিষ্কারের নতুন নতুন সব তথ্য তিনি অবলীলায় তাঁর কাহিনীতে ব্যবহার করে পাঠকদের চমকে দিতেন। বাংলার পাঠকদের জন্য বিদেশী নানা রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীকে বাংলার স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগী করে লিখেছেন বেশ কিছু রচনা। এসব কাহিনীর মধ্যে ‘বিশালগড়ের দুঃশাসন’ (ব্রাম স্টোকারের ‘ড্রাকুলা’), ‘নিশাচরী বিভীষিকা’ (আর্থার কোনান ডয়েলের ‘দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস’), ‘হারাধনের দ্বীপ’ (আগাথা ক্রিস্টির ‘টেন লিটল নিগারস’) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠেছিল ‘মৌচাক’-এ ‘যকের ধন’ প্রকাশের পরে। ‘আবার যকের ধন’, ‘দেড়শো খোকার কাণ্ড’, ‘কিংকং’, ‘পদ্মকাঁটা’… লিখেই চলেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। আর বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মাণিক, বিনয়বাবু-কমল, ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবুতে বুঁদ হয়ে থাকে কয়েক যুগের বাঙালি। এত লেখার কারণ, মিলিটারি অ্যাকাউন্টসের স্থায়ী চাকরি ছেড়ে দেওয়া সাহিত্যিক হেমেন্দ্রের ওই লিখেই যে চলে।
অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ছাড়া সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়ও তাঁর পদচারণা ছিল উল্লেখ করার মতো। ইতিহাসভিত্তিক রচনা লেখায় তিনি বেশ বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, লিখেছেন নানা বই। ‘আলো দিয়ে গেল যারা’, ‘ভগবানের চাবুক’ ইত্যাদি তার ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু অবাক হওয়ার মতোই। ‘আলোকচিত্রের নবধারা’, ‘রোদ্যার শিল্পচাতুর্য’, ‘মিশরের আর্ট’, ‘মানুষখেকো গাছ’ ইত্যাদিতে বিষয় বৈচিত্র্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।
তাঁর লেখা ‘তারা তিন বন্ধু’-তে মানবিকতার এক উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় আরেক গ্রন্থ ‘দেড়শো খোকার কান্ড’। এসব রচনার মধ্যে তার বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য, বিভিন্ন চরিত্রের রুপায়ণে সূক্ষ্মবোধ এবং গল্প নির্মাণের গভীরতা প্রবলভাবে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর ২৭ খন্ড রচনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরও বহু লেখা এখনো অগ্রন্থিত রয়ে গেছে এবং কালের গর্ভে হারিয়েও গেছে বহু সৃষ্টি।
বিভিন্ন পত্রিকায় শুধু লেখালেখির কাজেই হেমন্দ্রকুমার রায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেননি, নতুন নতুন পত্রিকা সম্পদনা করা, নতুন প্রতিভাধর লেখক খুঁজে বের করা সবই হয়েছে তাঁর হাত ধরে। ১৯২৫ সালে তিনি সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘নাচঘর’ এবং ‘ছন্দা’ নামের পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ‘নাচঘর’ ছিল একটি অতি উঁচু মানের শিল্প-সাহিত্য-বিনোদন সংক্রান্ত পত্রিকা। এই পত্রিকায় অনেক স্বনামধন্য লেখকের হাতেখড়ি হয়।
হেমেন্দ্রকুমারের আরেকটি গুণের কথা অনেকেই জানেন না। তিনি ছিলেন একজন সার্থক গীতিকার এবং সুরকার, এককথায় বলা চলে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন একজন মানুষ। শচীন দেববর্মণ, কৃষ্ণচন্দ্র দে’র মতো প্রখ্যাত শিল্পীরাও গেয়েছেন তাঁর রচিত গান। সে সময়ের বাংলা মঞ্চ এবং গ্রামাফোনে গাওয়া গানের প্রচলিত ধারা এবং রুচির আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তার রচিত অনেক গান তৎকালীন সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।
চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বেশ খ্যাতি ছিল। বাংলায় শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে তাকে অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে ভাবা হয়। চলচ্চিত্র সমালোচনা লিখতে লিখতে চলচ্চিত্র জগতেও প্রবেশ করেন কাহিনীকার হিসেবে। ১৯৩৫ সালে জ্যোতিষ মুখার্জী পরিচালিত ‘পায়ের ধুলো’ ছবির কাহিনীকার ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। ১৯৩৯ সালে তার গল্প ‘যকের ধন’ চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার জন্য গল্পের পরিমার্জনে তাকেই বেছে নেয়া হয়। গল্পের সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে বেছে নেয়া হয় শচীন দেব বর্মণকে। এছাড়া ১৯৫১ সালে তাঁর লেখা ‘নিশীথিনী বিভীষিকা’ অবলম্বনে বাংলা চলচ্চিত্র ‘জিঘাংসা’ এবং হিন্দিতে ‘বিশ সাল বাদ’ এবং ১৯৫৯ সালে তাঁর রচিত ‘দেড়শো খোকার কান্ড’ নির্মিত হয়।
বাঙালি সত্তার কারণেই এই মহানগরের বৌদ্ধিক জগৎ, ‘ভদ্রলোক’-এর দেখতে না চাওয়া জনজীবন, ধুলো-কাদা-জলের অধ্যায় দিয়ে সাজানো একটিই মাত্র বই লিখতে চেয়েছেন হেমেন্দ্র। কেমন সেই বইয়ের অধ্যায়গুলি?
সিনেমা তৈরি হচ্ছে। নাম ‘তরুণী’। সংলাপ রচনা, কাহিনি, গীতরচনায় হেমেন্দ্রকুমার। কয়েকটি গানের সুর-সংযোজনে ‘আকারে ছোটখাটো, শান্তশিষ্ট, মৃদুভাষী, সুদর্শন’ এক শিল্পী। কিছু দিন বাদে হেমেন্দ্রের পরামর্শেই ‘ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানি’তে সিনেমার সুরকারটি ‘স্থায়ী’ পদে যোগ দিলেন। কিন্তু ক’দিন বাদেই চাকরিতে ইতি।
‘কেন? কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা হল না?’ সুরকার জানালেন, তা নয়। আসলে রাশি রাশি গানে তাড়াতাড়ি সুর দেওয়ায় আনন্দ নেই। বয়সে ছোট শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানালেন হেমেন্দ্র। বললেন, ‘খাঁটি শিল্পীর উক্তি— সচরাচর যা শোনা যায় না। আর্টের মস্ত শত্রু হচ্ছে, ব্যস্ততা।’ সুরকারটি হিমাংশু দত্ত।
শুধু হিমাংশু দত্তই নন, সঙ্গীত জগতের বহু কিংবদন্তির সঙ্গেই জড়িয়ে হেমেন্দ্র-জীবন। তেমনই এক জনের কথা—
কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রায়ই আসেন বাড়িতে। হেমেন্দ্রের লেখা টপ্পা গেয়েছেন ‘গায়কপ্রবর’ কৃষ্ণচন্দ্র। সেই কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গেই এলেন এক তরুণ। সেই তরুণের জন্যও হেমেন্দ্র লিখলেন, ‘ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে…’ বা পরে ‘ও কালো মেঘ, বলতে পারো…’ ইত্যাদি। ১৯৩২ সালে ‘হিন্দুস্তান রেকর্ড’ থেকে সেই তরুণের আত্মপ্রকাশ। হেমেন্দ্রের মনে হল, এই শিল্পী ‘অতি-আধুনিক যুগের গায়কদের মধ্যে সর্বপ্রথম’।
কিন্তু সেই তরুণ সিনেমার প্রেমে পড়লেন। হেমেন্দ্রেরও সোজা কথা, ‘সিনেমার কবলে পড়লে দুর্গত হয় চারুকলা’। যাঁর সম্পর্কে এই কথা, তিনি শচীন দেববর্মণ।
হেমেন্দ্রের সঙ্গীত সম্পর্কে ‘বিশুদ্ধ’ রুচিটি আসলে তৈরি করেছিল তাঁর পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের পৈতৃক বাড়ির পরিবেশ। যে পরিবেশে সুর নিয়ে নাড়াচাড়া করেন ফ্লুট ও এস্রাজ-বাদনে পারদর্শী বাবা রাধিকানাথ। বছর পনেরোর কিশোর হেমেন্দ্র বাবাকে দেখে ভাবলেন, লালচাঁদ বড়ালের কাছে গান শিখবেন। কিন্তু বড়াল সাহেব জানালেন, ‘গুরুগিরি করেন না।’ শেষমেশ নাড়া বাঁধা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর শিষ্য মহিম মুখোপাধ্যায়ের কাছে। কিন্তু তত দিনে মনের মধ্যে তিরতির করে বেড়ে উঠেছে সাহিত্যপ্রেম।
প্রথাগত তালিমের সেই শেষ।
তালিমের শেষ হলেও সঙ্গীতপ্রীতি বা গান রচনা, তাতে খামতি নেই।
এক কবি-বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি শান্তিপুরে চলেছেন হেমেন্দ্র। পূর্ণিমা রাত, দু’পাশে বন। চলেছেন চূর্ণি নদীর ঘাটে। এমন সময়ে কে যেন বাঁশের বাঁশী বাজায়। মুগ্ধ হয়ে গেলেন হেমেন্দ্র।
এমন সঙ্গীতপ্রীতি যাঁর, তাঁর বাড়ির মজলিসে উস্তাদ জমীরুদ্দিন খাঁ সাহেব, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দিলীপকুমার রায়ের মতো দিকপালদের নিত্য আসা স্বাভাবিকই। হেমেন্দ্রকুমার মুগ্ধ শ্রোতা। কিন্তু সে মুগ্ধতায় বিপত্তিও ঘটে। অন্তত ‘তিনি’ থাকলে তো বটেই। এক বার গভীর রাত পর্যন্ত মজলিস চলেছে। সেই ‘তিনি’ বললেন, ‘হেমেনদা, রাত হয়েছে, আজ এখানেই আমার আহার আর শয়ন। জ্ঞানও থাকবে।’ জ্ঞান অর্থাৎ সুরকার জ্ঞান দত্ত।
তেতলার ঘর ছেড়ে হেমেন্দ্র এলেন দোতলায়। আচমকা গভীর রাতে ঘুম ভাঙল। তেতলা থেকে দুড়ুম দুড়ুম শব্দ আসছে। ‘কী ব্যাপার? তোমরা দু’জনে কি মারামারি করছ?’
মারামারি নয়, ধাক্কাধাক্কি! কারণ, খাটে দু’জনেই অন্য জনকে জায়গা দিতে নারাজ। এমন আমোদই স্বাভাবিক। যখন ‘তিনি’টির নাম কাজী নজরুল ইসলাম।
নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কিন্তু সঙ্গীতের সূত্রেই। মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’ নাটকের গান সংযোজনের সময়ে সম্ভবত এই ‘আড্ডাপ্রিয়’ দুই বাঙালির ভাব জমে ওঠে।
এ ভাবেই আলাপ বিপুলবপু যতীন্দ্রচরণ ওরফে গোবর গুহের সঙ্গেও। আলাপের স্থান মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে নরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ি। শনিবাসরীয় এক আড্ডায় উদয় হলেন সেই ভদ্রলোক। কিন্তু, আলাপের পরে হেমেন্দ্র জানলেন, ওই ভদ্রলোক শুধু কুস্তিতেই দড় নন, সঙ্গীতশিল্পীও বটে। ব্যাঞ্জো শিখেছেন ককুভ খাঁয়ের কাছে। ‘ভারতবর্ষ যে অধৃষ্য মল্লের দেশ, এ-সত্য য়ুরোপের চোখে আঙুল দিয়ে সর্বাগ্রে দেখিয়েছিলেন গোবরবাবু ও শ্রীশরৎকুমার মিত্র,’ মনে করেন হেমেন্দ্র।
আখড়া-ময়দান সম্পর্কে এমন স্বদেশি ভাবনাকে আসলে লালন করেছেন হেমেন্দ্র। আর তাই গাছে উঠে ধুতির সাহায্যে নিজেকে পেঁচিয়ে মহা-খেলা দেখতে পৌঁছে যান হেমেন্দ্র। খেলাটা দেখতেই হত। কারণ, তাতেই ১৯১১ সালে মোহনবাগানের শিল্ড জয় হয়! সেই জয় শুধু জয় নয়। ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ময়দানি জবাব, মনে হয় হেমেন্দ্রের। এই স্বদেশি টানেই সাহিত্য-আসর ফেলে তিনি ছুটে যান গড়ের মাঠের তাঁবুতে। দেখেন ভীম ভবানী, গামা পালোয়ান, হাসান বক্সদের কুস্তি।
আবার পরক্ষণেই সাহিত্যে তৈরি করেন বিদেশি ভিলেন। ‘রত্নপুরের যাত্রী’, ‘সুলু সাগরের ভুতুড়ে দেশ’, ‘সোনার পাহাড়ের যাত্রী’ প্রভৃতি বইতে বারবার ফিরে আসে বিদেশি দস্যুর দল। স্বদেশি ভাবনায় সেই দস্যুরা কখনও ইংল্যান্ড, মিশর বা অস্ট্রেলিয়ার।
কিন্তু শুধু ভাবনা নয়, নিজেও ক্রিকেট, হকি, ফুটবল খেলা, সাঁতার দিয়ে গঙ্গার এ পার-ও পার, সর্বত্রই অবাধ বিচরণ হেমেন্দ্রের।
আখড়ায় গিয়ে পালোয়ানদের রদ্দা দেখার পাশাপাশি হেমেন্দ্র ঢুঁ দেন আরও এক জায়গায়। ঠাকুরবাড়িতে। দেখেন, বিলিতি পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মগ্ন ‘পটের উপরে তুলিকা চালনায়’।
শিশু-কিশোরদের জন্য হেমেন্দ্রকুমার রায় ৮০টিরও বেশি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এর মধ্যে কী নেই? কবিতা, নাটক, হাসি ও ভূতের গল্প, অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা কাহিনী, ঐতিহাসিক উপন্যাস সবকিছুতেই তাঁর ছিল সরব পদচারণা। তাঁর অসাধারণ সব চরিত্র বিমল, কুমার, জয়ন্ত (গোয়েন্দা) ও সহকারী মানিক, পুলিশ ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবু, ডিটেকটিভ হেমন্ত বাংলা কিশোর সাহিত্যে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে।
পঁচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত একটানা লিখে গেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। সারা জীবন এত লিখেছেন যে একসময় তাঁর ডান হাতের তর্জনীতে কড়া পড়ে গিয়েছিল। সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা এত তীব্র ছিল যে সরকারি চাকরির নিশ্চিত জীবন ছেড়ে অনিশ্চিত সাহিত্যকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। জীবনের একসময় এমন অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল যে খুব অল্প টাকায় প্রকাশকের কাছে বেশ কয়েকটি বইয়ের কপিরাইট বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।
লেখক হিসেবে জীবনে যেমন সুনাম কুড়িয়েছেন, তেমনি অপমানও কম সইতে হয়নি। প্রথম জীবনে অনেক বড় নামী সাহিত্যিক মুখের ওপর না করে দিয়েছেন, পরবর্তীতে তাঁরাই সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কাছে নিজের লেখা ছাপানোর অনুরোধ করতে আসলে তিনি তাঁদের ফেরাননি। ‘কুসুম’ নামের একটা গল্প লেখার পর নিম্নমানের লেখা বলে অনেক পত্রিকা থেকে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। বারো বছর পর সেই গল্পই যখন জার্মান ভাষায় অনুদিত হয়ে বিপুল প্রশংসা পায়, তখন সেসব পত্রিকার সম্পাদকদের সাহিত্য বিচারের দক্ষতা দেখে অবাকই হতে হয়। এ লেখা নিয়ে বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ রাইনহান্ড ভাগনার প্রশংসাসূচক একটি চিঠি লেখেন হেমেন্দ্রকুমার রায়কে। প্রত্যাখাত সেই গল্পের এমন প্রশংসামূলক চিঠিটি তাঁর মৃত্যুর তেইশ বছর পর প্রকাশ করা হয়।
লেখার সূত্রেই নানা অভিজ্ঞতা হেমেন্দ্রকুমারের। তিনি ঠিক কল্লোলীয় নন। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা যখন স্রেফ অশ্লীলতার দোহাই দিয়ে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তখন কলম ধরে আগুন ঝরান হেমেন্দ্রকুমার। আবার নিজেও পড়েন ওই ‘শ্লীল-অশ্লীল’-এর ফাঁদে।
হেমেন্দ্রকুমারের ‘পোড়ারমুখী’ গল্পটি ‘কল্লোল’ পত্রিকা বাতিল করে। কারণ তাতে যথেষ্ট ‘অশ্লীলতার উপাদান’ নেই! আবার তা ‘অশ্লীল’ বলেই ছাপল না ‘ভারতবর্ষ’! পরে অবশ্য ওই গল্পই দিব্যি প্রকাশিত হয় ‘উত্তরা’ পত্রিকায়।
‘উত্তরা’, ‘কল্লোল’ বা ‘ভারতী’ শুধু নয়, ‘জাহ্নবী’, ‘যমুনা’, ‘বৈকালী’ প্রভৃতি অজস্র পত্রিকার সঙ্গেও কখনও লেখক হিসেবে, কখনও বা সম্পাদকীয় কাজের সূত্রে যোগাযোগ হেমেন্দ্রের। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সঙ্গে যৌথ ভাবে এবং আরও পরে একক ভাবে ‘নাচঘর’ পত্রিকার সম্পাদনা করতেও দেখা যায় হেমেন্দ্রকুমার রায়কে। ‘নাচঘর’ পত্রিকাটি ঘোষিত ভাবে শিল্পপত্রিকা। এবং সেই সঙ্গে ‘রাজনৈতিক আলোচনা থাকিবে না’, তা-ও ঘোষণা করে।
এই পত্রিকাটি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে ধারাবাহিক গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন করল। এমনকি, ‘চিরকুমার সভা’য় শিশিরকুমারের অভিনয়ের বিরূপ সমলোচনা প্রকাশিত হওয়ায় তার পাল্টা দেয় ‘নাচঘর’। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ায় যে লিখতে হয়, ‘নাচঘরের সঙ্গে শিশিরবাবুর কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই।’
কিন্তু পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক না থাক, আত্মিক সম্পর্ক তো ছিলই হেমেন্দ্র-শিশিরের।
সেই সম্পর্কের সূত্রপাত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শিশির ভাদুড়ীর ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস’ নাটক দিয়ে। ভীম ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরিত্রে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে হেমেন্দ্রের ‘অবস্থা হলো আকাশ থেকে সদ্য-পতিতের মতো’। অনুরোধে কাটা টিকিট সার্থক হল। এই নাটকের সমালোচনাও লিখলেন হেমেন্দ্র। সমালোচনাটি তাঁকেও ছুঁয়ে গিয়েছে, এ কথা বলেছিলেন স্বয়ং শিশিরকুমার। এ ছাড়া দু’জনের সখ্যের সাক্ষ্য দেয় হেমেন্দ্রের ‘বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার’ বইটিও।
সখ্য ছিল অনুজদের সঙ্গেও। তেমনই এক অনুজের জীবনের সঙ্গে জড়ানো এক গল্প।
গঙ্গাপাড়ে আপার চিৎপুর রোডের কাছে ভাস্কর্যশোভিত তেতলা বাড়ি। এই বাড়ি থেকে ‘সমুদ্রের ভ্রান্তি’ জাগা স্বাভাবিক, জানিয়েছেন পরিমল গোস্বামী। বাড়িটির মালিক হেমেন্দ্র। সেখানেই সপরিবার আড্ডা চলছে। আচমকা গঙ্গাপাড়ে ‘ক্রীড়াচঞ্চলা’ দুই তরুণীর উদয়। হেমেন্দ্রবাবু ছেলে প্রদ্যোৎকে বললেন, ‘ওঁদের ডাকো দেখি’। তা শুনে হেমেন্দ্রবাবুর স্ত্রী রেণুকাদেবী বললেন, ‘অচেনা বাড়িতে ওঁরা আসবেন কেন?’
সটান জবাব হেমেন্দ্রের, ‘গৃহিণী, ওঁরা হচ্ছেন নতুন বাঙলার মেয়ে।’ খানিক বাদেই দরজায় টোকা। সেই দুই তরুণীই। এক জন বললেন, ‘শুনেছি, এইখানে কোথায় হেমেন রায়ের বাড়ি আছে।’ এই ঘটনার ক’দিন পরে হেমেন্দ্র অনুজ সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে বললেন, ‘তোমার স্ত্রী হরণ করেছিলুম!’
এমনই রসবোধের সাক্ষী হয়েছিলেন কালিদাস রায়ও। এক বার কালিদাসের জিজ্ঞাসা, ‘হেমেন্দ্রকুমার প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও প্রেমের কবিতা লেখেন কেন।’ হেমেন্দ্রকুমারের সটান জবাব, ‘পঞ্চাশোর্ধেও মনে বনে যাবার ইচ্ছা জাগেনি, তাই।’
জীবনরসের সন্ধান হেমেন্দ্রকুমার পেয়েছেন কলকাতার সেই সব মানুষের কাছ থেকে, যাঁদের প্রতি ছুৎমার্গ মধ্যবিত্তের অভ্যেস। সেই অভ্যেসের পর্দা সরিয়েই গোটা কলকাতার ‘নক্সা’ খোঁজেন ‘নিশাচর’ হেমেন্দ্রকুমার। হাঁটা দেন চিনে-পাড়া, সোনাগাছি, হাড়কাটা গলি, ফুলবাগান, বেনেটোলা-সহ নানা স্থলে। এই নিশাচর দুমড়ে-মুচড়ে দেখেন বারবণিতা, গুন্ডা, শ্মশানচারী, শ্রমিক, ভিক্ষাজীবীদের প্রত্যেক রাতের যাপন। দেখেন, সেই যাপনের আবডালে নিয়ত লুকিয়ে পড়া মধ্যবিত্তকেও।
আর এ সব দেখতে গিয়ে বিপদ, তা-ও এসেছে পায়ে পায়ে।
সাহিত্যজগতের পরিচিত এক ‘ভদ্রলোক’ তাঁর দুই বন্ধুকে নিয়ে ঢুকেছেন এক পরমাসুন্দরীর ঘরে। ‘একটু আসছি’ বলে বেরিয়ে গেলেন সেই সুন্দরী। বহুক্ষণ কেটে যায়। দেখা যায়, ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। বিছানায় কী যেন ঢাকা দেওয়া। খানিক ঠাহর করতেই বোঝা গেল, তা ‘মড়া! গলা কাটা!’
আরও এক বার। এক অপরিচিত বৃদ্ধের অনুরোধে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়ি থেকে দেহ কাঁধে সৎকার করতে চলেছেন হেমেন্দ্র। গ্যাস-আলোর সীমানার মধ্যে যেতেই দেখা যায়, মড়ার চাদর বেয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত। কী ঘটেছে বুঝতে বাকি রইল না।
বৃদ্ধ পগারপার। দেহ ফেলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে কোনও রকমে রক্ষা পেলেন লেখক! এ সব অভিজ্ঞতা নিয়েই মেঘনাদ গুপ্ত ছদ্মনামে লেখা ‘রাতের কলকাতা’।
যে লেখালেখি আনন্দের উপকরণ, সেই লেখাটাই একসময় তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল যন্ত্রণার। কঁকিয়ে উঠেছিল হেমেন্দ্রের কণ্ঠস্বর, ‘আমার কাছে পত্রিকার পক্ষ থেকে অনেকেই আসে। এই তো সেদিন পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেল। লিখতে আমার কষ্ট হয়। শরীর বড় খারাপ।’ সঙ্গে সম্পাদকের বার্তা, ‘ডিটেকটিভ গল্প হওয়া চাই। এমন ফরমায়েস মত কি লেখা চলে! আমার ভালো লাগে না।’
ভাল লাগেনি। কিন্তু লিখতে হয়েছে। পেটের প্রয়োজনে, নাটকের প্রয়োজনে, সিনেমার প্রয়োজনে… আর এই সূত্রেই দেখলেন, নিজের লেখা প্রায় চারশো গানের অনেকই কী ভাবে অন্যের নামে বাজারে প্রচলিত হয়ে গেল!
আসলে এ ভাবেই অনেকে ঠকিয়ে গিয়েছেন ব্যক্তি হেমেন্দ্রকুমারকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অনেক বিখ্যাত, অখ্যাতরা। তাঁর নাতনি মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় সংবাদ মাধ্যম কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, এক পাতানো নাতনি হেমেন্দ্রকে ‘গ্যারেন্টার’ রেখে দামি সেলাইকল কিনে চম্পট দেন। টাকাটা দিতে হয়েছিল ‘গ্যারেন্টার’ হেমেন্দ্রকুমারকেই। বইপত্রের সংগ্রহ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায়ের আঁকা ছবি, যা হেমেন্দ্রের আদরের সম্পদ, তা-ও তো ‘একটু নিচ্ছি’ বলে ফেরত দিলেন না অনেকেই!
অন্যের এমনই নানা প্রয়োজনের জন্য বারবার নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন হেমেন্দ্র। সেই ‘অন্যে’র তালিকায় শেষ নাম এই কলকাতাও ছিল কি না, তা বলেননি তিনি। কিন্তু অভিমান… তা তো রয়েইছে।
আর তাই গঙ্গার পাড়ে বিখ্যাত বাড়ির চৌহদ্দিতে মন টেকে না প্রবীণ হেমেন্দ্রকুমারের। প্রবীণ লেখক গঙ্গা নয়, বরং বাড়ির কাছেই গলিপথের মধ্যে চিৎপুর রোডে অন্যের বাড়ির রকে বসে থাকেন। তাকিয়ে থাকেন ‘গঙ্গার স্রোতের বদলে ধুলো ওড়ানো লরি, ট্রাক, মোটরসাইকেল, বাস…’ ইত্যাদির স্রোতের দিকে। কারণ, সেই স্রোতেই যে ‘কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।’
১৯৬৩ সালের ১৮ এপ্রিল সাহিত্যের দিকপাল হেমেন্দ্রকুমার মৃত্যুবরণ করেন। বড়দের লেখক হিসেবে তিনি পাঠকদের কাছ থেকে হারিয়ে গেলেও শিশু ও কিশোর সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি আজও অমলিন। তার ভক্তরা এখন পর্যন্ত তার হাত ধরেই পাড়ি দিয়ে থাকেন বিপদসংকুল অজানা দুর্গম গন্তব্যে, তাঁর লেখাই পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর অমর সৃষ্টির সন্ধান।
লেখক শিবরাম চক্রবর্তী হেমন্দ্রকুমার রায় সম্পর্কে বলেছিলেন,
“বাংলা শিশু-কিশোরদের সাহিত্যকে সেই আদ্যিকালের বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর জগত থেকে আধুনিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন হেমেন্দ্রকুমারই। তারপরে আমরা সবাই তাঁরই অনুবর্তী।”
এই কলকাতার আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রবীণ হেমেন্দ্রকুমার বলতে পারেন নিজের কথা, ‘না কোন ভবিষ্যৎ নেই আমার… শুধু অতীতের কথা ভাবি… এত কথা আছে যা ফুরোবার নয়—’’
সত্যিই কি তিনি ফুরিয়ে যাবার!
(তথ্যসূত্র:
১- দেশ পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যা।
২- হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি।
৩- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯শে জানুয়ারি ২০১৯ সাল।
৪- উইকিপিডিয়া।
৫- https://roar.media/bangla/main/literature/hemendra-kumar-roy-mystery-and-adventure-writer-in-bengali-literature/)
মতামত লেখকের ব্যক্তিগত