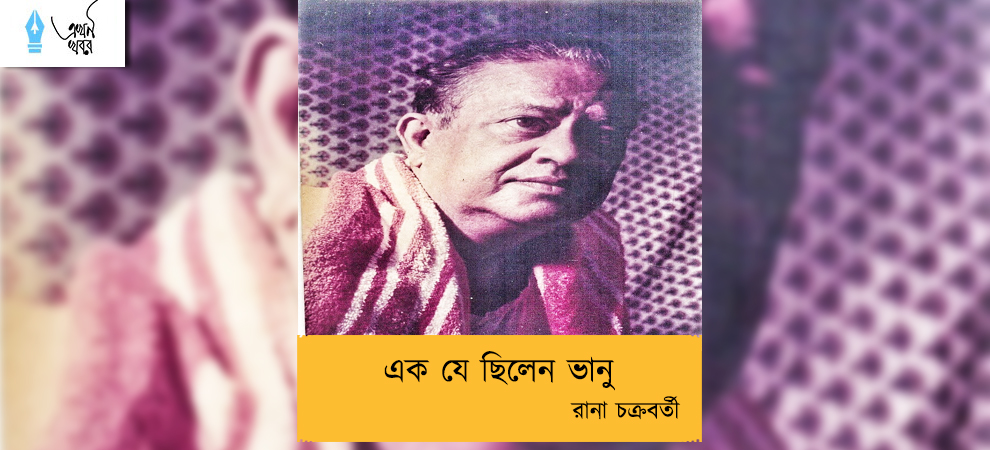অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘পূর্বরাগ’, সুশীল মজুমদারের ‘সাহারা’ বা বিমল রায়ের ‘অঞ্জনগড়’ ছবির মাধ্যমে বাংলা ছবির জগতে ধীরে ধীরে নিজেকে পরিচিত করে তুলছিলেন ‘জহর রায়’। ঠিক সেই সময়েই আর এক ‘বাঙাল অভিনেতা’ বাংলা ছবির মহাকাশে পা রেখেছিলেন। বরিশালের জহর সেভাবে বাঙাল ভাষা বলতে পারতেন না। কিন্তু এই অভিনেতার আবার বাঙাল ভাষাই ছিল মূল অস্ত্র। তিনি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় সমসাময়িক সময়তেই ‘জাগরণ’ ছবিতে ভানুর আবির্ভাব। জহর রায়ের সঙ্গে প্রথম থেকেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ভানুর। যে ভানু-জহর জুটি পরবর্তীকালে ইতিহাস তৈরি করেছিল, সেই জুটির পথ চলা শুরু প্রভাত মিত্রর ‘ইন্দ্রনাথ’ ছবি দিয়ে ১৯৫০ সালে। এরপর থেকে জহর-ভানু সম্পর্কে চিড় ধরা তো দূরে থাক, বন্ধুত্ব ক্রমশ গাঢ় হয়েছে। দু’জনেই কমেডিয়ান হিসেবে সাফল্যের চূড়ায় অধিষ্ঠান করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত সংঘাত বা পেশাগত রেষারেষির মনোভাব কোনওদিনই দু’জনের মধ্যে মাথাচাড়া দেয়নি। দু’জনেই নিজেদের অভিনয়ে স্বতন্ত্র ধারা বজায় রেখেছেন। শুধু পর্দাতেই নয়, পর্দার বাইরেও ভারী ভাব ছিল দুজনের।
অথচ, বাজারে গুজব চালু ছিল যে ভানু আর জহর নাকি পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পারেন না। এসব কথা নিয়ে কেউ দু’জনকে প্রশ্ন করলে তাঁরা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই তার জবাব দিতেন। ভানু বলতেন, ‘‘লোকের কথায় কী আসে যায়। আমি কী হেইডা জহর ভালো কইরাই জানে, আর জহর কী হেইডা আমি জানি।’’ অন্যদিকে জহর রায় বলতেন, ‘‘যাঁরা ওইসব কথা রটাচ্ছে তাদের মুখের মতো জবাব দেওয়ার জন্য একবার বাথরুমে যাওয়া দরকার। তাদের কথার উত্তর ওইসব জায়গাতে দাঁড়িয়েই দিতে হয়।’’ ভানুর তূণে প্রধান অস্ত্র যেমন ছিল বাচনভঙ্গি, তেমন জহরের অভিনয়ের অনেকটা জুড়েই ছিল শরীরী ভাষা। ভানু লিখেছেন, ‘‘জহরের সব থেকে বড় গুণ ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। … আর একটা গুণ হল ফিজিক্যাল ফিটনেস। নাকের ওপর একটা ঘুষি মারলে জহর সমস্ত শরীরটা ঠেলে দিয়ে এমনভাবে পড়ে যেত যে, সেটা কিছুতেই অভিনয় বলে মনে হতো না।’’ এই দুই অভিনেতার বন্ধুত্বে আরও দুই ব্যক্তির ভূমিকার উল্লেখ করতেই হবে। একজন পরিচালক ‘সুশীল মজুমদার’। তাঁর স্ত্রী ‘আরতি মজুমদার’ পাটনার মেয়ে ছিলেন। সেইসূত্রে সুশীলবাবু জহর রায়ের পূর্বপরিচিত ছিলেন। সুশীলবাবু আবার ছিলেন স্টুডিওপাড়ায় ভানুর গুরুস্থানীয়। ভানুর প্রথম ছবির পরিচালক বিভূতি চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেন সুশীলবাবুই। এই সুশীলবাবুর বাড়িতেই এক সিনেমার আড্ডায় প্রথম আলাপ হয় ভানু ও জহরের। আর দ্বিতীয় যে ব্যক্তির বড় ভূমিকা ভানু-জহরের অভিনয় জীবনে তিনি হলেন আর এক হাস্যকৌতুকশিল্পী ‘অজিত চট্টোপাধ্যায়’। ‘ভানু-জহর-অজিত’ ছিলেন ‘এক আত্মা-এক প্রাণ’। ভানু-জহর যখন অভিনয় জীবনে স্ট্রাগল করছেন, জলসার জগতে তখন অজিতের বেশ নামডাক। ফলে তাঁর কাছে শো-এর বায়না আসত প্রচুর। অজিত প্রায়শই মফস্সলের জলসায় ভানু-জহরকে সঙ্গে করে হাজির হতেন। ধীরে ধীরে দুই বন্ধুকে এমন একটা জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি যেখানে দর্শক সংখ্যা আর শিল্পীর কদর দুই-ই অনেক বেশি। কখনও নিজের শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে, আবার কখনও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে ভানু-জহরকে মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রাস্তা খুলে দিয়েছিলেন অজিত। বন্ধুর এই আত্মত্যাগের ফলে মঞ্চজগৎ থেকে অজিত চট্টোপাধ্যায় ধীরে ধীরে চলে গেলেন পিছনের সারিতে। আর উঠে এল ভানু-জহর জুটি। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জহর রায়ের সম্পর্ক কীরকম ছিল তার অনেক গল্পই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাবার কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েছেন। তখনকার দিনে সিনেমার তারকাদের কাছে এক দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল ‘উল্টোরথ পুরস্কার’। যে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তোলা সত্যজিৎ রায়ের সহাস্য ছবিটিই নিজের ঘরে সাজিয়ে রেখেছিলেন জহর রায়। যাইহোক, এই পুরস্কারটি দর্শকদের ভোটে নির্ধারিত হতো বলে এর আলাদা মাহাত্ম্য ছিল। গৌতম একদা জানিয়েছিলেন,‘‘উল্টোরথ পুরস্কার নিয়ে বাবার ভীষণ ইন্টারেস্ট ছিল। কারণ বাবা ১০ বার শ্রেষ্ঠ কৌতুকাভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিল। এটা একটা রেকর্ড। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছাড়া কেউই এতবার এই পুরস্কার পাননি। বাবা গর্ব করে বলত, ২৯ ইঞ্চি বুকের ছাতি, এইরকম খারাপ চেহারা লইয়া, খারাপ কণ্ঠস্বর লইয়া, তুলসীদা, নবাদা (নবদ্বীপ হালদার), জহর, অজিতের মতো বাঘা বাঘা আর্টিস্টের সঙ্গে লইর্যা, বাইচ্যা আসি কম কথা না।’’ প্রত্যেকবার ভানু ‘উল্টোরথ’ পুরস্কার ঘোষণার আগে গিরীন সিংহের সঙ্গে দেখা করে বা ফোন করে কে ক’টা ভোট পেলেন, কে পুরস্কার পেলেন এইসব খবর সংগ্রহ করতেন। তখনকার দিনে সব আর্টিস্টই এরকম খবর নিতেন। ভানু ফোন করলেই ‘গিরীন সিংহ’ বলতেন, ‘‘মশাই বিরক্ত করবেন না, শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতার পুরস্কারটা আপনার বাঁধা হয়ে গিয়েছে।’’ গৌতম জানিয়েছিলেন, ‘‘একবার বাবা ফোন করাতে গিরীন সিংহ বলেন, ‘মশাই, খুবই আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এবার পুরস্কারটা আপনি পাননি। জহরবাবু পেয়েছেন দুই বেচারা ছবির জন্য। অবশ্য আপনার জন্যই আপনি এবারটি পেলেন না।’ …’’ ভানু এই কথার অর্থ জিজ্ঞেস করাতে গিরীনবাবু বলেন, ‘‘আপনার শখের চোর আর হসপিটাল ছবি দু’টির মধ্যে ভোট কাটাকাটিতে জহরবাবু পুরস্কারটি পেয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ শখের চোর ছবিতে আপনি পেয়েছেন ৮০০ প্লাস, আর হসপিটাল ছবিতে আপনি পেয়েছেন ৭০০ প্লাস। এদিকে জহরবাবু দুই বেচারা ছবির জন্য ৯০০ ভোট পেয়েছেন। শখের চোর আর হসপিটাল মারামারি করাতে জহরবাবু বেরিয়ে গেলেন। ভালোই হয়েছে আপনাকে পুরস্কার দিতে দিতে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।’’ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও পাল্টা বলে দেন, ‘‘জহর পুরস্কার পাইসে এ আমার হার নয়, অর পুরস্কার পাওনের অর্থ আমারই পুরস্কার জেতা।’’

৮-১০ বয়সে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গুরু’ ছিলেন বিপ্লবী ‘দীনেশ গুপ্ত’। ওই বয়সে ভানু বেশিরভাগ সময়েই দীনেশ গুপ্তর সাইকেলে করে ঘুরতেন। বিপ্লবী বইপত্র, এমনকী টিফিন বক্সে রিভলবার পাচার করতেন। দীনেশ গুপ্তর কথা মতোই ‘খুদে গুপ্তচর’ ভানুর কাজ ছিল ঢাকার সদরঘাট দিয়ে কোন পুলিস, সরকারি কর্মচারী আসছে-যাচ্ছে তার খবরাখবর দেওয়া। এই সদরঘাটেই ভানুর আলাপ ঘোড়ার গাড়ির চালক ‘ঢাকাই কুঠি’দের সঙ্গে। এরপর দীনেশ গুপ্ত মারা যাওয়ার পর ভানু খুব প্রভাবিত হন ‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন’-এর ঘটনায়। এই সময় ‘সূর্য সেন’, ‘অনন্ত সিংহ’, ‘লোকনাথ বল’রা ছিলেন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। এরপর ‘অনুশীলন পার্টি’র ‘ত্রৈলোক্য মহারাজ, ‘রাধাবল্লভ গোপ’, ‘ত্রিদিব চৌধুরী’র প্রতিও তাঁর ভয়ানক শ্রদ্ধা ছিল। রাধাবল্লভ গোপের মৃত্যু পর্যন্ত ভানুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৪১ সালে বিএ পরীক্ষার পর ভানু ঢাকায় কোনও এক ‘ব্রিটিশ ইনফর্মার মার্ডার কেসে’ জড়িয়ে পড়েন। শেষে কলকাতায় পালিয়ে বোন ‘প্রকৃতিদেবী’র বাড়িতে ওঠেন। সেখান থেকেই ভানুকে প্রকৃতিদেবীর স্বামী ‘বাদল গঙ্গোপাধ্যায়’ ‘আয়রন অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোলার’-এর অফিসে চাকরি দিয়ে দেন। এইসময় ভানু সকাল ৮টায় বেরতেন আর রাত ১০টায় বাড়ি ফিরতেন। সাধারণত ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত অফিস করতেন। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে ২টোয় অফিস থেকে বেরিয়ে গেট ম্যানেজ করে, ৪টেতে মাঠে ঢুকলেন। ১৯৪১ থেকে ভানুর লাইফ মেম্বারশিপ নং-২১৩। এখানে ভানুর একজন ‘গুরু’ ছিলেন। তিনি কোনও প্লেয়ার নন, সুরকার ‘শচীন দেব বর্মন’। ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখতে রেগুলার আসতেন ‘শচীনকত্তা’। সঙ্গে থাকতেন ‘হিমাংশু দত্ত’ ও মেলোডির মালিক ‘সুশীলবাবু’। হাফটাইমে শচীনদেব বর্মনের চীনাবাদাম, চা ও পান। সিগারেটের তদারকির ভার থাকত ভানুর ওপর। এই খেলার একটা মজার ঘটনা জানা যায় গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্যে, ‘‘ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলা হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গলে তখন সালে, আপ্পারাও প্রমুখ পঞ্চপাণ্ডব দুর্দান্ত খেলছে। হঠাৎ শচীনদেব বর্মন বলে উঠলেন ‘আহা-হা-কী খেলা। কী সুর, কী লয়, কী ছন্দ যেন ফৈয়াজ খাঁর ঠুমরি।’ অমনি মোহনবাগানের গ্যালারি থেকে কে বলে উঠল, ‘ও আর আমাদের খেলাটা বুঝি কিছু না।’ শচীনকত্তা বললেন, ‘আপনাদেরটাও ভালো, তবে সেটা কাঠখোরা, ধ্রুপদ, ধামার।’ …’’ শচীনদেব বর্মনের সঙ্গীতের অসম্ভব ভক্ত ছিলেন ভানু। প্রায় সব রেকর্ড ছিল তাঁর সংগ্রহে। ভানুর সঙ্গীত-অজ্ঞতা নিয়ে একটা গল্প আছে। ‘পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট’ ছবিতে প্রথমে কথা ছিল উত্তমকুমার অভিনয় করবেন। সেই হিসাবে সুরকার ‘নচিকেতা ঘোষ’, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় কয়েকটা গান রেকর্ড করে নেন। পরে উত্তমকুমার সেই চরিত্রটা আর করেননি। ভানুকে সেই জায়গায় কাস্ট করা হয়। এই ঘটনায় নচিকেতা ঘোষ বললেন, উত্তমকে ভেবে গানগুলো করলুম। ভানু পার্টটা করছে জানলে, সুরই দিতুম না। আসলে উনি ভেবেছিলেন, উত্তম নেই, ছবি ফ্লপ হবে। এরপর ছবি হিট হলে বললেন, না লিপটা ভানু ভালোই মিলিয়েছে। এরপর শচীনকর্তা পাকাপাকিভাবে বম্বে চলে গেলেন। আর ভানুরও কাজের চাপ বাড়াতে ময়দান যাওয়া কমতে থাকল।
খেলা না থাকলে চৌরঙ্গি পাড়ায় গিয়ে সিনেমা দেখতেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর টালিগঞ্জ স্টুডিওপাড়ায় পার্টের জন্য দরবার। এখানে ছিলেন ভানুর গুরু-স্থানীয় পরিচালক ‘সুশীল মজুমদার’ ও ‘নির্মল দে’। ভানুকে ফিল্মে প্রথম সুযোগ করে দেন ঢাকার বিপ্লবী ও পরে কলকাতার চিত্র প্রযোজক জীবন দত্ত’। পরিচালক ‘সুশীল মজুমদার’, ‘বিভূতি চক্রবর্তী’র সঙ্গে ভানুর আলাপ করিয়ে দেন তিনিই। বিভূতি চক্রবর্তীর ‘জাগরণ’ ভানুর প্রথম ছবি। ওপার বাংলা থেকে আসা ‘বাঙাল’ ভানুকে শুধু চেহারা দেখেই নাকি ‘জাগরণ’ ছবির জন্য নির্বাচন করেছিলেন ‘বিভূতি চক্রবর্তী’। কারণ হিসেবে বলেছিলেন, ‘‘আমার ছবিতে দুর্ভিক্ষপীড়িত চিমসে চেহারার একটা চরিত্র আছে, সেটা তুমি করবে।’’ পরে সুশীল মজুমদারের ছবি ‘সর্বহারা’ ভানুকে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। ভানুর দাদা-স্থানীয় সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ছিলেন ‘সর্বহারা’র সুরকার। সিদ্ধেশ্বরবাবুর কাছে গান শিখতেন নীলিমাদেবী। এই ছবিতে নীলিমাদেবীকে দিয়ে তিনটে গান গাওয়ান তিনি। পরবর্তীকালে সিদ্ধেশ্বরবাবুর মধ্যস্থতাতেই ভানু-নীলিমার বিয়ে হয়।
কমেডিয়ান হিসেবে জগদ্বিখ্যাত হলেও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিরিয়াস চরিত্রের প্রতি টান ছিল শুরু থেকেই। ‘নির্মল দে’র কাছে ভানু একটা সিরিয়াস পার্ট চাইতে গিয়েছিলেন। ‘নতুন ইহুদি’ নাটকে ভানুর অভিনয় দেখে দারুণ খুশি হয়েছিলেন নির্মল দে। কিন্তু তিনি ভানুকে বললেন, ‘‘তোমাকে আমি কমেডি রোল দেব। ভালো মানাবে।’’ ‘বসু পরিবার’ ছবিতে চান্স দিলেন। প্রায় ওই একই সময় ভানু পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের কাছেও একটা সিরিয়াস চরিত্রে কাস্ট করার অনুরোধ নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু উনিও কমেডি চরিত্রেই ‘পাশের বাড়ি’ ছবিতে ভানুকে নেন। এটাই ছিল ভানুর সত্যিকারের বড় ব্রেক। ‘রাহুলদেব বর্মন’ একবার বম্বের কমেডিয়ান ‘মেহমুদ’কে ভানুর সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে আসেন। ‘মেহমুদ’ ভানুকে বলেন, ‘‘আমি পাশের বাড়ি ১০ বার দেখেছি। অসামান্য। এই ছবিটি আমি হিন্দিতে করছি এবং আপনার পার্টটা করব আমি। আশীর্বাদ করুন যাতে ভালো করতে পারি।’’ মেহমুদের ‘পড়োশন’ ছবিটি ‘পাশের বাড়ি’ থেকেই তৈরি হয়েছিল।
এরপর নির্মল দে’র ছবি ‘সাড়ে ৭৪’। ম্যাসিভ হিট। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় রাতারাতি স্টার হয়ে গেলেন। যেটা সবচেয়ে গর্বের বিষয়, ছবিতে অতগুলো বাঘা বাঘা কমেডিয়ানের মধ্যে থেকে তিনিই সে বছর ওই ছবির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনয়ের জন্য ‘উল্টোরথ’ পুরস্কার পেলেন। দর্শকদের ভোটে এই পুরস্কার দেওয়া হতো। তাই এটা শিল্পীদের জন্য ছিল বিরাট সম্মানের। পরে যখন বম্বেতে তিনি ‘সাগিনা মাহাতো’র শ্যুটিং করতে গিয়েছিলেন তখন একদিন আড্ডায় কেষ্ট মুখার্জি তাঁকে বলেছিলেন, ‘‘দাদা সাড়ে ৭৪’ আপনার বেস্ট অ্যাক্টিং। এই ছবির একটা সিন যেখানে তাড়াতাড়ি আপনি পা থেকে চটি খোলার চেষ্টা করছেন কিন্তু খুলছেন না। এই আইডিয়াটা আমি একটা হিন্দি ছবিতে মেরে দিয়েছি।’’
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে নিয়ে অসম্ভব ঠাট্টা করতে পারতেন, যেটা বড় অভিনেতার অন্যতম বড় লক্ষণ। তবে তাঁর আত্মসম্মানবোধও ছিল প্রবল। নির্মল দে প্রায় সব ছবিতেই ভানুকে নিতেন। ওঁর শেষ ছবি ‘বিয়ের খাতা’র অরিজিনাল কাস্ট লিস্টে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছিল। কিন্তু বাগড়া দিলেন তখনকার বিখ্যাত প্রোডাকশন ম্যানেজার ‘বিমল ঘোষ’। উনি নির্মল দে’কে বলেন, ‘‘কী ব্যাপার ভানু ছাড়া ছবিই করছেন না। আপনি কি ভানু-ম্যানিয়ায় ভুগছেন?’’ ব্যস, ভানুকে আর নির্মলবাবু ছবিতে নিলেন না এবং কেন নিলেন না সে নিয়েও গল্প আছে। এর কিছুদিন বাদে বিমল ঘোষ ভানুর কাছে এলেন নতুন প্রজেক্ট নিয়ে। উনি একটি ছবি করছেন ‘বধূ’। তার একটি মুখ্য চরিত্রে ভানুকে নিতে চান। ভানু যেন মুখিয়েই ছিলেন এমন একটি সুযোগের জন্য। বিমল ঘোষকে বললেন, ‘‘সে কী কথা। আপনেই না নির্মল দারে ভানু ম্যানিয়া হইসে বইল্যা আমার রোলটা ক্যাঁচাইয়া দিসিলেন? আর অখন আমারে দিয়াই কাজ করাইতে আইসেন, আপনারও কি ভানু ম্যানিয়া হইল?’’ বিমল ঘোষও চালাক লোক। বললেন, ‘‘না, না, সেকি। তোমার-আমার সম্পর্ক খারাপ করার জন্য শত্রুরা ইন্ডাস্ট্রিতে মিছে কথা কইছে।’’
ভানুর একটা বড় গুণ ছিল কোনও দিন উপকারীর উপকার ভুলতেন না। ‘বিকাশ রায়’ একবার ১৯৫০-’৫১ সালে রেশন তোলার জন্য ভানুকে ৪০ টাকা ধার দিয়েছিলেন। এই কথা তাঁর পরিচিতদের সবসময় বলতেন ভানু। এরপর বিকাশ রায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলে, ভানু সবসময় তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে বসতেন। কোনও দিনও বিকাশ রায়ের পাশের চেয়ারে বসেননি। এই ঘটনায় বিকাশ রায় খুবই অস্বস্তিতে পড়তেন, কিন্তু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে টলাতে পারেননি।
পরিচালক সুশীল মজুমদার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম জীবনে অনেক ছবিতে চান্স দিয়েছেন। ভানুর তৃতীয় ছবি (প্রথম রিলিজ) ‘অভিযোগ’-এ সুযোগ দিয়েছিলেন। যদিও টাইটেলে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছিল না (প্রভৃতির মধ্যে ছিল)। পরেও ‘সর্বহারা’, ‘দিগভ্রান্ত’, ‘রাত্রির তপস্যা’ প্রভৃতি ছবিতে বেশ বড় চরিত্র দিয়েছিলেন। ১৯৭৩-’৭৪ সালে এহেন সুশীল মজুমদারের ফিল্মে যখন আর কাজটাজ নেই, ভানু তৎকালীন মন্ত্রী ‘সুব্রত মুখোপাধ্যায়’কে ধরে সুশীল মজুমদারের জন্য দুটি সরকারি ডকুমেন্টারি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। রবি ঘোষ যখন ‘নিধিরাম সর্দার’ ছবি করার কথা ভাবছেন, তখন তিনি প্রায়ই পরিচালনা, আর্টিস্ট সিলেকশন প্রভৃতি নিয়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেন। একদিন ‘রবি ঘোষ’ বললেন, ‘আমার ছবিতে বয়স্ক ভিলেনের জন্য একজন আননোন ফেস, ভালো অভিনেতা দরকার।’ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে সুশীল মজুমদারের নাম প্রস্তাব করলেন। প্রথম দিকে রবি ঘোষ একটু দোনামোনা করছিলেন। কারণ এতদিন উনি অভিনয় করেননি। প্রথম দিন সুশীল মজুমদারের শ্যুটিংয়ের পর ভানু বন্দ্যোপাধ্যাকে ফোন করেন রবি ঘোষ। উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, ‘‘ভানুদা কী আর্টিস্ট দিয়েছেন। কী গলার মডিউলেশন, কী দারুণ বেস।’’ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুব খুশি হয়ে বলেন, ‘‘এই জানবি! আমি বেস্ট লোক ছাড়া কখনও কাউকে রেফার করি না।’’
নিজে যেমন অসাধারণ কমেডি অভিনয় করতেন, তেমনই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেন্স অব হিউমারও ছিল অতুলনীয়। বিশ্বররেণ্য পরিচালক হয়ে ওঠার আগেও ‘সত্যজিৎ রায়’কে বিলক্ষণ চিনতেন তিনি। আত্মকথা ‘ভানুসমগ্র’তে নিজেই লিখছেন, ‘‘ওঁকে সুকুমার রায়ের পুত্র ‘লম্বা মানিক’ হিসেবে চিনতাম।’’ ‘পথের পাঁচালী’ দেখে অভিভূত ভানু একদিন বসুশ্রী সিনেমার অফিসঘরে ঢুকে দেখেন কর্ণধার ‘মন্টু বসু’ ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে বসে আছেন সত্যজিৎ। ঘরে ঢুকেই ভানু চেঁচিয়ে বললেন, ‘‘আরে মানিকবাবু এই সত্যজিৎ রায়টি কে? এ তো সাংঘাতিক ছবি বানিয়েছে।’’ তৎক্ষণাৎ মন্টুবাবু বলে ওঠেন, ‘‘আরে মানিকবাবুই তো সত্যজিৎ রায়।’’ সঙ্গে সঙ্গে ভানুর কণ্ঠ থেকে অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী বেরোয়, ‘‘আরে মশাই, কী ছবি বানিয়েছেন। আপনি তো কাননবালার চেয়ে বেশি পপুলার হয়ে যাবেন।’’ সত্যজিৎ রায় পরে ভানুকে নিয়ে বলেছেন, ‘‘ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অজস্র ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং যেখানে বিশেষ কিছু করার নেই সেখানেও করেছেন। আশ্চর্য এই যে, যাই করেছেন, তা বহরে ছোট হোক বা বড়ই হোক, তারমধ্যে তাঁর সাবলীলতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন। সর্বজন প্রশংসিত বিরল অভিনেতাদের মধ্যে ভানুবাবু একজন। আমার কোনও ছবিতে যে তিনি অভিনয় করেননি তার মানে এই নয় যে আমি তাঁর অভিনয়ের কদর করি না। প্রথমে মঞ্চে ‘নতুন ইহুদি’ এবং পরে চলচ্চিত্রে ‘বসু পরিবার’, ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এর সময় থেকেই ভানুবাবুর সহজ ও বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করে এসেছে।’’ আপামর জনসাধারণ তো বটেই, মানিকবাবুর মতো ব্যক্তিত্বও কেমন তাঁর অভিনয়ের গুণমুগ্ধ ছিলেন এই কথাই তার প্রমাণ।
ভানুর অভিনয়ে আসা কিন্তু একেবারেই আকস্মিক। স্টেজের নীচে দাঁড়িয়ে পাড়ার নাটক দেখছে ছোট্ট ভানু। ওপর থেকে কোনও এক খুদে অভিনেতা দুষ্টমি করে লাথি কষায় মাথায় – ‘‘হালায় ওই লাথখান কোনওদিনও ভুলি নাই। ওই দিনই ঠিক কইরা নিছিলাম, অগ্যো দ্যাখাইয়া ছাড়ুম।’’ ওয়াড়ি ক্লাবের ‘রণবীর’ নাটকে প্রথম সুযোগ এল। তখন সবে ক্লাস সিক্স। উদয়সিংহর চরিত্রে অভিনয় করলেন ভানু। কলকাতায় এসে পাড়ার নাটক ‘চন্দ্রগুপ্ত’য় চাণক্য সাজলেন। সে অভিনয় এতই সাড়া ফেলল যে পাড়ারই একজন ডাক্তার তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তখনকার নামকরা পরিচালক সুশীল মজুমদারের কাছে।
তবে ভানুর প্রথম সিনেমায় অভিনয় কিন্তু বিয়ের পরে। এইজন্যে অনেকে বলতেন স্ত্রীভাগ্যেই নাকি ভানুর উত্থান। আর এখানেও একটা চমৎকার গল্প আছে।
বেতারশিল্পী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভানুর বিয়ে হয় ’৪৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। আর তার দিন তিনেক পরেই বিপত্তি। কী হয়েছিল? শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে এসেছে বাপের বাড়ি। অফিস থেকে ফিরে ভানুই নীলিমাদেবীকে তাঁর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। স্ত্রীকে বলে গিয়েছেন, ‘রাধা ফিল্ম স্টুডিও থেকে আসছি। কাজ আছে।’ নীলিমাদেবীর বাড়িটা ছিল স্টুডিওপাড়াতেই। একেবারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশের বাড়ি। নীলিমাদেবীর বাড়ির একদিকে ছিল ‘রাধা ফিল্ম স্টুডিও’। অন্যদিকে ‘ভারতলক্ষ্মী স্টুডিও’, যেটা এখনকার ‘নবীনা সিনেমা’। ভানু পৌঁছে তো দিলেন, কিন্তু ফেরার নামটি নেই। শীতের বেলা। রাস্তাঘাটও শুনসান। একটু সন্ধে গড়াতেই অনেকটা রাত মনে হয়। বাড়ির সবাই একে একে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ছে। আর কিনা নতুন জামাই বেপাত্তা! শেষে বাধ্য হয়ে শ্বশুরমশাই জামাই খুঁজতে বেরলেন। স্টুডিওতে গিয়ে খোঁজ করতে দারোয়ান একটা লোকের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। কালিজুলি মাখা। চিটচিটে ছেঁড়া চট গায়ে জড়ানো। ভালো করে নজর করে বুঝলেন, এই লোকটিই তাঁর জামাই। কী একটা ফিল্মের নাকি শ্যুটিং হচ্ছে, আর তাতে অভিনয় করছে সে। কাজ শেষ হতে তখনও ঢের দেরি। রাগে গরগর করতে করতে নীলিমাদেবীর বাবা বাড়ি ফিরলেন। এমন বেআক্কেলে ছেলের সঙ্গেই কিনা শেষে মেয়ের বিয়ে দিলেন! এই ছবিই ছিল বিভূতি চক্রবর্তীর ‘জাগরণ’।
চল্লিশের দশকের শেষ। পূর্ববাংলা থেকে তখন দলে দলে উদ্বাস্তু আসছে। তাদের সাহায্য করতে সীমান্তে, স্টেশনে শিবির গড়ছে ‘মেঘনাদ সাহা’র নেতৃত্বাধীন ‘ইস্টবেঙ্গল রিলিফ কমিটি’। শয়ে শয়ে স্বেচ্ছাসেবক রাতদিন কাজ করছে। সেই দলে ছিলেন ভানুও। একটি অপেশাদার নাটকের দলও গড়েছিলেন। তারই এক সদস্য ছিলেন সলিল সেন। উদ্বাস্তুদের নিয়ে তিনি ‘নতুন ইহুদি’ নাটকটি লেখেন। সেখানে ভানুর অভিনয় তখনকার তাবড় অভিনেতাদের মন জয় করেছিল। নজরে পড়ে যান ছবি বিশ্বাসের। লোকে বলে, নতুন ইহুদির সাফল্যই ভানুকে পুরোদস্তুর অভিনেতা বানিয়ে দেয়। ‘নতুন ইহুদি’ নিয়ে আর একটা মজার ঘটনা আছে ভানুবাবুর জীবনে। আজকের প্রখ্যাত অভিনেত্রী ‘সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়’ তখন ফ্রক পরা মেয়ে। স্কুল ছুটির পর খালি পায়ে বন্ধুদের সঙ্গে বাঙাল ভাষায় কথা বলতে বলতে চলেছে। ভানুর নাটকের দলে তখন অভিনেত্রী চাই। রাস্তায় ছোট্ট সাবিত্রীকে মনে ধরে ভানুর। কাছে গিয়ে বললেন, ‘‘অভিনয় করবা?’’ মেয়েটি কটমট করে তাকাল। তারপর বলল, ‘‘আমাকে বলছেন কেন, বাবাকে বলুন।’’ তারপরই ট্রামে উঠে পালাল। এবার হন্যে হয়ে মেয়েটির বাড়ি খুঁজতে বেরলেন ভানু। শেষমেশ বাড়ি খুঁজে পেয়ে দেখলেন মেয়েটির বাবা সম্পর্কে ভানুর মামা হন। সেই সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম মঞ্চে নামা।
পরের উপকার করে বেড়ালেও বাড়িতে কুটোটি নাড়তেন না ভানু। স্মৃতিচারণায় নীলিমাদেবী বলছেন, বাড়িতে ঠাকুর ছিল ‘যজ্ঞেশ্বর’। বাজারহাট সেই করত। একবার আমার শাশুড়ি বললেন, ‘‘কী সব বাজার আনে, তুই যদি করতি কত ভালো হইত, ক’তো!’’ তখনকার মতো মায়ের কথায় মাথা নেড়ে কেটে পড়ল। পরদিন সকাল থেকে থলে হাতে বেরতে লাগল। সবাই ভাবছ ওই সব করে। মা-ও খুশি। কিন্তু একদিন সব জারিজুরি ফাঁস। জানা গেল, বাজারটা যথারীতি ঠাকুরই করে। ও শুধু থলে হাতে বাড়ি থেকে বেরয় আর ঢোকে। তবে খেতে নাকি ভীষণ ভালোবাসতেন, যাঁকে বলে খাদ্যরসিক। ভীষণ প্রিয় ছিল ইলিশ। ভানুপুত্র গৌতম পরে জানিয়েছিলেন, ‘‘বাবা ইলিশ পেলে আর কিছু চাইত না। ভাতের ওপর রাখত ভাজা ইলিশ। খানিক বাদে সেখান থেকে মাছ সরিয়ে তলার তেল ভাতটা খেত। আবার ওপাশ থেকে সরিয়ে অন্যদিকে মাছটা রেখে সেই ভাতটাও খেত। আর ভালোবাসত কই, ট্যাংরা। বিশেষ করে তেল কই। তবে বড় কই হতে হবে। ওসর ছোট কই-টই চলত না বাবার।’’ গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ফেভারিট ছিল ভানুবাবুর এই ‘তেল কই’। পরিবার নিয়ে চলে আসতেন তেল কই খেতে। আর রবিবার হলে পাঠার মাংস ছিল মাস্ট। ইলিশ নিয়ে চমৎকার একটা দৃশ্য আছে ভানু অভিনীত একটি ছবিতে। ‘ওরা থাকে ওধারে’, ১৯৫৪-র ছবি। দু’মাসের ভাড়া বাকি, তাও ধীরাজ ভট্টাচার্য বাজার থেকে জোড়া ইলিশ কিনে এনেছেন। বাড়িওয়ালা খোঁচা দিয়ে কথা শোনাতেই রুখে দাঁড়ালেন ভানু, ‘‘ইলশা তুইল্যা কথা কইবেন না!’’ নিজে যেমন খেতে ভালোবাসতেন, তেমনই লোককে খাওয়াতেও ভালোবাসতেন খুব। তাঁর একটা বাতিক ছিল। যখন তখন লোকজনদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বসতেন। আর সেটা নীলিমাদেবী জানতে পারতেন একদম শেষ মিনিটে। কোনওদিন সেভাবে বাইরে ঘুরতে না গেলেও পরিবারকে নিয়ে রেস্তরাঁয় খেতে যেতেন ভানু। গড়িয়াহাটের ‘নিরালা’য় বা ‘কোয়ালিটি’তে। বসুশ্রীর মালিক মন্টু বসুর পরিবারের সঙ্গে ভানুর পরিবারের দারুণ হৃদ্যতা ছিল। ফলে সবাই মিলে খেতে যাওয়া লেগেই থাকত।
আর ভালোবাসতেন গান। নীলিমাদেবীর গলায় প্রায়ই শুনতে চাইতেন ‘বাঁশি বাজাব কবে’। শচীনকর্তার পল্লিগীতি হলে তো কথাই নেই। শচীনকর্তা ছাড়া ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আরও এক গায়ক। ‘সুধীরলাল চক্রবর্তী’। রাসবিহারীর মোড়ে অমৃতায়ন রেস্টুরেন্ট ছিল ভানু ও তাঁর বন্ধুদের আড্ডাস্থল। সেখানে ‘অমূল্য সান্যাল’, ‘রসরাজ চক্রবর্তী’, মাউথ অর্গান শিল্পী ‘প্রফুল্ল চক্রবর্তী’রা আড্ডা মারতেন। খাওয়াদাওয়া চলত। আর ছিল লেক মার্কেটে ‘রাধুর চায়ের দোকান’। সুধীরলাল এখানেই থাকতেন। ভানুর সঙ্গে সুধীরলালের আলাপ করিয়ে দেন এইচএমভির ‘পবিত্র মিত্র’। সুধীরলাল ভদ্রলোকটি ছিলেন খুব আমুদে। একবার ‘হিন্দুস্তান’ রেকর্ড-এ সুধীরলালের সঙ্গে গিয়েছেন ভানুও। পাশে এসে বসলেন ভারতের আধুনিক সঙ্গীতের পিতৃপ্রতীম ‘পঙ্কজ মল্লিক’। কিন্তু পঙ্কজ ও সুধীরলালের কথা নেই। দু’জনে দু’দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে। হঠাৎ পঙ্কজ মল্লিক সিট ছেড়ে উঠে সুধীরলালের হাত ধরে বললেন,‘‘বাঃ, সুধীরভাই কী গানটাই না গাইলেন। মধুর আমার মায়ের হাসি ভারতীয় সঙ্গীতের সম্পদ।’’ সুধীরলাল বললেন, ‘‘আপনি যে আমাকে চিনতে পেরেছেন এতেই আমি উল্লসিত।’’ এরপর পঙ্কজ মল্লিক চলে যেতেই ভানুকে সুধীরলাল বললেন, ‘‘… ‘মধুর আমার’ গানটি যেই হিট হয়েছে অমনি নিজে এসে কথা বললেন। অথচ কয়েকদিন আগেই এক ফাংশনে আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন।’’ এই সুধীরলালের কাছেই রোজ গান শিখতে আসতেন ‘শ্যামল মিত্র’, ‘গায়ত্রী বোস’, ‘উৎপলা সেন’, ‘গীতা বর্ধন’রা। রাধুর চায়ের দোকান তাই ফাংশন অর্গানাইজারদের কাছে ছিল মোক্ষলাভের জায়গা। কেন না, একাধারে সুধীরলালের মতো বড় গায়ককে হাতের নাগালে পাওয়া, আবার কমিকের জন্য ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাউথ অর্গান বাজিয়ে ‘প্রফুল্ল চক্রবর্তীর’ও দেখা মিলত। এতগুলো আর্টিস্ট একসঙ্গে পাওয়া যায় বলে সুধীরলালের বাড়িতে কিম্বা রাধুর চায়ের দোকানেই অনেক জলসার কনট্রাক্ট সই হতো। অনেকসময় বিনা পয়সাতেও ফাংশন করতে হতো। এই ধরনের ফাংশনকে বলা হতো ‘আক্ষেপ’। মানে টাকাপয়সার কোনও বালাই নেই, অনুরোধই সম্বল। আর সুধীরলালের ছিল খুব গাড়ি চড়ার শখ। যদিও নিজের গাড়ি ছিল না। আসলে ‘পঙ্কজ মল্লিক’, ‘রাই বড়াল’, ‘কাননদেবী’ ছাড়া সঙ্গীতজগতে তখন কারও গাড়ি ছিল না। একবার এক ভদ্রলোক পন্টিয়ার গাড়িতে সুধীরলাল আর ভানুকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফাংশন করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে, ফাংশন অর্গানাইজাররা ‘বিশেষ খাতির’-এর ব্যবস্থা করেননি। কিন্তু সুধীরলালকে মিথ্যা বলে যাচ্ছেন, এখনই ব্যবস্থা করছি। প্রায় আটটা নাগাদ হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে ভানুকে বললেন সুধীরলাল – ‘‘চলুন বাড়ি যাই।’’ ফাংশন পার্টি হই হই করে উঠল। – এই এক্ষুনি আপনাকে মঞ্চে তুলছি। অবস্থা বেগতিক দেখে অর্গানাইজারদের একজন বললেন, ‘‘এই এক্ষুনি আসছে, আপনি বসে পড়ুন। আপনার গান হয়ে গেলেই …’’ সুধীরলালও হেঁয়ালি করে বললেন, ‘‘পাগল নাকি, আমার সুরা না হইলে সুরই বাইরইব না গলা দিয়া।’’ এহেন সুধীরলাল ভানুকে খুব পছন্দ করতেন। উনি কখনই গান শেখাতে কারও বাড়ি যেতেন না। কিন্তু ভানুর খাতিরে নীলিমাদেবীকে বাড়ি গিয়ে গান শেখাতেন। সুধীরলালের সুরে হিন্দি গান ‘এক অমর বসন্ত কী ছায়া’ রেকর্ড করার কথা ছিল নীলিমাদেবীর। পরে অবশ্য গানটি রেকর্ড করেন উৎপলা সেন। একবার এই ভানুই সুধীরলালের রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেইসময় রেগুলার পাড়া, অফিসে থিয়েটার, ফাংশন করে বেড়াচ্ছেন ভানু। সিনেমাতে অভিনয় চলছে টুকটাক। একটু আধটু নামটামও হয়েছে। সুধীরলালের তখন বেশ নামডাক। এই সময় লেকমার্কেটের মস্তানরা সুধীরলালের ওপর জোর-জুলুম শুরু করল। তখন বন্ধু ‘নির্মল চক্রবর্তী’, ‘রুনু বোস’দের নিয়ে সুধীরলালের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করেন এই ভানুই। আসলে অন্যায় কখনও বরদাস্ত করেননি। জোরজুলুম করলে তো ভয়ানক রেগে যেতেন।
খেলা ভালোবাসলেও অভিনয়ই যে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, পেশা-নেশা সব ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সাফল্য করায়ত্ত করেও অনুশীলনে ফাঁকি দেননি কখনও। তিনি যখন রেডিওতে কাজ শুরু করেন, তখন লাইভ টেলিকাস্ট হতো, আর তাই নিয়ে টেনশন করতেন খুব। তবে নিয়ম করে অন্তত বার চারেক রিহার্সাল করতেন। পরে যখন লাইভ অনুষ্ঠান উঠে গিয়ে রেকর্ডিং শুরু হল, তখন ভুল ত্রুটি শুধরে নেওয়ার সুযোগ থাকায় অনুষ্ঠান করা তুলনায় সহজ হয়ে গেল। কিন্তু ভানু নিজের অভ্যাস বদলাননি। তখনও নাকি চারদিনই রিহার্সাল দিতে ছুটতেন। ভানু-কন্যা বাসবী এক জায়গায় বলছেন, ‘‘বাবা যে কোনও অনুষ্ঠান নাটক বা যাত্রার জন্য মঞ্চে ওঠার আগে প্রচণ্ড টেনশন করতেন। ছটফট করতেন। যেন প্রথমবার মঞ্চে উঠছেন এমনই অস্থির হয়ে থাকতেন ভিতরে ভিতরে। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, যেদিন এটা থাকবে না, সেদিন শিল্পী হিসেবে আমার দিনও শেষ হয়ে যাবে।’’ রেডিওতে অনুষ্ঠান করে যে সামান্য টাকা পেতেন তা দিয়ে গাড়ির তেলখরচটুকুও উঠত না। বেশিরভাগ সময় সহঅভিনেতারাও থাকতেন না। কিন্তু তিনি ঠিক যেতেন।
পি জি উডহাউসের লেখা আর চার্লি চ্যাপলিনের খুব বড় ভক্ত ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের কর্মজীবনেও চার্লির বোধের উপরেই ভরসা রেখেছিলেন। নিজেই লিখেছেন, ‘‘আমি বিশ্বাস করি, পরিবেশন ঠিকমতো হলে সাধারণ মানুষ সেটা উপলব্ধি করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, চার্লি চ্যাপলিনের কোনও ছবিই সাধারণ মানুষের দুর্বোধ্য নয়।’’ ছবিতে অভিনয় করতে ভালোবাসলেও, নাটক যাত্রার মতো মাধ্যম ছিল তাঁর ভীষণ প্রিয়। কারণ দর্শকদের পছন্দ-অপছন্দ যাইহোক না কেন সেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তিনি উপলব্ধি করতে চাইতেন।
মনে করতেন সমাজের সমস্যা তুলে ধরা প্রত্যেক শিল্পীর একটা নৈতিক দায়িত্ব। নাটকের পাশাপাশি কৌতুক নকশার মাধ্যমেও সেই চেষ্টাই চালিয়েছেন আজীবন। এ বিষয়ে সম্পদ ছিল তাঁর মুখের ভাষা। প্রতি বছর গ্রামাফোন কোম্পানি থেকে বেরত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিক নিয়ে শারদ অর্ঘ্য। আর তার জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকত শ্রোতারা। কমিক রেকর্ডের ঐতিহ্য একশো বছরেরও বেশি প্রাচীন। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর দুটি কৌতুক নকশার রেকর্ড – ‘বিকট বিরহ’ এবং ‘চাষার খেদ’। একইসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের দুটি কমিক – ‘স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সোহাগ’ আর ‘স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সোহাগ।’ পরবর্তীকালে নবদ্বীপ হালদার থেকে রবি ঘোষ অনেক শিল্পীই নিজেদের কমিক রেকর্ড করেছেন। কিন্তু এই পরম্পরায় ধারাবাহিকতা এবং প্রভাবে ভানুর কাছাকাছি পৌঁছতে পারেননি কেউই। ভানুর রেকর্ড প্রকাশিত হলে যাঁরা কিনতেন, তাঁদের থেকে অনেক বেশি সংখ্যক শ্রোতা রেকর্ড ডিলারের দোকানে বাজানো কৌতুক নকশা কার্যত মুখস্থ করতেন। পরবর্তীকালে নিজেরা আড্ডায় সেই কৌতুক স্মৃতি থেকে তুলে এনে বাহবা কুড়োতেন। দৈনন্দিন জীবন থেকেই ভানু তাঁর কমিকের রসদ সংগ্রহ করতেন। যেমন, যাঁরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়, তাদের নিয়ে ‘চোখে আঙুল দাদা’, দাম্পত্য দ্বন্দ্বের চিরকালীন বিষয় নিয়ে ‘কর্তা বনাম গিন্নি’। ক্রস কানেকশন নিয়ে যখন সাধারণ মানুষ জেরবার তখন ভানু নিয়ে এসেছেন ‘টেলিফোন বিভ্রাট’। আবার পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে বাড়াবাড়ির সময় তাঁর কৌতুক নকশা ‘পরিবার পরিকল্পনা’ শ্রোতাদের মুখে মুখে ফিরত। এভাবেই ‘চন্দ্রগুপ্ত’ থেকে ‘মহাকাশ ভ্রমণ’ ভানুর কমিক রেকর্ডের অংশবিশেষ শ্রোতাদের স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে আজও। সিনেমার মতোই নিজের নামেও কৌতুক নকশা করেছেন তিনি— ‘লর্ড ভানু’ বা ‘ভানু এল কলকাতায়।’ এমনকী ‘নব রামায়ণ’ কৌতুক নকশায় রাম-লক্ষ্মণ-সীতার অস্বাভাবিক আচরণ নিয়ে যে সব স্যাটায়ার ভানু করেছেন, আজকের জমানায় তা প্রকাশিত হলে তিনি নিশ্চিত বিপদে পড়তেন।
লোককে এত হাসাতেন অথচ বাস্তবে তাঁর মতো জেদি মানুষের খোঁজ পাওয়া ছিল দুষ্কর। শিল্পীদের স্বার্থরক্ষায় সংগঠন তৈরি করেছিলেন অভিনয় জীবনের মধ্যগগনে। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে যখন ধর্মঘট হয়েছিল, তখন অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি ও অভিনেতা ছবি বিশ্বাস যুক্ত হন ‘সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন’-এর আন্দোলনে। প্রযোজকদের একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন বারবার। এই জেদি স্বভাবের জন্যই উত্তমকুমারের সঙ্গেও একসময় তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। অথচ নিজের ছোটভাইয়ের মতো ভালোবসাতেন মহানায়ককে। উল্টোদিকে উত্তমকুমারও তাই। ‘ভানুদা’ ডাকতেন, আবার ‘তুই’ বলে সম্বোধন করতেন। ‘কাঞ্চনমূল্য’ ছবিটি তৈরি করতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে যাঁরা অর্থসাহায্য করেছিলেন, উত্তমকুমার ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ‘ভ্রান্তিবিলাস’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য ভানুকে ‘সোনার গিনি’ দিয়ে অ্যাডভান্স করেছিলেন তিনি। এমন ভালো সম্পর্কেও তৈরি হয়েছিল সংঘাত। ষাটের দশকে ‘অভিনেতৃ সংঘ’ ভেঙে ‘শিল্পী সংসদ’ তৈরি করলেন উত্তমকুমার। মহানায়কের সঙ্গে সেখানে চলে গেলেন ‘বিকাশ রায়’, ‘অনিল চট্টোপাধ্যায়’রা। এদিকে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থেকে গেলেন ‘সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়’, ‘অনুপকুমার’রা। ‘কালো’ তালিকাভুক্ত করা হল ওঁদের। এই সময় সত্যজিৎ রায়ের ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ রিলিজ করবে। তাতেও বাধা দেওয়া হতে পারে বলে খবর রটে গেল। একজোট হলেন ভানু, সৌমিত্র, অনুপকুমার, অজিত লাহিড়ী, সৌমেন্দ্যু রায়রা। বিজলি সিনেমায় গন্ডগোল হতে পারে আঁচ করে টানা ৮ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতেন। হাতে কাজ নেই। কিন্তু মনে জেদ। মাথা নোয়াবেন না কিছুতেই। যাত্রা দল গড়লেন। নিলিমাদেবীর স্মৃতিচারণে জানা যায়, ‘‘যে মানুষ নরম বিছানা ছাড়া শুতে পারতেন না, তিনিই গ্রামে-গঞ্জে শতরঞ্জি পেতে গাছের তলায় ঘুমতেন। বাড়িতে থাকলে যিনি এটা-ওটা খেতেন না, সেই তিনিই দিনের পর দিন চপ, ফুলুরি, মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছেন। একবার একটা আধভাঙা বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার সময় তো বুকের ওপর সিলিংয়ের চাঙড় খুলে পড়েছিল।’’ এই সময়ই প্রথমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন ভানু। তাঁর পুত্র গৌতমবাবুর কথায়, ‘‘আসলে উত্তমকাকুর সঙ্গে বিচ্ছেদ কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি বাবা। পরে অবশ্য সব মিটমাট হয়ে যায়।’’
বেশ কিছু ছবি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতাছাড়া হয়েছিল। তারমধ্যে কয়েকটি মন্দ ভাগ্যের দরুন। যেমন – নীহাররঞ্জন গুপ্তর একটি গল্প নিয়ে ছবি করা তাঁর বহুদিনের ইচ্ছে ছিল। কিরীটী রায়ের ভূমিকায় ‘প্রদীপ কুমার’, নায়িকা ‘সুচিত্রা সেন’। ভানুর এই ছবি করা হয়নি। তাঁকে বাদ দিয়েই অনন্ত সিংহ (ঢাকায় ভানুর পরিচিত বিপ্লবী অনন্ত সিংহ পরবর্তীকালে ছবি তৈরির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন) ছবিটি করেছিলেন। আরও দুটো ছবি নিয়েও তিনি খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। প্রযোজক হেমেন গঙ্গোপাধ্যায় ‘অন্য নগর’ নামে একটি ছবি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। ছবিটির শ্যুটিং হওয়ার কথা ছিল লন্ডনে এবং অভিনয় করার কথা ছিল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপ কুমারের। প্রায় একই সময়ে পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ‘আনন্দ সংবাদ’ নামে একটি ছবি করার কথা ভেবেছিলেন। এই ছবিতে অভিনয় করার কথা ছিল রাজকাপুর, উত্তমকুমার ও ভানুর। কিন্তু উত্তমকুমার রাজি না হওয়াতে ছবিটা শেষপর্যন্ত হয়নি। পরে এই ছবিটাই হিন্দিতে তৈরি হয়— ‘আনন্দ’। জনি ওয়াকার যে চরিত্রটি করেন, সেই চরিত্রটি ‘আনন্দ সংবাদ’-এ করার কথা ছিল ভানুর।
অন্যের যাতে একটু উপকার হয় তার জন্য নিজের ক্ষতিকেও হাসিমুখে মেনে নিতেন ভানু। পরবর্তীকালে নিজের কেরিয়ার সমস্যায় পড়তে পারে জেনেও পরোয়া করতেন না। কমেডিয়ান সুশীল চক্রবর্তীর ঘটনাটাই তেমন। তখন সুশীল তরুণ কমেডিয়ান। নবদ্বীপ হালদারের কমিক স্কেচের অনুকরণে কলকাতায় বিভিন্ন ফাংশনে বেশ নাম করেছেন। জনপ্রিয় হওয়াতে তাঁর ইচ্ছে হল গ্রামাফোন কোম্পানি থেকে নিজের কমিক স্কেচ রেকর্ড করবেন। সেইমতো কোম্পানিতে গিয়ে তৎকালীন রেকর্ডিং কর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আশ্বাসবাণীও পেলেন। কিন্তু ওই আশ্বাসই সার। অনুরোধ করতে করতে জুতো খয়ে গেল, কিন্তু রেকর্ডিং আর হয় না। অবশেষে রহস্য উন্মোচন হল। আসলে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিক স্কেচ এত বিক্রি হচ্ছে যে কোম্পানি আর নতুন শিল্পীর রেকর্ডিংয়ে আগ্রহী নয়। তবে যোগাযোগ রাখলে ভবিষ্যতে কখনও না কখনও রেকর্ডিং হতে পারে এই আশ্বাসও পেলেন। কিন্তু তাতে কী আর স্বপ্নপূরণ হয়! সুশীল বেশ মুষড়েই পড়লেন। কী করবেন ভেবে উঠতে না পেরে একদিন সকাল সকাল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে উপস্থিত হলেন।
অত সকালে সুশীলকে দেখে ভানু অবাকই হলেন। বললেন, ‘‘কী খবর সুশীল। তোমার মুখখান অমন শুকনা দ্যাখায় ক্যান?’’ সুশীলবাবু বললেন,‘‘আর বলবেন না ভানুদা। আমার কপালটাই খারাপ। গ্রামাফোন কোম্পানি থেকে বোধহয় আমার আর রেকর্ড করা হল না।’’ ভানু বললেন, ‘‘ক্যান? তুমি তো কইছিলা খুব শিগগির তোমার রেকর্ড হইব।’’ সুশীলবাবু বললেন, ‘‘ওঁরা তো তাই বলেছিলেন। এখন বলছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এত জনপ্রিয় শিল্পী থাকতে নতুন শিল্পীর রেকর্ড করতে যাব কোন দুঃখে। যোগাযোগ রাখবেন, পরে দেখা যাবে।’’ ভানু বললেন, ‘‘হেই কথা কইছে? একবার টেলিফোনের ডায়ালটা ঘুরা তো?’’ ফোন ধরেই গ্রামাফোন কর্তাকে ভানু বলেন, ‘‘শোনেন, আমি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কইতাছি। এবার পুজোয় আপনাগো ওখান থিকা আমি রেকর্ড করুম না। আপনারা জুনিয়র আর্টিস্টদের লগে দুর্ব্যবহার করেন।’’ সেই কর্তা এরপর ভানুকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ভানু অনড়। বলেন, ‘‘রাগের কথা নয়। কিন্তু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ড অ্যাকসেপ্টেড হইতাছে বইল্যা নতুন আর্টিস্টের প্রয়োজন নাই, হেইডা কেমন কথা? ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর দেশ থিক্যা কমেডি উইঠ্যা যাইব নাকি? আমার শর্ত যদি আপনারা মানেন, তবেই পূজায় রেকর্ড করুম। না হলে গুডবাই।’’ সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা করেন, ‘‘ব্যাপারটা কী ভালো হল ভানুদা? এর ফলে গ্রামাফোন কোম্পানির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খারাপ হলে তো ক্ষতি আপনারই।’’ ভানু হেসে বলেন, ‘‘আমার ক্ষতি করনের ক্ষ্যামতা মাইনষের নাই। আছে একমাত্র ঈশ্বরের।’’ শেষপর্যন্ত ভানুর হুমকিতেই কাজ হয়েছিল। সেই প্রথম সুশীল চক্রবর্তীর রেকর্ড প্রকাশিত হয়।
ঠোঁট ফাঁক হলেই ভানুর যেন যুক্তি মজুত থাকত। একবার দূরদর্শন দপ্তরে আড্ডা চলছে। একজন এসে বলল, ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ আর একবার করলে কেমন হয়। তখন অন্য একজন বলল, ‘‘ভানুদা, এরকম বস্তাপচা কাজ এখন আর চলে?’’ ভানু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,‘‘বস্তাটা পইচ্যা গ্যাসে। ভিতরের সোনাটা তো আর নষ্ট হয় নাই।’’ এরকমই আর একটি ঘটনা। জাতীয় নাট্যশালা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। শম্ভু মিত্র হঠাৎ ভানুকে বললেন, ‘‘আপনি এ ব্যাপারে আবার নাক গলাচ্ছেন কেন?’’ সটান উত্তর এল, ‘‘আমি নাক গলাইতে যামু ক্যান? আপনার নাকের যা অবস্থা, আপনে চেষ্টা করনের আগেই তা গইল্যা যাইবে গিয়া।’’
বাড়িতে কিছু না করলে কী হবে, বাইরে ম্যানেজ করতে ওস্তাদ ছিলেন। এলাহাবাদে ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’র আউটডোর শ্যুটিং। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন শুনে লোকেশনে হামলে পড়েছেন প্রবাসী বাঙালিরা। তিনি তখন স্পটে নেই। যাত্রিক হোটেলে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এদিকে লোকের চাপ এত বাড়ছে যে কিছুতেই কাজ করতে পারছেন না পরিচালক দিলীপ রায়। কাজের দফারফা। শ্যুটিং প্রায় ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম। বিপদ বুঝে ভানুকে আনার জন্য গাড়ি পাঠানো হল হোটেলে। ভানু এসেই নিজস্ব ভঙ্গিতে পরিস্থিতির রাশ হাতে নিয়ে নিলেন। দূরে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘‘আমারে দ্যাখনের কী আছে কন তো! ইচ্ছা হইলে দ্যাখেন তবে জোড় হাত কইরা কইতাছি, গোলমাল কইরেন না।’’ দিব্যি কাজ হয়ে গেল। ওঁর ইমেজটাই ছিল এরকম। আর এই ইমেজের জন্যই বাড়ির লোকজনকে অনেকসময় অপ্রস্তুতে পড়তে হয়েছে। ওঁর মেয়েকে স্কুলে বন্ধুরা খালি জিজ্ঞাসা করত, ‘‘হ্যাঁ রে, তোর বাবা সব সময় খুব হাসায়, তাই না?’’ মেয়ে এসে বাবাকে সেই কথা বলেন। শুনে ভানু বাসবীকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘‘আজ তরে যে কইসে তার বাবা কী করে?’’ মেয়ে বলেন, ‘‘সার্জেন। মানে ডাক্তার।’’ শুনে ভানুর জবাব, ‘‘অ, তাইলে ওরে কইবি, শোন তর বাপ কি তরে দ্যাখলেই ছুরি-কাঁচি লইয়া প্যাট কাটতে আসে?’’
শিবরাম চক্রবর্তীর সাথে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়েরও একটি মিষ্টি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ছিয়াত্তর-সাতাত্তর সাল নাগাদ একদিন সকালে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গাড়ীতে দুজন সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় একটি মিষ্টির দোকান থেকে বড় বড় জলভরা সন্দেশ কিনে গাড়ী এসে থামল মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের একটি পুরনো মেসবাড়ির সামনে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ঘরের সামনে পৌঁছতেই ভানুবাবু তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আগে দেখ তিনি ঠিক জায়গায় আছেন কিনা। সঙ্গী আদেশমত ঘরে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এসে জানালেন, হ্যাঁ, ঠিক জায়গায়ই আছেন। ভানু তাঁর দুই সঙ্গীকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। প্রথম সঙ্গী ঘরে বসে থাকা বৃদ্ধকে বললেন, ‘‘এই দেখুন, ভানুদা এসেছেন।’’ বৃদ্ধর চোখে মুখে শিশুর সরলতা। একটা চার বাই পাঁচ কিংবা তার থেকেও ছোট চট পাতা চৌকিতে সেই বৃদ্ধর চৌকিদারি। সেই সিংহাসন থেকেই রাজাধিরাজ একবার তাকিয়ে প্রায় নিমেষের মধ্যে বুকে টেনে নিলেন ভানু বাবুকে। ভানু বাবুও আশ মিটিয়ে জাপটে ধরলেন আরেক ‘রসরাজ শিব্রাম চকরবর্তি’কে। শিবরাম বাবুর প্রাণখোলা হো-হো হাসি, ভানু বাবুর চোখ চিক্ চিক্ হা-হা হাসির যুগলবন্দীতে ১৩৪ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের পুরনো মেসবাড়ীটা হঠাৎ যেন জলসাঘরে পরিণত হল। দুই পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ যেন একে অপরের সারল্যে নিজেদের জীবনের অক্সিজেন রিফিল করে নিচ্ছেন। শিবরাম বাবু জড়িয়ে ধরে বলে চলেছেন – ‘‘ফার্স্টক্লাস। কতদিন-কতদিন ভেবেছি একবার দেখা করবই। দেখা কি হবে না কোনোদিন!’’ ভানুবাবু বলে চলেছেন – ‘‘এতোদিনে মনের-প্রাণের সাধ মিটল। ইচ্ছেটা পূর্ণ হল।’’ সময় যেন থমকে গেছে, রসরাজ-যুগল একে-অপরকে জড়িয়ে ধরে মজে আছেন আপন খেয়ালে। একটু পরেই সবাইকে বসতে বললেন শিবরাম বাবু। ভানু বাবুর সাথে ওনার কথাবার্তা চলতে থাকে। ওদিকে একটা কলাই-এর থালায় ভাত, কিছু তরকারি আর বাটি থেকে গড়িয়ে পড়া ছোট্ট পোনা মাছের ঝোল দিয়ে গেলেন মেসের কর্মচারী। শিবরাম বাবুর ওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ভানু বাবু বুঝতে পারলেন যে এখন শিবরাম বাবুর খাবার সময়, তিনি চলে যাবার জন্য অনুমতি চাইলেন। শিবরাম বাবু বললেন, ‘‘যাবে? বেশ। আবার এসো কিন্তু।’’ তাঁরা উঠে পড়েছেন, এমন সময় ইশারায় ভানু বাবু তাঁর সঙ্গীকে সন্দেশের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সন্দেশ হাজির হল শিবরাম বাবুর সামনে। চোখ জ্বলে ওঠে তাঁর, ‘‘সন্দেশ এনেছ? বাঃ ফার্স্টক্লাস!’’ বলতে বলতেই দুটো বড় বড় জলভরা সন্দেশ তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন তিনি। ভাত পড়ে রইল। ভানুবাবু একটু দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে তাঁর সঙ্গীর কানে কানে চাপা গলায় বললেন, ‘‘খাইসে, ডায়াবিটিস্ আছে নাকি! ভাতের সঙ্গেই খাবে নাকি? বয়স হয়েছে, এতোটা …’’ শিশু ভোলানাথের কান সজাগ – ‘‘কিছু কি বললে?’’ ভানু বাবু কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন – ‘‘এই না, বলছি, আর একটু আগে আসলেই ভাল হতো আর কি। আপনি খেয়ে নিন, আমরা আসি তবে।’’ শিবরাম বাবুর এক হাতে সন্দেশ। হঠাৎ ভানু বাবুর এক সঙ্গীর সাদা জামায় সবুজ-কালোর কলকা করা হাতা ধরে তিনি বলতে লাগলেন – ‘‘বাঃ ভারী সুন্দর জামা পরেছ তো!’’।আরও একবার জামাটায় হাত বুলিয়ে বললেন, ‘‘বেশ বেশ। ভাল লেগেছে তোমায়, আবার এসো।’’ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভানু বাবু তাঁর সঙ্গীদের বললেন, ‘‘ছিটটা খুব পছন্দ হয়েছে ওনার। আবার যখন আসব তখন এইরকম একটা ছিট – না, পাওয়া হয়ত যাবে না। তবে এই ধরণের কলকা করা বেড কভার নিয়ে আসব।’’ সিঁড়ি থেকে নেমে এসে সবাই নিশ্চুপ। গাড়ীতে উঠে দরজা বন্ধ করে ভানুবাবু নিস্তব্ধতা ভাঙলেন – ‘‘সবই ঠিক হল, একটুখানি মিসটেক …’’ সত্যিই একটা ‘মিসটেক’ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তাঁরা ক্যামেরাটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। নিয়ে গেলে এমন দুই রসরাজের একত্রে ছবিটা বাঙালি সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকত। বিশেষ করে আজকের এই যন্ত্রণাময় যান্ত্রিক জীবনে এই ছবি হয়ত ক্ষণিকের জন্য সব ভুলিয়ে নিয়ে যেত সেই সময়ে যখন বাঙালি হাসত এবং হাসাত। সেই ছবির ক্যাপশন হয়ত হতেই পারত – ‘শিবরাম বাবু, রাবড়িচূর্ণ খামু!’
অভিনেতা, গায়ককে নানারকম সাহায্য করলেও ভানু নিজের বাড়ির লোকের জন্য সাহায্য চাইতে লজ্জা পেতেন। যেমন ‘নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে’ ও ‘কাঞ্চনমূল্য’ ছবিতে ভানুর স্ত্রী নীলিমাদেবীর দু’তিনটে গান ছিল। ভানুপুত্র গৌতম বলছিলেন, ‘তবু মা’র নাম ছিল না। না টাইটেলে, না বুকলেটে। অথচ বাবার চেয়ে আগে নাম করেছিলেন মা। স্বাধীনতার পর গভর্নর হাউসে গাইবার জন্য মা আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। বাবা এসকর্ট হিসেবে মা’র সঙ্গে গিয়েছিলেন। ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ ছবিতে অমর পালের গানটির সুর দিয়েছিলেন মা। কিন্তু টাইটেলে মা’র নাম ছিল না। ‘কাঞ্চনমূল্য’ ছবিতে মেন রোল আমি করেছিলাম। কিন্তু ‘ইন্দিরা’ হলে আমার নাম বা ছবি ছিল না। তাই দেখে বসুশ্রীর জোজো কাকা (সুবোধ মুখোপাধ্যায়) বাবাকে বলেছিল ‘ভানুদা, এটা তোর খুব অন্যায়। অন্তত গৌতমের মুড়োর একটা ছবি দিতে পারতি।’ এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয় মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কথায়। তাঁর ভাষ্যে, ‘‘আমি যখন রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী ছিলাম, তখন সিনেমা লাইনের বহু লোক আমার কাছ থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি অনেকবার আমার কাছে এসেছেন। অনেক সুযোগ-সুবিধাও আদায় করে নিয়েছেন। কিন্তু তার একটাও নিজের জন্য নয়। এই জন্যই ভানুবাবুকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। জেনুইন মানুষ। প্রতিবার আমার জন্মদিনে প্রথম ওঁরই ফোন পেতাম।’’ ‘নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে’ ছবিতে একটা কাণ্ড হয়েছিল। ছবির সুরকার ছিলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী। গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কিন্তু নির্মলেন্দুবাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জানা গেল, ‘গঙ্গা’ ছবির গান শিখিয়ে বেড়াচ্ছেন নির্মলেন্দু। সেখানেও এক অবস্থা। সলিল চৌধুরী সুর করে হাজিরা দিতে না পারায় ভার পড়েছে নির্মলেন্দুর উপর। শেষে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গান শিখলেন নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। ‘‘মা অবশ্য ছোট থেকেই গানের চর্চায়। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রী। অল ইন্ডিয়া রেডিওর গায়িকা, তবু হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তো!’’ – জানিয়েছিলেন গৌতম।
নিছক কৌতুকাভিনেতা নন, একজন পূর্ণাঙ্গ অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয় করেছেন প্রায় ৩০০ ছবিতে। আর প্রায় সব ছবিতেই তাঁকে তৈরি করতে হয়েছে কৌতুক। সংলাপ থেকে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে গড়ে নিয়েছিলেন কমেডির নিজস্ব ভুবন। সাদাকালোর সেই পর্দায় যতবারই তাঁকে দেখা গিয়েছে, ততবারই ম্যাজিক দেখেছেন দর্শক। কখনও শার্ট-প্যান্ট, আবার কখনও কেতাদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নিজস্ব কায়দায় দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন। ‘ভানু পেল লটারি’, ‘নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে’ ছবিগুলো যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, অভিনয়ের জোরে তিনি কাঁদাতেও পারেন। অভিনয়শক্তিতে ভর করে এমন কিছু তিনি করেছেন, বহু শিল্পী শত চেষ্টাতেও যা পারেননি। ভানুর লিপে প্লে ব্যাক করেছিলেন শ্যামল মিত্র ‘পুতুল নেবে গো পুতুল’ গানটিতে। ছবির নাম ‘ভানু পেল লটারি’। এই ছবির মতো ‘ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট’ ছবিতেও তাঁর নাম ব্যবহার করে ছবির নামকরণ হয়েছে। এই দৃষ্টান্তও এক জহর ছাড়া আর কোথায়! ভানুর লিপে অসাধারণ গান আরও রয়েছে। ‘স্বর্গ মর্ত্য’ ছবিতে ‘এই মধু রাতে বধূ তুমি কাছে ডাকো’ গেয়েছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। ‘পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট’ ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন ‘ক রয়েছেন কলকাতায়’, ‘তোমাদের নতুন কুঁড়ির’, ‘এই বেশ ভালো লাল সাদা কালো’। কিশোরকুমার গেয়েছিলেন ‘সাবরমতী’ ছবিতে ‘তাক ধিন ধিন তা’। এই গানটির সিংহভাগ অবশ্য ছিল উত্তমকুমারের লিপে। ‘আশিতে আসিও না’ ছবিতে মান্না দে গেয়েছেন ‘তুমি আকাশ এখন যদি হতে’, ‘ও ভোলা মন’।
১৯৭৯ থেকেই ভানুর শরীর ভাঙতে শুরু করে। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেই ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ করেন। এনলার্জড হার্ট ছিল। তিন-চারবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ায় শেষ দিকে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। তারমধ্যে রেনাল ফেলিওর। চলে যাওয়ার এক মাস আগে ভর্তি হলেন নার্সিংহোমে। ডাক্তার তিন মাস রেস্ট নিতে বললেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছাড়া পেয়েই একবার উত্তরবঙ্গে গিয়ে যাত্রা করে এলেন। ফিরে আসার পর একদিন সকাল থেকে হঠাৎ শুরু হল বমি। ১৯৮৩ সালের ৪ঠা মার্চ। ভর্তি করা হল ‘উডল্যান্ডসে’। যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে শুয়ে মেয়ে বাসবীকে জিজ্ঞেস করেন, ‘‘উডল্যান্ডসে একদিনের ভাড়া কত রে?’’ গৌতম জানিয়েছিলেন, ‘‘দোতলায় আইসিইউতে ছিল বাবা। ভাই তার সাতদিন আগেই দেশে ফিরেছে ন’বছর পর। ভগ্নীপতির সঙ্গে ও-ই রাত জাগতে হাসপাতালে ছিল। সে রাত আর গড়াল না।’’ বারোটা নাগাদ খবর এল ভানু আর নেই। আজীবন আপামর বাঙালিকে হাসিয়ে নিজের শেষযাত্রায় সকলকে কাঁদিয়ে শেষবারের মতো বাড়ির কর্তা ভিটে ছাড়লেন। তাঁর শেষ ছবি ‘শোরগোল’ মুক্তি পেয়েছিল মৃত্যুর এক বছর পরে, ১৯৮৪ সালে।
আড্ডায় বসে ভানু প্রায়ই বলতেন, ‘‘আমার দশা ক্যামন জানেন। মা মারা গ্যাসে। শ্মশানে গেসি। চোখে জল। একটা লোক কাছে আইয়া কইল, আরে ভানুদা না! কী হইসে? কোনওক্রমে কইলাম, ভাই মা মারা গ্যাসেন। শুইন্যা হালায় হাসতে হাসতে চইল্যা যাইতে যাইতে কইল, দ্যাখ ভানুরে কাঁদলে কেমন লাগে দ্যাখ। বুঝেন একবার। হালায় নিজে যখন শ্মশানে যামু লোকে হয়তো কইবে, ওই দ্যাখ, ভানুর মাথাটা কেমন নড়তাসে।’’ নিজেকে কেবল পূর্ববঙ্গীয় নয়, খাস ঢাকার বলেই গর্ব করে পরিচয় দিতেন – ‘‘আমি বাঙাল’’। হীনমন্যতা নয়, এই পরিচয় দানে ছিল প্রবল অহংবোধ। অথচ একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এপার বাংলার অনেক গুণী শিল্পী সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে নানাসময় ঢাকা গিয়েছিলেন। কিন্তু ভানুকে কেউ ঢাকা নিয়ে যাননি। অবশ্য, পরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গিয়ে তিনি বিটিভিতে একটি অনুষ্ঠানও করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠান শেষে আক্ষেপও করেছিলেন, ‘‘আপনাদের ডাকের অপেক্ষায় বহুদিন ছিলাম। আপনারা কেউ আমাকে ডাকেননি।’’ এ লজ্জা কিন্তু সমগ্র বাঙালির। দুঃখের বিষয় হল, মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসা ছাড়া কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানই তাঁর ভাগ্যে জোটেনি কোনওদিন। কী আর করা যাবে! বাংলা চলচ্চিত্রের অগণিত দর্শকের অন্তরেই বেঁচে থাকবেন তিনি। স্বমহিমায় চিরকাল।
(তথ্যসূত্র:
১- হাসি-রাজ ভানু-জহর, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, পাণ্ডুলিপি (২০১১)।
২- ভানু সমগ্র, পত্রভারতী (২০১৭)।
৩- আজও তারা জ্বলে, বর্তমান পত্রিকা।)
মতামত লেখকের ব্যক্তিগত