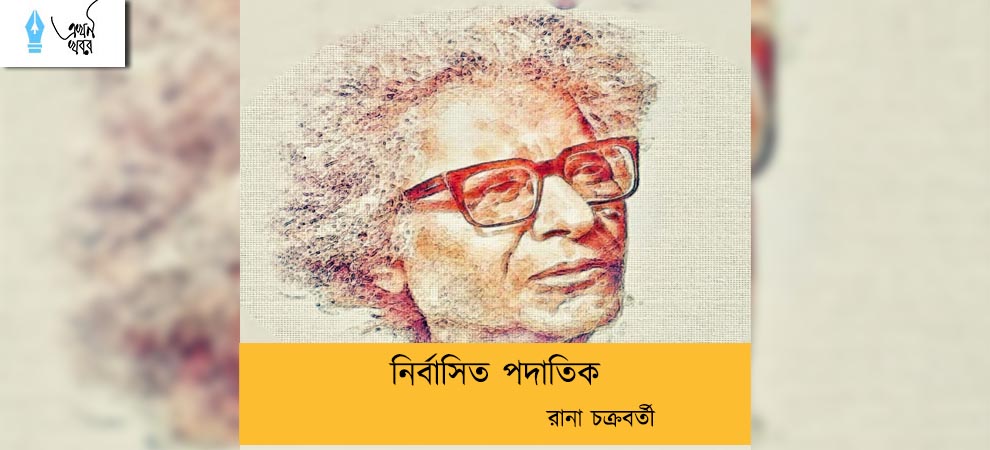লেখায় ডুবে আছেন। বাড়ির লোকজন মনে করলেন, বাইরের আওয়াজে হয়তো অসুবিধা হচ্ছে। বন্ধ করতে যাবেন দরজা-জানলা। কিন্তু তিনি নারাজ। রাস্তায় মানুষ যাতায়াত করছে। মানুষকে দেখতে, মানুষের সঙ্গে কথা বলতে যে অসম্ভব ভালবাসতেন! তাই জানলা বন্ধ করা যাবে না! জানলার পাশে বসেই লিখতেন।
৫বি, শরৎ ব্যানার্জি রোডের ছোট ঘরের জানলাগুলো এখন সব সময় বন্ধই থাকে। খোলা হয় না। ঘরের এক দিকে বইয়ের র্যাকে সার দিয়ে বই। পুরনো, ধুলোপড়া। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বড় নাতনি শ্রীমতী পৃথা রায় সংবাদমাধ্যমে বলছিলেন, ‘‘দাদু তো চার দিকে বই ছড়িয়ে বসতেন। ঘরে বসার জায়গাটুকুও থাকত না।’’ পৃথার ডাকনাম মিউ। তাঁর জন্যই সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটানো’। পৃথা ওরফে মিউ আরও জানিয়েছিলেন, ‘‘দাদুর শতবর্ষের জন্য অন্য অনেক কিছুই পাল্টেছি বাড়ির। কিন্তু এই র্যাক থেকেই উনি বই নামিয়ে নিতেন খুশি মতো। তাই আমরা এই জায়গাটা পাল্টাইনি।’’
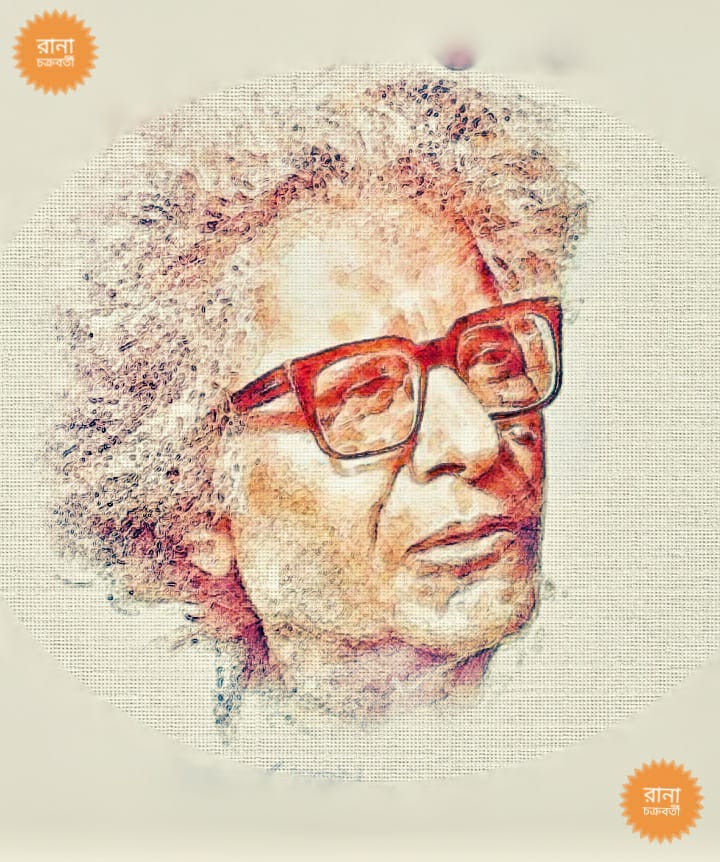
ফলে ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে শততম জন্মদিনের সামনে দাঁড়িয়েও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার ঘরের চেহারা মোটামুটি একই ছিল আর আজও একই আছে। কবি, কবিপত্নীর বিভিন্ন সময়ের ছবি দেওয়াল জুড়ে, তাঁর সংগৃহীত বই, সেই সঙ্গে সারাটা ঘরের আটপৌরে চেহারা— সব একই রয়েছে।
কবির বড় মেয়ে কৃষ্ণকলি (পুপে) রায় সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, হাঁটতে খুব পছন্দ করতেন তিনি। হাঁটতে-হাঁটতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আড্ডা মারতে, কথা বলাটাও ভীষণ পছন্দ ছিল তাঁর। আবার হয়তো বাজারে গিয়েছেন। খেয়াল করতেন, কে ফাঁকা বসে রয়েছেন। তাঁর কাছ থেকেই সব জিনিস কিনে নিয়ে আসতেন। কৃষ্ণকলির কথায়, ‘‘নিয়মিত পচা মাছ আনতেন। তা নিয়ে মা-র সঙ্গে ঝামেলাও হত। বাবা শুধু বলতেন, ওঁর (যাঁর কাছ থেকে মাছ কিনেছেন) বউনি হচ্ছিল না। তাই এনেছি। না হলে ওঁদের চলবে কী করে।’’ মানুষের সঙ্গে এই সহজ সম্পর্ক ঘুরে-ফিরে এসেছে তাঁর লেখায়, কবিতায়। সক্রিয় বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পার্টি করেছেন দীর্ঘ বছর। জেলও খেটেছেন।
কবি জয় গোস্বামী তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়েছিলেন, ‘‘সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের কথাকে নিজের কবিতায় তুলে এনেছিলেন। সাধারণ মানুষের ভাষাই তাঁর হাতে হয়ে উঠেছিল কবিতা। শুধু কবিতাই নয়। অসাধারণ গদ্য লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন!’’
যদিও নিজের কবিতা লেখা নিয়ে তাঁর রসিকতার অন্ত ছিল না। কখনও তিনি নিজের কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন, ‘আমার মতো লোকেদের মা-সরস্বতী দিনের পর দিন নাকে দড়ি দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে মারেন।’ আবার লিখেছেন কোথাও, ‘আমার লেখায় আমি দেখেছি, যে জায়গাটা লোকে খুব প্রশংসা করেছে, এটা দারুণ লিখেছো, সে সব জায়গা, আমি দেখেছি, আসলে আমার নয়। অন্যের কথা। সাধারণ মানুষের কথা। আমি মেরে দিয়েছি। আত্মসাৎ করেছি। কেউ ভিক্ষে করে খায়। তুমি কী করো? না, টুকিয়ে, টুকিয়ে খাই।’ তবে দিনের শেষে নিজের কবিতা লেখার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি চাই কবিতা দিয়ে মানুষের হাতগুলোকে এমন ভাবে কাজে লাগাতে যাতে দুনিয়াটা মনের মতো করে আমরা বদলে নিতে পারি।’
আর এখন যখন ধর্ম ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে, ধর্মের শাখাপ্রশাখায় যেখানে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে চতুর্দিক, সেখানে সেই ১৯৮৫ সালে এক জায়গায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ‘এ দেশের মুসলমানের সঙ্গে আমার পূর্বপুরুষের তো রক্তেরই সম্বন্ধ।’ লিখেছিলেন, ‘…মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে শাস্ত্রের গণ্ডি টেনে ধর্মকে যারা খাটো করতে চাইছে, আসলে তারাই যে ঘরের শত্রু বিভীষণ— এটা আজ বোঝবার সময় এসেছে।’ বিশ্বাস করতেন, ইংরেজি আগ্রাসনেও ‘মুখে মুখে বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে।’ বরাবর বিশ্বাস করে এসেছেন— ‘আমি যত দূরেই যাই।/ আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে/ নিকোনো উঠোনে/ সারি সারি/ লক্ষ্মীর পা…’।
তাঁর অনুজ কবিরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে স্বীকার করেছেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমৃত্যু লেখার আলো নিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকেছেন। তার পরে সেই লেখার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন চার দিকে। আর সেই আলোয় সরে গিয়েছে চাপ-চাপ অন্ধকার। কিন্তু তিনি, সেই সমস্ত আলোর মধ্যে দাঁড়িয়েও নির্মোহ ভাবে শুধু বলেছেন,— ‘আমাকে কেউ কবি বলুক/ আমি চাই না।/ কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে/ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত/ যেন আমি হেঁটে যাই।’
বাংলা ভাষায় সাহিত্য ও কাব্য রচনা করলেই যে সবার ভাষার প্রতি দায়দায়িত্ব থাকে, এ কথা মনে করার কারণ নেই। তবে কারও কারও থাকে। ভাষার প্রবাহ কী ভাবে অনেক বেশি মানুষের ব্যবহারে প্রবল হয়ে ওঠে, তা নিয়ে কোনও কোনও বড় লেখক ও কবি মাথা ঘামান, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঘামাতেন। তাঁর শতবর্ষে তাঁর কবিতা, গদ্য, রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে অনেক কথা হবে সন্দেহ নেই, হওয়া উচিতও। তবে বাংলা ভাষাকে আমজনতার ব্যবহারে কী ভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা ও অবদানকে আলাদা করে চিহ্নিত করা চাই। কোনও ভাষা কেবল কাব্য-সাহিত্যের আবেগে বাঁচে না, রকমারি ব্যবহারে বাঁচে। কোনও বড় সাহিত্যিক বা কবি যদি ভাষার সেই রকমারি ব্যবহারের কাজে হাত লাগান, তা হলে তো সোনায় সোহাগা।
খোদ বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত বাংলা ভাষা যত বেশি সংখ্যক মানুষ ব্যবহার করেন তত ভাল। অনেকে হয়তো খেয়ালই করেন না, ‘পাঠ্য পুস্তক/ সহজ রচনাশিক্ষা’ নামে বঙ্কিম একটি বই লিখেছিলেন। সে বইতে দ্বিতীয় পাঠে বঙ্কিমের মন্তব্য, ‘‘তোমার যাহা বলিবার প্রয়োজন, রচনায় তাহা যদি প্রকাশ করিতে না পারিলে, তবে রচনা বৃথা হইল।’ মনের ভাব স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার জন্য ‘যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে। তাহা শুনিতে ভাল নয় কি বিদেশী কথা, এরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিও না।’’ এই বঙ্কিমী দাওয়াই খুব উদার। বাংলা শব্দভান্ডারে নানা জাতের শব্দকে বঙ্কিম ঠাঁই দিতে চান। আর তার পরেই সেই মোক্ষম কথাটি লেখেন, ‘‘তুমি যাহা লিখিবে, লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে। যাহা লিখিলে, লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা।’’ এই লোক আমজনতা। পণ্ডিত ও কৃতবিদ্যদের বইঘরে ভাষা আটকে থাকলে বাঁচে না, তাকে সাধারণের উঠোনে নামতে হয়।
বঙ্কিমের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনের ও সময়ের মিল নেই। তবে ভাষা ভাবনার মিল খানিকটা আছে। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সুভাষের অক্ষরে অক্ষরে। জ্ঞানে প্রবৃদ্ধদের জন্য নয়, পণ্ডিতদের জন্যও নয়, মূলত কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা এ বইতে ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, ‘‘জানাবার এই উপায়টার নামই ভাষা।’’ সুভাষ তাঁর জীবনের শেষের দিকে হাসপাতালে শুয়ে দুটো নোটবইতে টুকিটাকি লিখতেন। সেই টুকিটাকি লেখা ও আরও কিছু কবিতা নিয়ে প্রয়াণের পর প্রকাশিত হয়েছিল ‘নতুন কবিতার বই’। তাতে নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন। নিজের নাম দিয়েছিলেন সুভাষ মূর্খজী। সুভাষ মূর্খজী নিজের সঙ্গে নিজে কথা চালান। চমৎকার সে সওয়াল জবাব। ‘‘আপনি কবি? কভি নেহি।/ কী আপনি? পদকার।’’ কবির মধ্যে অহমিকা থাকে, সাধারণের থেকে যেন কবি আলাদা। আর পদকার জানেন মানুষকে জানানোই তাঁর কাজ। ‘পেশা? পদসেবা।’ সাধারণের চলনে-বলনে, কাজে-কর্মে যে ভাব আর কথা, তাকেই অন্যের কাছে তুলে ধরেন পদকার। সেই পদকার অপরকে জানাতে চান, সেই পদকার বঙ্কিমের মতোই ভাবেন, ‘‘যাহা লিখিলে, লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা।’’ কবি সুভাষ অক্ষরে অক্ষরে বইতে ছেলে-মেয়েদের ছন্দ বোঝাতে গিয়ে লেখেন, ‘‘মানুষের ছন্দে শুধু জীবনের রসই থাকে না, থাকে সমাজ-বাঁধা রস। একার ছন্দ নয়, অনেকের ছন্দ।’’ এই অনেকের ছন্দ ধরা চাই, ভাষাটাকে অনেকের কাজে লাগানো চাই।
লাগাতে গেলে সবার আগে ছোট ছেলে-মেয়েদের ভাষার কান তৈরি করতে হবে। তা তৈরি করার জন্য সুভাষ লিখেছিলেন প্রাইমার ‘শুনি দেখি পড়ি লিখি’। জীবনের শেষ কয়েকটা বছর এই প্রাইমার লেখায় মন দিয়েছিলেন। এই প্রাইমারে তিনি জোর দিয়েছিলেন চলিত আটপৌরে শব্দের ওপর। পড়ুয়াদের চেনা পরিচয়ের সীমা বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালি তো অনেক রকম। জল, পানি, নমস্কার, আদাব, মা, আম্মা— সবই থাকা চাই বাঙালির মাতৃভাষায়। যার যা সংস্কৃতি, সবার মিলমিশেই বাংলা ভাষা। বোশেখ, জষ্টি যেমন জানা চাই, তেমনই জানা চাই মহরম, শফর। যুক্তাক্ষর শেখাতে গিয়ে বাক্স, ট্যাক্সি, বক্সিং, ক্লাস, ক্লাব শব্দগুলি ব্যবহার করেন। বিদেশি শব্দগুলো তো এখন বাংলাই, তা হলে বাদ দেবেন কেন! দৃশ্য হিসেবে গ্রাম যেমন আছে সে প্রাইমারে, তেমনই আছে শহর। ‘‘হাঁটু গেড়ে/ দুটো ঠ্যাং/ ডোবার পাড়ে/ কোলাব্যাং’’— এ ছবি গ্রামের, আধা শহরেরও হতে পারে। ‘‘দিদির ভারি/ বিবিয়ানি/ ফিশচপ আর/ বিরিয়ানি’’ বিবিয়ানি করা বিরিয়ানি খাওয়া দিদিটি শহুরে বলেই মনে হয়। ছেলেবেলায় এ প্রাইমার পড়লে ভাষা আর সংস্কৃতির ছুঁইছুঁই বাই অনেকটাই কাটবে। ছেলে-মেয়েদের জন্য পাতাবাহার নামে একটি গদ্য-পদ্যের বই সংকলন করেছিলেন সুভাষ, সে বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে, অক্ষরে অক্ষরে বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরের বছর। সে বই শুরু হয়েছিল সুকুমার রায়ের অপ্রকাশিত একটি পদ্যে— ‘কলিকাতা কোথা রে!’ গিরিধি আরামপুরীতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে অলস দিন কাটছে। এমন সময় চিঠি এল কলকাতায় চায়ের ভোজ। কিন্তু কলিকাতা সে আবার কোথা? রেলের ‘টাইমটেবিল’ পটনা, পুরী, গয়া, গোমো, হাওড়ার নাম লেখে। কলকাতার নাম লেখে না। কলকাতা নামের স্টেশন তো হালে হয়েছে। সুকুমারের সময় সে কোথায়? সুতরাং কলিকাতা কাহাঁ বলে মাথা চুলকানো ছাড়া গতি নেই। সুভাষের মস্ত গুণ তিনি কখনও কলকাতার হয়ে ওঠেন না। তাঁর লেখাপত্তরে কলকাতার ছাপ-ছবি আছে বটে, কিন্তু তিনি বাংলা ও বাঙালিকে কলকাতার বাইরে অনেকটা বড় পরিসরে দেখতে চান। পদাতিক কি আর তিনি এমনি এমনি! পাতাবাহার বইয়ের গোড়ায় সুকুমারি পদ্যে কলকাতাকে নিয়ে রঙ্গ করতে তাঁর দিব্য লাগে। বন্ধ হয়ে যাওয়া ‘সন্দেশ’ রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে ১৯৬১ সালে যে আবার নতুন করে প্রকাশিত হল, তার পিছনেও সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগ। ভাষাটাকে ছেলেমেয়েদের কাছের করা চাই— সত্যজিৎ সুভাষের কথা শোনেন।
শুধু ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় বাংলায় কান তৈরি করবে, এটুকুর চেয়ে বেশি কিছু চাই। বাংলা ভাষাকে জ্ঞানের ভাষা কাজের ভাষা না করলে চলবে কেন? বাংলা ভাষাকে যে চমৎকার সংহত জ্ঞানের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা চলে, সুভাষ ইতিউতি তার নানা নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাস বইটির চমৎকার সংক্ষিপ্ত একটি রূপ নির্মাণ করেছিলেন সুভাষ। বিশদকে সংক্ষেপে সংহত করার মন্ত্র যে ভাষা জানে, সে ভাষা বেঁচে থাকে। জ্যোতি ভট্টাচার্য লিখেছিলেন শ্রমিকের দর্শন, মেহনতি মানুষদের সহজে মার্ক্সের দর্শন বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছিল সে বই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘হাংরাস’ উপন্যাসে আটপৌরে ভাষায় এসেছিল মার্ক্সের ভাবনা— ‘‘কলওয়ালা কিনছে খাটুনিওয়ালার খাটবার ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাকে সে ব্যবহার করছে লোকটাকে কাজে লাগিয়ে।’’ কাজের বাংলা নামে চটি একখানি বই লিখেছিলেন তিনি। বাংলা ভাষার ব্যবহারিক দিক নিয়ে নানা কথাবার্তা ছিল তাতে।
এ সব আসলে একই উদ্দেশ্য থেকে লেখা। পদকার তিনি, বাংলা ভাষার পদকার। সেই পদকারের দায় অনেক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘শিক্ষার বিকিরণ’ প্রবন্ধে দুঃখ করে লিখেছিলেন, যে মন চিন্তা করে, বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগ সাধন করে সে মন বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় আসা-যাওয়া করে না। ‘‘গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলাসাহিত্যের পনেরো-আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়।’’ সুভাষ মুখোপাধ্যায় শক্তির আয়োজন করার জন্য বাংলা ভাষাকে নানা ভাবে ব্যবহার করেছিলেন। সে ব্যবহার যত পোক্ত হবে, ভাষার ভিত্তি ও সেই ভাষাকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কৃতির প্রত্যয় তত দৃঢ় হবে।
তিরিশ বছর আগে ভোপালের ‘ভারতভবন’। ভারতের শিল্প সাহিত্য নিয়ে গড়ে উঠেছে একটা ‘মাল্টি আর্টস কমপ্লেক্স’, এক অপূর্ব স্থাপত্য। বানিয়েছেন ভুবনবিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়া। সিঁড়ি নেমে গিয়েছে ভারতভবনের সিংহদুয়ার থেকে। নামতে নামতে একটা সমতল। বাঁ দিকে করমণ্ডলম, তার পর নাটকের রেপার্টরি, তার পর এ পাশে বাগর্থ, ভারতীয় সাহিত্যের বিশেষ করে ভারতীয় কবিতার দলিলঘর, জ্ঞান চর্চার উপাসনাগৃহ, তার পর একটা বিশাল আর্ট গ্যালারি— স্বামীনাথন থেকে গণেশ পাইন, তার পিছনে ভারতীয় সঙ্গীতের আকাশ। সারা ভারতের কবিরা সে দিন জড়ো হয়েছেন আরও অনেক সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা পুকুরপাড়ে। ভোপালের লোকেরা যাকে বলেন ‘বড়ে তালাও’। সেই পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পিছনে জল ও আকাশ। তাঁর সামনে ভারতের কুড়িটি ভাষার শতাধিক কবি এবং এশিয়া মহাদেশ থেকে আমন্ত্রিত কবিরা। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংহ এসে দাঁড়ালেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে ‘কবির সম্মান’ তুলে দেবেন। বাংলা কবিতার জন্য এ রকম একটা মুহূর্ত গত তিরিশ বছরে ভারতের আর কোথাও দ্বিতীয় বার তৈরি হয়নি। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার অনেক বড় পুরস্কার, কিন্তু সে দিন ‘কবির সম্মান’ উপলক্ষে যে আয়োজন হয়েছিল, তা ইতিহাসে এক বারই ঘটেছে।
কেন এক বার? তার পিছনে একটা গ্লোবাল রাজনীতি ছিল। সারা পৃথিবীর চোখ তখন ভোপালের গ্যাস ট্র্যাজেডির দিকে। হাজার হাজার গরিব মানুষ বিষক্রিয়ায় মারা গিয়েছেন। ব্রিটিশ কবি স্যর স্টিফেন স্পেন্ডারকে একঝাঁক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘যখন গরিব মানুষ মারা যাচ্ছেন, তখন আপনারা কবিতা নিয়ে মহোৎসব করছেন! টাকাটা তো গরিবের ঘরে যেতে পারত?’’
স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারে অংশ নেওয়া স্পেন্ডার তেতে উঠে উত্তর দিলেন, ‘‘এখনই তো সময় কবিতার! কী বললেন, টাকা? সংস্কৃতির জন্য সব সরকারের আলাদা ফান্ড থাকে। সেটা টোটাল বাজেটের ওয়ান পার্সেন্টও নয়। যাঁরা গ্যাস ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী, তাঁদের বলুন! ইউনিয়ন কার্বাইডকে টাকা দিতে বলুন! কবিদের বলছেন কেন? কবিরা আপনাদের সব সময়ের টার্গেট, তাই না?’’
সুভাষ মুখোপাধ্যায় মুখে একটা বাদাম দিতে দিতে অর্জুন সিংহের দেওয়া নৈশভোজে আস্তে আস্তে অনুজ কবি সুবোধ সরকারকে বলেছিলেন, ‘‘জানো তো, আমরা হলাম নরম মাটি। আঁচড়ানো সোজা।’’ তার অনেক আগেই শুরু হয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের বিষ-মেশানো তরজা। সুভাষের হাতে সম্মান তুলে দিচ্ছেন অর্জুন সিংহ, সেই ছবি ঘি ঢেলে দিল আগুনে। দ্বিতীয় একটা বাদাম মুখে দিতে দিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুবোধ সরকারকে বলেছিলেন, ‘‘তোমরা তালাওয়ের জলটা দেখেছ? কী সুন্দর, রাতের আঁধারেও চকচক করছিল।’’ এই হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি জানেন, কলকাতায় ওরা ছিঁড়ে খাচ্ছে তখন। কিন্তু কী সহজে তৃতীয় আর একটা বাদাম তুলে নিলেন ঠোঁটে। কবি সুবোধ সরকারের ভাষায়, “আমরা তখন গোল হয়ে বসে আছি সুভাষদাকে ঘিরে। আমরা মানে ভারতের একঝাঁক তরুণ কবি—কন্নড় ভাষার শিবপ্রকাশ, তামিলের রাজারাম, হিন্দি থেকে ধ্রুব শুক্ল, মালয়ালমের চুল্লিকাড়। একজন উঠে দাঁড়িয়ে আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘‘আপনিই ভারতের প্রথম ও শেষ পাবলো নেরুদা।’’ যে ভাবে নারকেল গাছ মাটিতে পড়ে, ঠিক সে ভাবেই সে মাটিতে পড়ে গেল। অনেকটা মদ খেয়ে ফেলেছিল বেচারা, তবু সুভাষদাকে চোখে দেখার পর সে আত্মহারা সে দিন! এই তরুণ কবির নাম আমি বলব না— সে এখন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর।”
একাধিক বার জেলে গিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। স্বাধীনতার পরে এ রকম সৌভাগ্য কোনও বাঙালি কবির কপালে আর জোটেনি। নকশাল আন্দোলনের সময়ে কিংবা ইমার্জেন্সির সময়ে কেউ জেল খেটেছেন। তবে তাঁরা কেউ সুভাষ মুখোপাধ্যায় নন। চিলির কবি নিকানর পাররা লিখেছিলেন, ‘জেল না খাটলে সে আবার কবি নাকি?’ পাররা কখনও জেলে যাননি। আর সে দেশেরই রাউল সুরিতা লিখেছিলেন, ‘জেলের দেওয়াল কবিতাকে শেষ করে দেয়।’ কী আশ্চর্য, সুরিতা পিনোশেতের অত্যাচার সহ্য করে জেলে গিয়েছিলেন। জেলে থাকাকালীন (যে সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ) সাধারণ দু’জন বন্দি বলেছিলেন, ‘আপনি আর লেখেন না কেন? আপনার লেখা পড়ে রাস্তায় নেমেছি, আপনার লেখা পড়েই তো জেলে এলাম।’ কোনও কবিরই এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি হতে পারে না।
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ‘টোটো কম্পানি’তে লিখছেন, ‘‘যখন জেলে গেলাম, মনে হল সেও এক ভ্রমণ… দড়িচালী থেকে ঘানিঘর ঘুরে ঘুরে দেখা। মানুষগুলো প্রত্যেকেই যেন রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের বই। পড়ে শেষ করা যায় না। মামলা থাকলে জাল দেওয়া গাড়িতে রাস্তা দেখতে দেখতে কোর্টে পৌঁছনো। ভ্রমণ বৈকি। রীতিমতো ভ্রমণ। তার ওপর আছে এক জেল থেকে অন্য জেলে যাওয়া। শুনলে অনেকে হিংসে করবে। জেলে থাকার সুবাদেই আমার জীবনে প্রথম এরোপ্লেন চড়া।’’ হাজতবাসকে এত সহজ করে নিতে পারে কেউ? যে সব তরুণ কবি আজকাল কথায় কথায় ডিপ্রেশনে চলে যান, তাঁরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জেলজীবন পড়ে দেখলে তাঁদের আর ঘুমের বড়ি খেতে হবে না।
শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে একটি অনুষ্ঠানের পর সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আশ্চর্য ভূমিকায় দেখেছিলেন কবি সুবোধ সরকার। টেবিলে টেবিলে অফুরন্ত খাবার। তিনি নিজে একটি খাবারও মুখে দিলেন না। অথচ ঘুরে ঘুরে রুমালে তুলে নিলেন মাছের চপ আর মাংসের টুকরো। সুবোধ সরকারের এক বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে খুব জোরে জোরে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন (জোরে, কেননা তিনি তখন বাঁ কানে প্রায় কিছুই শুনতে পেতেন না)। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আন্দাজেই উত্তর দিলেন, ‘‘ওরা বসে আছে না খেয়ে, আমি বাড়িতে গেলে ওরা একটু খেতে পাবে।’’ এই ওরা কারা? ওরা হল ধুলো আর বালি। তাঁর পোষ্য দুই বেড়ালের নাম।
রবীন্দ্রনাথের যেমন বোলপুর, তারাশঙ্করের যেমন লাভপুর, বিভূতিভূষণের বনগাঁ, সতীনাথের পূর্ণিয়া (সতীনাথ ভাদুড়ির সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দু’জায়গায় মিল — জেল খেটেছেন দু’বার এবং রাজনৈতিক মত পাল্টেছেন), জীবনানন্দের বরিশাল, হেমিংওয়ের হাভানা, কনরাডের মালয়দ্বীপ, গ্রাহাম গ্রিনের আফ্রিকা— তেমনই হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বজবজ। এই বজবজ থেকে তিনি একটার পর একটা কবিতা পেয়েছেন। বজবজ তাঁর জীবনে একটা বিরাট স্থান করে নিয়েছে। কত মানুষ তাঁর জীবনে এসেছে, মানুষের পিছনে পিছনে এসেছে কবিতা।
বজবজ ছিল তাঁর নিঃশ্বাস। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সাল অবধি তিনি ছিলেন চটকলের শ্রমিকদের সঙ্গে। এরাই ছিল তাঁর কবিতার আত্মা। লোথার লুৎসেকে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘‘আমি জেলখানায় কিছু লিখিনি। বরং আন্দোলন করেছি, রাজনীতি পড়েছি। কিন্তু লেখা আমি শুরু করলাম এর পর জেল থেকে বেরিয়ে— যখন চটকল শ্রমিকদের গ্রামে গিয়ে থাকলাম। শ্রমিক আন্দোলন করতে করতেই আমার চারপাশের জীবন আমাকে লেখার দিকে ঠেলে দিল।’’
কলকাতা ছিল তাঁর কবিতার ত্বক। রাজনীতি ছিল তাঁর কবিতার হাড়মাস। রাজনীতি তাঁকে যেমন দিয়েছিল, তেমনই তাঁকে নিয়েছিল। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে থেকেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় আকাশের কবিতা লিখতে পারতেন। মুখ থুবড়ে পড়তে তো হয়ই, কিন্তু ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ানোর নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়।
কবি সুবোধ সরকার তখন থাকতেন লেক গার্ডেন্সে। ফোন ছিল না। হঠাৎ হঠাৎ সন্ধেবেলায় গিয়ে দাঁড়াতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। সুভাষ তখন একটা ছোট টাইপরাইটারে একটা করে লাইন লিখতেন, তার পর সেটাকে টাইপরাইটার থেকে খুলে গোল্লা করে মেঝেতে ছুড়ে ফেলতেন। সারা ঘরে ছড়িয়ে থাকত, উড়ে বেড়াত গোলা পাকানো লাইন। বিড়াল গোলাগুলো নিয়ে খেলে বেড়াত। সে কথাও তাঁর কবিতায় আছে। শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায় (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী) মজা করে হাসতে হাসতে বলতেন— ‘‘এই দ্যাখো, তোমাদের সুভাষদা গড়াগড়ি খাচ্ছেন।’’ সুবোধ সরকার জানিয়েছেন, “বহু দিন কোনও কথা না বলে বসে থেকেছি। কথা প্রায় বলতেনই না। তাঁর উপর নেমে আসা খড়্গ আমি দেখতে পেতাম। তিনি নিজের মুখে কোনও দিন বলেননি।”
কবি সুবোধ সরকার তাঁর স্মৃতিচারণে আরও জানিয়েছিলেন, “নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে সে বার গিয়েছি। ওঁরা বললেন, ভারতবিখ্যাত এক জন বাঙালি কবিকে আমরা ডেকেছি, সঙ্গে এক জন নবীন কবি। সুভাষদার সঙ্গে আমাকে ডাকার কোনও কারণ ছিল না। কিংবা একটা কারণ ছিল বটে। সে সময়ে ‘দেশ’ পত্রিকায় আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, নাম ‘রূপম’। কবিতাটি ফোটোকপি করে হস্টেলের দরজায় দরজায় টাঙানো হয়েছিল। সেই গল্প ছাত্র আর মাস্টারমশাইদের মুখে শুনে মনে হল, এ জন্যই আমায় ডেকেছে।
দুপুরবেলা সুভাষদা কবিতা পড়তে শুরু করলেন। কী সব কবিতা! পাগল বাবর আলির চোখের মতো আকাশ (সালেমানের মা), মিছিলের মুখ, কুকুরের মাংস কুকুর খায় না, ভেঙো নাকো শুধু ভাঙা নয়, ফুল ফুটুক না ফুটুক, ফুলগুলো সরিয়ে নাও, আমি যত দূরেই যাই, ঘোড়ার চাল (ঘোড়াগুলো বাঘের মতো খেলছে), ছেলে গেছে বনে, কাল মধুমাস (ওঁর দীর্ঘতম কবিতা)। প্রতিটা কবিতাই ইতিহাস! সারা গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। জানালার শিক ধরে ছেলেমেয়েরা কবিতা শুনছিল। এক-একটা লাইন বলছিলেন আর চাপা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছিল হলঘর। আর আমি ভাবছিলাম, এর পরে আমাকে কবিতা পড়তে হবে, ধরণী দ্বিধা হও! কিন্তু বাংলা কবিতার অভিভাবক অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার, সে দিনের সভাপতি আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন সাহস দিয়ে, স্নেহ দিয়ে। রাতের বেলায় গেস্ট হাউসে সুভাষদার সঙ্গে কত গল্প! আমি প্রথমেই বললাম, আপনি বাসে চড়ে ৩৭ নম্বরে মস্কো যেতেন? একটু হাসলেন। ‘‘হ্যাঁ, আমি একটু বেশি বেশি মস্কো গিয়েছি। তবে শোনো— তোমরা নতুন এসেছ, তোমাদের বলি। রাশিয়াতে চুরি হত, ডাকাতি হত, ধর্ষণ হত। আমি সেগুলো লিখতে পারিনি, আমাকে লিখতে দেয়নি ওরা।’’ আমি বললাম, কারা দেয়নি? ‘‘এই আমাদের পাড়ার স্তালিনগুলো। তবে শোনো, রাশিয়ার একটা জিনিস খুব ভাল। তার নাম ভদকা। লেক মার্কেট থেকে আমি ছোট ছোট আলু কিনি। কম দাম। মার্বেলের মতো ছোট। ওগুলো সেদ্ধ করে নুন-মরিচ দিয়ে খেতে খুব ভাল লাগে। সঙ্গে একটু ভদকা। তোমাকে ফিরে গিয়ে বলব।’’ আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম— পরেন একটা ফতুয়া, প্রিয় খাবার আলুসেদ্ধ, পায়ে একটা চপ্পল, লেখেন দুটো কবিতা, ঘুমোন একটা চৌকিতে। অথচ এত আয়োজনহীন একটা মানুষ— তাঁকেও কিনা শুনতে হচ্ছে মদ-মেয়েমানুষের বদনাম!
উত্তরবঙ্গের ওই অসাধারণ আড্ডায় এক বারও কারও নামে নিন্দে করেননি। ‘পাড়ার স্তালিন’রা তাঁকে ছিঁড়ে খাচ্ছে তখন। তবুও মুখ খোলেননি। দুটো ছোট আক্ষেপ তিনি করেছিলেন অবশ্য, ‘‘শক্তিকে (কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়) বলেছিলাম, ‘শক্তি, অনেক দিন বাঁচতে হবে, না হলে জ্ঞানপীঠ পাবে না।’ শক্তি আমার কথা শোনেনি।’’ ওঁর দ্বিতীয় আক্ষেপটি বড় তিক্তমধুর, ‘‘নীরেনের (কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) কবিতা আমার খুব ভাল লাগে, সেটা আমি কাউকে বলতে পারিনি। বললে ওরা আমার দিকে খারাপ চোখে তাকাত।’’
আমি পরের দিন সকালেই কলকাতায় ফিরে আসি। দুপুরবেলা খবর পেলাম, তিনি গেস্ট হাউসে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছেন। আঁতকে উঠলাম। উনি তো পা দিয়ে কবিতা লিখতেন। মানে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে না বেড়ালে উনি লিখতে পারতেন না। তা-ই হল। এর পর সুভাষদার লেখা কমে গেল।”
এত অনুবাদ করেছেন, ভাবা যায় না। বুদ্ধদেব বসু অনুবাদক হিসেবে কিংবদন্তি হয়ে আছেন। তিনি বাংলায় ইউরোপ নিয়ে এসেছেন, উজ্জয়িনী নিয়ে এসেছেন, রাশিয়া নিয়ে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের ৬০০ পৃষ্ঠা দিয়েছেন অনুবাদের জন্য। অসামান্য অনুবাদ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু কারও অনুবাদ মুখে মুখে ঘোরেনি— যেমন নাজিম হিকমতের ‘জেলখানার চিঠি’ কিংবা পাবলো নেরুদার কবিতা, ফয়েজের কবিতা, গাথাসপ্তশতী, চর্যাপদ, অমরুশতক … কী অনুবাদ করেননি! অনুবাদ না করলে এক জন কবির হাত পবিত্র হয় না, সেটা বিশ্বাস করতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।
শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘ছড়ানো ঘুঁটি’-তে (২০০১) সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) ‘অরণ্যে রোদন’ কবিতায় লিখেছিলেন, ‘‘সেই কবেকার ফেলে আসা/ পায়ের ধুলো/ ঘুমের মধ্যে আমাকে পেছন থেকে/ সামনে তাড়া করে।’’
প্রকৃতপক্ষে, পায়ে চলা পথের সঙ্গ-অনুষঙ্গে তাঁর সমস্ত কবিতা-গদ্য-ছড়া-কথাসাহিত্য মায় তর্জমাও গ্রথিত। ঘরের বদলে পথ। গৃহের বদলে রাস্তা। রাস্তাই তাঁর জীবন আর সাহিত্যের একমাত্র রাস্তা। পথ চাওয়াতেই তাঁর আনন্দ।
একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর গ্রন্থনামে ফিরে ফিরে আসে এই চলাচলের প্রসঙ্গ। হাঁটা আর হাঁটা। পা-তোলা পা-ফেলা। ‘পদাতিক’ দিয়ে শুরু। তার পর ‘যত দূরেই যাই’, ‘একটু পা চালিয়ে ভাই’, ‘যা রে কাগজের নৌকো’। এমনকি ‘একবার বিদায় দে মা’ বললেই অব্যক্ত ‘ঘুরে আসি’ কথাটা শোনা যায়। ‘জল সইতে’ বা ‘ছড়ানো ঘুঁটি’ নামেও তো সেই পথবিলাসের সুমধুর ইশারা। বদ্ধ, স্থাণু ঘরে তিনি নেই। ওই যে তিনি ওই যে বাহির পথে… না, রথে নয়। পদব্রজে।
হয়তো সে কারণেই তাঁর কবিতায় এত সমাসোক্তি অলঙ্কার, এত জড়ের স্থবির অস্তিত্বে প্রাণস্পন্দন। পথ জীবন্ত, পথের দৃশ্য জীবন্ত, গাছপালা তো বটেই, এমনকি পাথর-নদী-পাহাড় কিংবা রোদ্দুর-মেঘ-বৃষ্টি সবাই জীবন্ত চরিত্র। একটা জীবন এই সব হরেক প্রাণস্পন্দনকে সঙ্গে নিয়ে চলমান রইলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গ্রিক শব্দ ‘অয়দিপাউস’ মূল ভাষার অর্থে ‘গোদা-পা’। আবার সফোক্লেস-এর নাটকে সেই নাম বহন করে অভিশাপ আর বিনষ্টি, দুর্ভাগ্য আর ভয়াবহ পরিণাম। পা সেখানে সর্বনাশের প্রতীক। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে বারংবার পা হয়ে ওঠে উজ্জীবনের দ্যোতনা, পায়ে চলা হল জীবনপার্বণের উল্লাস-উচ্ছ্বাস, আনন্দময় আয়ুযাপনের নিশান।
একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, ভাষা, ভূমি আর ভবিষ্যৎ— এই তিনটি ‘ভ’-এর ওপর ভর করে তাঁর লেখালিখির জগৎ। আমার কিন্তু মনে হয়, তার সঙ্গে মিশে থাকে তিন ‘প’-এর দুনিয়া— পা, পথ আর প্রান্তিকতা!
তাঁর গদ্যগ্রন্থগুলির দিকে তাকালেও দেখি একই আলপনা। ‘যখন যেখানে’, ‘ডাকবাংলার ডায়েরি’, ‘নারদের ডায়েরি’, ‘আবার ডাকবাংলার ডাকে’ তো বটেই, ‘যেতে যেতে দেখা’, ‘টো টো কোম্পানি’ কিংবা ‘চরৈবতি চরৈবতি’ সরাসরি আনে চলমানতার সঙ্কেত। ‘ইয়াসিনের কলকাতা’ জুড়ে হেঁটে হেঁটে পথে ব্যান্ড বাজানো আর শহর চেনা, ‘অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ’ উপন্যাসেও শেকড় ছিঁড়ে নতুন পরিবেশে যাওয়া। ‘কে কোথায় যায়’ সেই যাত্রার আর এক বিবরণ।
কবি সুভাষের জীবনটাও তো নিরন্তর অভিযাত্রা। এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে, এক মতাদর্শ থেকে অন্য মুক্তিতে, সঙ্ঘশাসন থেকে ব্যক্তি-প্রতিবাদে। আবার, একটু ঝুঁকি নিয়ে বলা চলে, নিষ্প্রাণ তত্ত্বকাঠামো ভেঙে প্রাণবন্ত মানবিকতায়। হয়তো কথাটা ভুলই বললাম। সুভাষের লেখাপত্র পড়লে দেখা যাবে, মানবিক নানা অনুভূতিতরঙ্গ দিয়ে তিনি সর্বদাই খাঁচাবন্দি তত্ত্বব্যাখ্যানগুলিকে ধাক্কা মেরে গিয়েছেন। ঘনিয়ে উঠেছে, তার ফলে, নানা আকারের রক্তমেঘ। এই প্রক্রিয়াটিও সুভাষ চালিয়ে গিয়েছেন। দমেননি। পার্টি এবং তার মধ্যমেধার হাতে অপমানিত হয়েছেন বারংবার, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন তার চেয়েও বেশি। অর্থকষ্ট, অসম্মান, অনটন কাঁধে নিয়েই কন্যাদের পালনের দায়িত্ব নিয়েছেন, বৈভবহীন অনাড়ম্বর জীবন কাটিয়েছেন আর বইয়ের নাম দিয়েছেন ‘ফকিরের আলখাল্লা’। সে-ও তো পথে পথে ‘সহজিয়া’ গান শোনানোর বৈরাগী মূর্তি!
‘সহজিয়া’ শব্দটাই হয়তো সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অনুধাবনের মূল চাবিকাঠি। হাজার বছরের পুরনো বাংলা বই ‘চর্যাপদ’ সেই ‘সহজিয়া’র উৎসমুখ। বাইরে সহজ, কিন্তু অন্তরে মুক্তিসাধনার সূক্ষ্ম ইশারা। বাউল ফকির দরবেশ কর্তাভজা আউলিয়া চিস্তি-র বিশাল বাহিনী যুগ যুগ ধরে এ দেশের পথে-সড়কে সেই বার্তা ছড়িয়ে চলেছে। সুভাষকে, মনে হয়, তারই উত্তরসূরি। তাঁর ‘মুক্তিসাধনা’ কি তত্ত্ববন্দি পার্টি প্রযোজিত? ‘লাল ঝান্ডা’র তলায় তলায়, সেই কোন যুগে এ তবে কেমন ইঙ্গিত?
‘‘রং-বেরঙের টুকরো কাপড়। জোড়া দিলে হয় বাউলের আলখাল্লা। নিজেদের মধ্যে তাদের যত বৈসাদৃশ্যই থাকুক, বাউলের জীবনই তাদের এক জায়গায় মিলিয়ে দেয়।”
‘‘এ বইতেও যদি পায়ের ধুলোয় সেই অমিলের মিল পাওয়া যায়, তা হলেই লেখক খুশি।’’
যে মূঢ় তত্ত্বান্ধরা ভাবছেন, এ হল উত্তরকালের ‘পার্টি-বিতাড়িত’ ‘জনবিচ্ছিন্ন’ ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ ‘নষ্টভ্রষ্ট’ সুভাষ, তাঁদের সবিনয়ে জানাই, এ লেখার তারিখ ৮.৫.১৯৬০। ‘যখন যেখানে’ বইয়ের ভূমিকা।
শেষ জীবনে তিনি আরও স্পষ্ট, আরও অন্তর্ভেদী। পা পথ আর প্রান্তিকতা কেমন অনায়াসে মিশিয়ে দিচ্ছেন মুক্তিসাধনার ‘সহজিয়া’ ঘরানায়— ‘‘চালের বাতায় গুঁজে রেখে এসেছি/ গাজীর পট/ শিকের ওপর তোলা রইল গুপীযন্ত্র/ কালের হাত সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতে/ আমি ফিরে আসব।/… ফুলছে ফুঁসছে ঢেউ—/ এক বার তুলছে মাথায়/ এক বার ফেলছে পায়ে।/ ও মাঝির পো,/ দরিয়া আর কত দূর?/ ঘর বার সমান রে বন্ধু/ আমার ঘর বার সমান/ পায়ের নীচে একটুকু মাটি/ পেলাম না তার সন্ধান/ আমার সেই পোষা পাখি/ আকাশের নীল রঙে আঁকি/ যত্নে বুকে করে রাখি/ তবু কেন সে করে আনচান/ আমার ঘর-বার সমান’’(‘জল সইতে’, ১৯৮১) কিংবা, ‘‘নীচে তাকালে জল থই থই বন্যা/ ক্ষেত জ্বলছে খরায়/ চুনি কোটালের মা দাঁড়িয়ে/ নেহার বানুর কন্যা/ সারি সারি বন্দুকধারী/ সেলাম দেয় বুলেটপ্রুফ গাড়ি/ হেলিকপ্টার পায়ের ধুলো/ দিল যখন দীঘায়/ জানো কি মা, ঠিক তখনই বাউলগুলো. দুয়োরে এসে কী গায়—’’ (‘একবার বিদায় দে মা’, ১৯৯৫) সেই বহুস্তরিক ‘মুক্তি-সন্ধানী’ সুভাষ, সেই অপমানিত কিন্তু পরাক্রমশালী কলমের অধিপতি সুভাষ, সেই মহাবিশ্বজগতের প্রাণচাঞ্চল্যে স্নাত সুভাষ, সেই পথপদাবলির কীর্তনিয়া সুভাষ, লোকালয় আর লোকালয়হীন ভূখণ্ডবাসীদের আশা-নিরাশার বীণকার সুভাষের শতবার্ষিকী! আজ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, শতবর্ষ পূর্ণ হল তাঁর।
আমরা, যারা তাঁর উত্তরকালে দেখছি সেই একই ভাবে ‘‘রক্তে পা ডুবিয়ে হাঁটছে/ নিষ্ঠুর সময়,/ সারা পৃথিবীকে টানছে/ রসাতলে/ এখনও আকাশচুম্বী ভয়’’— তারা কি এক বার সর্বান্তঃকরণে অভিবাদন আর কুর্নিশ জানাব না এই মহামানবিক স্রষ্টাব্যক্তিত্বকে? বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি আর বাংলা জনমানবকে যিনি আশ্চর্য মমতায় ছুঁয়ে থাকতে চেয়েছেন, সেই কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা আমাদের সকলেরই দায়। দেশ, সমাজ আর সমকালকে তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন বহমান ব্যক্তিসঙ্কটের সঙ্গে।
তাঁর গ্রন্থে-পঙ্ক্তিতে-রচনায় অনশ্বর মুক্তিসাধনাকে আমাদের প্রণাম, তাঁর ‘মানুষ-রতন’ বন্দনাকে আমাদের সমর্থন। একেবারে আটপৌরে, সাধারণ্যে মুখে মুখে ফেরা শব্দ-বাক্যকে তিনি জাদুবলে অলৌকিক করে দিয়েছেন। বিবৃতিকে এক মোচড়ে বানিয়ে দিয়েছেন নভশ্চর। তাঁর শতবার্ষিকীর সানন্দ আয়োজন প্রকৃতপক্ষে বাংলার সমবেত সঙ্কল্প। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে চাই আমাদের যাপনে, বেদনায়, সংশয়ে, রোমাঞ্চে, বিশ্বাসে, অঙ্গীকারে, অনুসন্ধিৎসায়। তাঁর বেদনার আকাশগঙ্গা আমাদের বুকে বুকে ঢেউ তুলুক।
‘‘আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে/ নিকোনো উঠোনে/ সারি সারি/ লক্ষ্মীর পা/ আমি যত দূরেই যাই।’’
যে দিন চলে গেলেন, সে দিন তাঁরা কেউ আসেন নি। তাঁরা মানে ওঁরা। যাঁরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনীতি করে বড় হয়েছেন, মিছিল করেছেন, রাস্তায় নেমেছেন, পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা এলেন না। শ্মশানে ছিলেন মাত্র কয়েক জন। ভাবা যায় না। সবচেয়ে জনসমাদৃত একজন আধুনিক কবি ঢুকে গেলেন চুল্লিতে।
তবে যে নাজিম হিকমতকে তিনি বাঙালি ঘরে বসিয়ে গেলেন, যে নেরুদাকে তিনি ডাল মাখা ভাতের পাশে রেখে গেলেন, যে ফয়েজকে তিনি লাহৌর লখনউ থেকে কলকাতার গলিতে রেখে গেলেন, এ রকম একটা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে গেলেন— তাঁকে কে কোথায় কোন তামিলে, কোন মরাঠিতে, কোন স্প্যানিশে, কোন ফরাসিতে তুলে আনলেন? আজ পর্যন্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় বড় করে ইউরোপ এশিয়া আমেরিকায় পৌঁছতে পারেননি। সেটা ২৫ কোটি বাঙালির দুর্ভাগ্য। দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কবি সুবোধ সরকার একটি বিনীত প্রশ্ন করেছেন — “আপনাদের পোস্ট কলোনিয়াল প্যাকেজে কি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নামটা তোলা যায় না?”
(তথ্যসূত্র:
১- সুভাষ মুখোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্য, সন্দীপ দত্ত, র্যাডিকেল ইম্প্রেশন (২০১২)।
২- সালেমন, কবিরণ বজবজে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ (২০১২)।
৩- শতবর্ষে সুভাষ মুখোপাধ্যায়: বাংলাদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি, মতিউর রহমান, প্রথমা প্রকাশন (২০১৯)।
৪- ২৬শে মে ২০১৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণে কবি সুবোধ সরকার লিখিত প্রবন্ধ।
৫- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সাল।
৬- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২শে এপ্রিল ২০১৮ সাল।
৭- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সাল।)
মতামত লেখকের ব্যক্তিগত