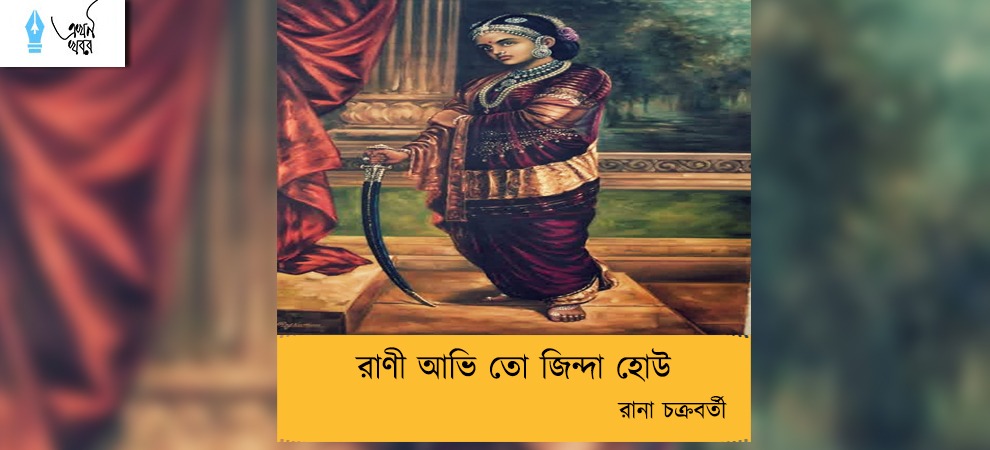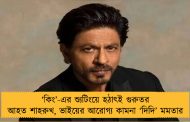১৮২৮ সালে আজকের দিনেই ‘বারাণসী’তে ‘ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই’ জন্মেছিলেন। আজ ১৬৩ বছর পরেও তিনি ১৮৫৭ সালে ভারতে সংঘটিত হওয়া ‘সিপাহী বিদ্রোহের’ অন্যতম আলোচিত চরিত্র। বুন্দেলখণ্ডের দেহাতি মানুষ আজও বলেন – ‘‘রাণী মরগেই ন হউনি, আভি তো জিন্দা হোউ।’’ রাণীকে লুকিয়ে রেখেছে বুন্দেলখণ্ডের পাথর আর মাটি। অভিমানিনী রাণীর পরাজয়ের লজ্জা লুকিয়ে রেখেছে বুন্দেলখণ্ডের জমি। সরকারি ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ রাণীকে এক ভাবে দেখেছে, আর স্থানীয় গরিব মানুষেরা তাঁকে উপকথায় নিজেদের জীবনে বয়ে চলেছেন। ঝাঁসির রাণীকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন কিংবদন্তী লেখিকা ‘মহাশ্বেতা দেবী’। ‘ঝাঁসির রাণী’ তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস। ‘মহাশ্বেতা দেবী’ এই উপন্যাস লেখার আগে খোঁজখবর নিতে ঝাঁসিতে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বশরীরে, আর সেখানেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল ‘ঝাঁসির রাণীর ভাইপো গোবিন্দ চিন্তামণি পাণ্ডে’র সঙ্গে। সত্যিই ‘রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে’ ছিলেন ‘গোবিন্দ চিন্তামণি পাণ্ডে’। তাঁর আত্মীয়া ছিলেন ‘রাণীর বিমাতা’। সেই সূত্রে তিনি ‘রাণীর ব্যক্তি-পরিচয়’ ভালই জানতেন। তাঁর কাছ থেকেই ‘রাণীর ব্যক্তিজীবনের প্রচুর তথ্য’ পেয়েছিলেন ‘মহাশ্বেতা দেবী’। রাণী (ব্যক্তিজীবনে নিরামিষাশী) ‘একটু অধিক পক্ব ঘি’ পছন্দ করতেন। রাণীর কপালে ‘অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি উল্কির দাগ’ ছিল। ‘রাণীর বিমাতা চিন্তাবাই’ তাঁর নাতনি ‘দুর্গা’কে কৌতুক করে মাঝে মাঝেই বলতেন, ‘‘আয়, তোর কপালে উল্কি পরিয়ে দিই। বাই সাহেবার যেমন ছিল!’’ জানা যায়, ১৯০৩ সালে ‘ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল’ তৈরির সময় ‘লর্ড কার্জন’কে ‘দামোদর রাও’ চিঠিতে অনুরোধ করেছিলেন, সেখানে যদি ‘রাণীর একটি প্রতিকৃতি’ থাকে! ‘লর্ড কার্জন’ উৎসাহ দেখিয়ে তাঁকে ছবি পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, ‘রাণীর ছবি’ ‘ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে’ রাখা যেতে পারে, কিন্তু ‘নানাসাহেবের’ নয়। সেই ছবি পাঠানো যায়নি, ‘কার্জনের’ পরবর্তী কোনও ‘বড়লাট’ এই বিষয় নিয়ে আর কোন উৎসাহ দেখাননি। দেখালে কলকাতার ‘ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে’ই থাকতে পারত রাণীর প্রামাণ্য তৈলচিত্রটি।

ইতিহাস বলে, বুন্দেলখণ্ডের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র মারাঠা সর্দারের রাজ্য ছিল ‘ঝাঁসী’। পেশোয়ার সময়ে এটি ‘সুবা প্রদেশ’ বলে পরিচিতি ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার প্রদেশটিকে আলাদা একটি রাজ্যের গৌরবে উন্নীত করেন। ‘বুন্দেল রাজা ছত্রশাল’ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সময় মতো সাহায্য করার জন্য ‘প্রথম বাজীরাও’কে তাঁর রাজ্যের ‘তিন ভাগের এক ভাগ’ দিয়ে দেন। পেশোয়া তাঁর শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ‘বুন্দেলখণ্ড’কে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথম অংশের শাসনভার ‘গোবিন্দ পান্থ খেরে’র হাতে অর্পণ করেন, তাঁর সদর দফতর ছিলো ‘সাগার’। দ্বিতীয় অংশে ছিল ‘বান্দা’ এবং ‘কল্পি’। তাঁর অবৈধ সন্তান ‘শমসের বাহাদুর’কে এই অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তৃতীয় অংশ ঝাঁসীর শাসনকর্তার পদ ‘রঘুনাথ হরি নাভালকর’-এর পরিবারে চিরস্থায়ী হয়ে যায়। তিনি তাঁর ভ্রাতা ‘শিবরাম ভাও’কে শাসনভার ছেড়ে দিয়ে ১৮০৪ সালে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ‘সন্ধিসূত্রে’ আবদ্ধ হন। ১৮১৭ সালে ‘শিবরাম ভাও’য়ের উত্তরাধিকারী এবং দৌহিত্র ‘রামচন্দ্র রাও’য়ের মধ্যে এক ‘সন্ধিচুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুসারে ‘রামচন্দ্র রাও’কে ‘উত্তরাধিকারী’ নির্বাচিত করা হয়। ১৮৩৫ সালে তাঁকে ‘মহারাজাধিরাজ ফিদভী বাদশাহ্ জমিয়া ইংলিশস্থান’ উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিলো না। তাঁর বিধবা পত্নী ‘কৃষ্ণরাও’ নামে তাঁর এক বোনের ছেলেকে ‘দত্তকপুত্র’ হিসেবে গ্রহণ করেন। যেহেতু প্রচলিত প্রথা অনুসারে অন্য পরিবারের সন্তানকে ‘দত্তক’ হিসেবে গ্রহণ করা চলে না, সেহেতু ‘রামচন্দ্র রাও’য়ের কাকা ‘রঘুনাথ রাও’য়ের সিংহাসনে আরোহণের স্বপক্ষে ‘ব্রিটিশ সরকার’ মত দিয়েছিল। কিন্তু ‘রঘুনাথ রাও’ ছিলেন একেবারে ‘হঠকারী’ প্রকৃতির লোক। তাঁর ‘কুশাসনে’ রাজ্য রসাতলে যাবার উপক্রম হয়েছে, ‘ব্রিটিশ সরকার’ এ অজুহাতে রাজ্যভার পরিচালনা নিয়ে নেয়, বলা ভালো ‘দখল’ করে নেওয়া হয়েছিল। ‘রঘুনাথ রাও’ আইনতঃ কোনো ‘উত্তরাধিকারী’ না রেখেই মারা যান। তাঁর অবৈধ সন্তানত্রয় ‘কৃষ্ণরাও’, ‘রামচন্দ্র রাও’ এবং রাজার ভ্রাতা ‘গঙ্গাধর রাও’য়ের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার ‘গঙ্গাধর রাও’কেই সমর্থন করে। কিন্তু ১৮৪৩ সালের আগে তাঁর হাতেও শাসনভার দেওয়া হয়নি। তিনি চমৎকার একখানা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন এবং শহরের উন্নয়ন সাধন করেছিলেন।
১৮৫৩ সালে তাঁর কোনো ‘পুত্রসন্তান’ না রেখে তিনি মারা যান। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বের দিন তিনি তাঁর সভাসদবৃন্দ ‘ঝাঁসীর ব্রিটিশ রাজনৈতিক এজেন্ট’ ‘মেজর এলিস’, ‘ঝাঁসী বাহিনীর সামরিক প্রধান’ ‘ক্যাপ্টেন মার্টিন’-এর সামনে ‘নাভালকর’ পরিবারের একটি ছেলেকে ‘দত্তক’ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ‘মেজর এলিস’কে অনুরোধ করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার যেন তাঁর ‘বিধবা পত্নী’ এবং পুত্রের হাতে ‘শাসনভার’ অর্পণ করেন। গভর্ণর জেনারেলের কাছে যে মানচিত্র পাঠানো হয়েছিলো, তাতে ‘রাণীমাতা দাতিয়া’, ‘ওরচা’ ইত্যাদি বুন্দেল রাজ্যে দত্তক পুত্রের অধিকার স্বীকৃতির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। ‘মেজর এলিস’ও বিধবা রাণীকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ‘গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট ম্যালকম’ এ সম্পর্কে ‘ভিন্নতর ধারণা’ পোষণ করতেন।
‘গঙ্গাধর রাও’য়ের মৃত্যুর সময়ে ‘লর্ড ডালহৌসী’ কলকাতার বাইরে ছিলেন, সুতরাং রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সে যাই হোক, ‘লর্ড ডালহৌসী’ রায় দিয়েছিলেন ঝাঁসীকে ব্রিটিশ শাসনাধীনে নিয়ে এলেই প্রজাদের সুবিধা হবে। ১৮৫৪ সালে ঝাঁসীকে ব্রিটিশ সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাণীর জন্য ‘যাবজ্জীবন ভাতা’ মঞ্জুর করা হয় এবং তাঁকে রাজপ্রাসাদে বাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ‘ব্রিটিশ বিচারালয়ের আওতামুক্ত’ থাকার অধিকারও দেওয়া হয়। এমন কি ‘দত্তক পুত্র’ গ্রহণেও কোনো বাধা দেওয়া হয়নি। ‘দামোদর রাও’কে পারিবারিক ঐশ্বর্যের এবং তাঁর বাবার ব্যক্তিগত সম্পদের ‘উত্তরাধিকারী’ হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।
‘গঙ্গাধর রাও’য়ের মৃত্যুর পর রাজকোষ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছিল যে, ৬ লক্ষ টাকা রাজকোষে সঞ্চিত রয়েছে। এ সমস্ত টাকা ভারত সরকারের কাছে গচ্ছিত ছিল, এ শর্তে যে সরকার অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজপুত্রের ‘আমানতদারী’ করবেন। সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, সরকার ভারতীয় জনসাধারণের ‘অনুভূতিতে আঘাত’ দিয়ে বসল। নাবালকের বংশের ‘পারিবারিক বিগ্রহ মহালক্ষ্মী’র মন্দিরের ব্যয়ভার বহনের জন্য যে সকল গ্রাম নির্দিষ্ট করে রাখা ছিলো সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়। রাণী প্রথমে ‘ভাতা’ গ্রহণ করতে রাজী হননি। কিন্তু ‘গঙ্গাধর রাও’য়ের আত্মীয়-স্বজনের ‘প্রতিপালন’ এবং ‘ঋণ শোধ’ করার জন্য ভাতা গ্রহণ ছাড়া তাঁর সামনে আর কোনো পন্থা ছিল না। সরকার ঝাঁসীর মতো ব্রাহ্মণ রাজ্যে ‘গো-হত্যা’র প্রবর্তন করাতে তিনি সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।
রাণী সঞ্চিত ৬ লাখ টাকার মধ্যে এক লাখ টাকা ‘গঙ্গাধর রাও’য়ের পবিত্র শ্রাদ্ধের কাজে বরাদ্দ করে সরকারের কাছে টাকার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সরকার ‘চারজন জামিনদার’ ছাড়া টাকা দিতে রাজী হয়নি। সরকারের পক্ষে যুক্তি ছিল, নাবালক রাজপুত্র যদি ‘সাবালক’ হয়ে এ টাকা দাবি করে, ‘জামিনদার’ চারজনকেই সে টাকা পরিশোধ করতে হবে। রাণী তখনও আশা করেছিলেন, অন্যান্য রাজ্যহারা রাজপুরুষদের বেলায় যেমন হয়েছে, তেমনি যদি ডিরেক্টরদের সভায় তিনি ‘প্রতিনিধি’ প্রেরণ করেন, তাহলে তাঁর ছেলের উপর অবশ্যই ‘সুবিচার’ করা হবে । সুতরাং তিনি বিলাতে ‘প্রতিনিধি’ প্রেরণ করলেন। তাতে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হলো, কিন্তু ‘ডিরেক্টর সভা’ গভর্ণর জেনারেলের সিদ্ধান্তের কোনো অদল-বদল করলেন না। সে কারণে এবং ঝাঁসীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে জনসাধারণের মনে ‘সন্দেহ’ দেখা দিলো।
‘রাণী লক্ষ্মীবাই’ ছিলেন গরীব পিতামাতার মেয়ে। রাণীর পিতা ‘মহরাপন্থ তসবে’ ‘চিমনজী আপ্পা’র ‘দেহরক্ষী’ ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ‘বেনারসে’ থাকতেন। রাণীর ‘বাল্যনাম’ ছিলো ‘মনিকর্ণিকা’। স্বামীর ঘরে এসেই তিনি ‘লক্ষ্মীবাই’ নামে পরিচিত হন। তাঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বিদ্রোহের পরে তাঁর সম্বন্ধে নানা ‘গল্প-কাহিনী’ এবং ‘গুজব’ সৃষ্টি হয়। স্বামীর তুলনায় তিনি অপেক্ষাকৃত কম বয়েসী ছিলেন। প্রথম রাণীর মৃত্যুর পর ‘গঙ্গাধর রাও’য়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ‘জন লেং’ নামে যে ‘খ্যাতনামা ব্রিটিশ আইনজীবি’ ঝাঁসীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, তিনি তাঁর সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন ‘নাতিদীর্ঘ মহিলা’, একটু ‘স্কুলাঙ্গী’, তবে ‘অধিক নয়’। যৌবনে নিশ্চয়ই তাঁর ‘মুখখানা অত্যন্ত সুন্দর ছিল’। তখনও সে মুখের আকর্ষণ কম ছিলনা। মুখাবয়বটিও ছিল ‘সুন্দর’, ‘বুদ্ধিদীপ্ত’। বিশেষ করে তাঁর ‘চোখ দুটি টানা টানা’, ‘নাকটা টিকালো’ ছিল। তাঁর গাত্রবর্ণ ‘ফর্সা’ না হলেও কিছুতেই তাঁকে ‘কৃষ্ণাঙ্গী’ বলা যেত না। সবচেয়ে আশ্চর্য, ‘একজোড়া ইয়াররিং’ ছাড়া তাঁর শরীরে আর কোনো ‘অলংকার’ থাকত না। তিনি সাদাসিধে ‘মসলিনের শাড়ি’ পরিধান করতেন। সে শাড়ি এতো ‘মিহি’, এতো সূক্ষ্ম যে তাঁর শরীর অন্তরাল থেকে আভাসিত হয়ে উঠত। তিনি ‘অনিন্দ্যসুন্দরী মহিলা’ ছিলেন। কিন্তু তাঁর ‘কর্কশ কণ্ঠস্বর’ সৌন্দর্যকে অনেকাংশে ‘ম্লান’ করে দিয়েছিল। ‘মেজর এলিস’ ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, ‘মেরে ঝাঁসী নেহি দেওঙ্গী।’ এটা ‘সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ’ না কি ‘আবেগের ক্ষণিকের প্রকাশ’ বলা মুশকিল। কিন্তু ‘ঝাঁসী’কে ভারত সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রাণী নীরবে স্বামীর প্রাসাদ ছেড়ে তাঁর জন্য নির্ধারিত প্রাসাদে চলে যান। সেখানে তিনি হিন্দু বিধবার মতো জীবনযাপন করছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ‘১২নং বাঙালি পল্টন’ কেল্লার মধ্যে ছাউনি ফেলে। সবকিছুই শান্তিপূর্ণভাবে চলছিলো। নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কোনো রকমের ‘বিশৃঙ্খলা’ দেখা দেয়নি। ‘ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার স্কীন’কে ‘পলিটিক্যাল অফিসার’ এবং ‘ক্যাপ্টেন ডানলফ’কে ‘সেনাবাহিনীর অধিনায়ক’ নিযুক্ত করা হয়।
১৮৫৭ সালের একসময়ে, ‘চর্বি মাখানো টোটার কাহিনী’ অন্যান্য স্থানের মতো নিশ্চিতভাবে ‘ঝাঁসী’তেও প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। মে মাসে দিল্লী এবং মীরাটের বিদ্রোহের সংবাদ ‘ক্যাপ্টেন ডানলফ’ এবং তাঁর সহকর্মীদের কাছে এসে পৌঁছয়। তাঁরা কোনো রকম গোলযোগের আভাসও পাননি। ‘আমানত খানের বর্ণনা’ মতে, জুন মাসে, ‘১২নং বাঙালি পল্টন’-এর একজন সেপাইকে ‘মৃত্যুদণ্ড’ দান করা হয়। ‘স্যার রবার্ট হ্যামিল্টন’ বলেছেন –
‘‘আমার রেজিমেন্টের কোনো একজন সেপাইয়ের আত্মীয় অথবা চাকর দিল্লী থেকে একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে। সে চিঠির মর্মানুসারে, ‘ঝাঁসীর ঘাঁটিতে বাংলা প্রেসিডেন্সীর যে সকল সেপাই রয়েছে তাঁরা যদি সামগ্রিকভাবে বিদ্রোহ না করে তা হলে জাতিচ্যুত অথবা ধর্মচ্যুত হবে।’ …’’
৫ই জুন চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ‘ঝাঁসীর ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্যাপ্টেন গর্ডন’ ৬ তারিখে ‘মেজর আরস্কিন’ এবং ‘ওয়েস্টার্ণ’কে লিখেছেন,
‘‘স্কীনের অনুরোধে কয়েক পংক্তি আমি আপনার কাছে লিখছি। ১২নং রেজিমেন্টের একাংশ ক্যান্টনমেন্টে প্রকাশ্য বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে। যে দুর্গের মধ্যে অস্ত্র ও সাড়ে চার লক্ষ টাকার মতো রাজস্ব জমা ছিলো, সব দখল করে ফেলেছে। তাঁদের সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীর সেপাইরা এসে যোগ দিয়েছে। এখন আমাদের হাতে রয়েছে মাত্র দু’টি কামান। তাঁরা কিভাবে এসব করতে সমর্থ হয়েছে, নিম্নে তা বলছি। গতকাল বেলা ৩টার সময় সেপাইদের মধ্যে শোরগোল উঠলো যে ডাকাতেরা অস্ত্রাগার আক্রমণ করেছে এবং তাঁরা দ্রুত সেদিকে ধাওয়া করলো। বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত নয় এমন কতিপয় সেপাই গুলি ভর্তি বন্দুকসহ অবস্থান নিয়ে নিলো। তারপরে বিদ্রোহীরা পালিয়ে যায় কিন্তু সন্ধ্যার সময় তাঁরা সদলবলে আবার আগমন করে। দু’টি কামান এবং ৫০ জন সেপাইয়ের সাহায্যে অস্ত্রাগার আমরা তখনো রক্ষা করে আসছিলাম। আমরা নিশ্চিত যে সেপাইদের এবং গোলন্দাজদের মধ্যে কাউকে বিশ্বাস করতে পারবো না। আমি ঠাকুরদের সাহায্যে বিদ্রোহীদের দুর্গ থেকে বের করে দিতে পারি, কিন্তু সকলে প্রথমবার গুলি ছোঁড়ার পরেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেবে।’’
জানা যাচ্ছে ঠাকুরেরা বেশ হৃষ্টচিত্তেই ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্যের প্রস্তাব করেছিল। অনেক সাহায্য তাঁদের কাছ থেকে নেওয়াও হয়েছিল। এরপরে সাহায্য চেয়ে ‘গোয়ালিয়র’ এবং ‘কানপুরে’ সংবাদ পাঠানো হয়। ‘আরস্কিন’ এবং ‘ফোর্ড’ সঙ্গে সঙ্গে ‘ইউরোপীয়’ এবং ‘খ্রীস্টানদের পরিবার-পরিজনসহ’ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ভালোভাবে জানতেন যে এখন কোনো দিক থেকে সাহায্যের আশা করতে পারেন না এবং নিজেদের যা আছে তাই দিয়েই আত্মরক্ষা করতে হবে।
‘ক্যাপ্টেন ডানলফ’ এবং অন্যান্য সামরিক অফিসারেরা তখনও আশা পোষণ করছিলেন যে তাঁরা সেপাইদের শান্ত রাখতে পারবেন এবং সেজন্য তাঁরা তখনও সেপাই লাইনে শয়ন করতেন। ৬ তারিখে ‘জেল দারোগা’ সেপাই-সান্ত্রীসহ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন এবং ‘ক্যাপ্টেন ডানলফ’কে হত্যা করেন। যাঁরা ব্রিটিশ পক্ষ নিয়েছিলো, সে সকল সেপাইদেরও হত্যা বা জখম করা হয়। ‘১৪নং গোলন্দাজ বাহিনীর লেফটেন্যান্ট ক্যাম্পবেল’ আহত হন। চারদিক থেকে দুর্গ ঘেরাও করে রাখা হয়। তিনজন ছদ্মবেশে দুর্গের বাইরে যেতে চেষ্টা করে ধৃত হয় এবং তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। ৮ তারিখে ‘ক্যাপ্টেন গর্ডন’ মাথায় ‘গুলিবিদ্ধ’ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন অথবা ‘হতাশায় আত্মহত্যা করেন’। ‘লেফটেন্যান্ট পাওরিস’ দুর্গের অভ্যন্তরেই একজন ভারতীয় চাকরের হাতে নিহত হয়েছিলেন। দ্বি-প্রহরের দিকে ‘নিরাপত্তার শর্তে’ অথবা ‘কোনো রকম শর্ত ছাড়াই’ দুর্গ থেকে সকলে বেরিয়ে আসেন। ‘শিশু’, ‘মহিলা’সহ দলের সমস্ত লোককে ‘নির্বিচারে হত্যা’ করা হয়। মৃতদেহগুলো স্থূপাকারে ‘জোখানবাগে’ রাখা হয়েছিল এবং সকলকে একটি মাত্র গর্তে চাপা দেয়া হয়। ‘জেল দারোগা করিম বখশ’ এই নৃশংস হত্যার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ‘দুটি সন্তানসহ একটি মাত্র মহিলা’ হত্যাকারীদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।
‘স্যার রবার্ট হ্যামিল্টন’ যিনি এক বছর পরেও এ ব্যাপারে ‘অনুসন্ধান’ করেছিলেন, তিনিও স্পষ্টভাবে রাণীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের কোনো সংযোগ আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। আগেই ‘১২নং রেজিমেন্টের মত্যুদণ্ড প্রাপ্ত সেপাইটি’র কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁকেই তিনি ‘দায়ী’ করেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, বিদ্রোহীরা ‘যে সকল সেপাই বিদ্রোহে অংশ নিতে রাজী ছিল না’, তাঁদেরকে ‘বন্দুকের মুখে বিদ্রোহে অংশ নিতে বাধ্য করে’ বিদ্রোহী সেপাইরা। তারপরে বিদ্রোহীরা সকলে রাণীর প্রাসাদে গমন করে ‘গুলি ভর্তি বন্দুক’সহ রাণীর কাছ থেকে ‘সাহায্য’ এবং ‘রসদ’ দাবি করে। তিনি সেপাইদেরকে খুশী মনে ‘রসদ’, ‘অস্ত্রশস্ত্র’ এবং ‘আরও নানা প্রকারে সাহায্য’ করেন।
এ বর্ণনার সঙ্গে ‘কমিশনার এবং এজেন্ট মেজর সি. আরস্কিন’-এর কাছে চিঠিতে বিদ্রোহের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায়, রাণীর কাছ থেকে ‘প্রচুর টাকা-পয়সা’ আদায় করে ১২ তারিখে সেপাইরা ‘দিল্লী’ অভিমুখে যাত্রা করে। সেদিনই ডাকহরকরা ‘আরস্কিন’কে একখানা পত্র দিয়ে যায়। দু’দিন পরে ডাকহরকরা ঝাঁসীর ঘটনার আনুপূর্বিক বৃত্তান্তসহ আরেকখানা পত্র তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত করে। দেখা যায় তাতে রাণী লিখেছেন, ঘাঁটিতে যে সকল ‘সরকারি সেপাই’ রয়েছে তাঁরা ‘ধর্মহীন’, নিষ্ঠুরভাবে ‘ঝাঁসীর সমস্ত সামরিক বেসামরিক ইউরোপীয় অধিবাসীদের হত্যা করেছে’। ‘কেরাণীকূল এবং তাঁদের পরিবারবর্গ’ কেউই রক্ষা পায়নি। ‘কামানের অভাববশতঃ’ রাণী তাঁদের কোনো রকমের ‘সাহায্য’ করতে পারেননি। তাঁর মাত্র ৫০ থেকে ১০০ জন সৈন্য ছিলো। তাঁর প্রাসাদ পাহারা দেয়ার জন্য তাঁদের প্রয়োজন। সে কারণে তিনি কোনো সাহায্য করতে পারেননি। এজন্য তাঁর ‘আফসোসের অন্তঃ’ নেই। তারপরে বিদ্রোহী সেপাইরা তাঁর বিরুদ্ধেও প্রচুর ‘ধ্বংসাত্মক কাজ’ করছে, চাকর-বাকরদের উপর ‘নির্যাতন’ করেছে এবং তাঁর কাছ থেকে ‘প্রচুর অর্থ ছিনিয়ে’ তাঁরা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছে। যেহেতু ‘রাণী শাসন করার একমাত্র দাবিদার’, তাই সেপাইরা যখন ‘সম্রাটের কাছে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা’ করেছে, এ সময়ে ‘শাসনকার্য’ তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক।
বোঝা যাচ্ছে, রাণী যে ‘ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল’ ছিলেন, তাই সেপাইদের দ্বারা সংঘটিত এতো বড়ো মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর তিনি ঝাঁসীর তহশীলদারের সাহায্যে ‘ডেপুটি কমিশনারের বিচার বিভাগীয় সেরেস্তাদার’ এবং ‘সুপারিন্টেন্ডেন্টের কোর্টে’ সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন। রাণী যদি সেপাইদের অনুরোধে রাজী না হতেন, তাহলে তাঁরা রাণীর প্রাসাদ উড়িয়ে দিত। তাঁর ‘মান-সম্মান রক্ষা’ করার জন্য তিনি সেপাইদের অনেক ‘অনুরোধ’ রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁকে অনেক ‘সম্পদ’ এবং ‘নগদ টাকা’ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। সমগ্র জেলার মধ্যে একজন ব্রিটিশ অফিসারও ‘জীবিত নেই’ জেনে তিনি জেলার প্রত্যেকটি সরকারি কর্মচারির কাছে ‘পরোয়ানা’ পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা ‘কর্মস্থলে’ থেকে ‘কর্তব্য কর্ম’ করে যায়। বার বার তাঁকে ‘ভয়’ দেখানো হয়েছিল। এটা ঠিক যে এ ‘সংবাদ’ সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো উচিত ছিল। কিন্তু ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি যে সকল লোক, তাঁরা তাঁকে সে রকমের কোনো ‘সুযোগ’ দান করেননি। সেপাইরা দিল্লীর দিকে পথ রওনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্র লিখতে বসেছিলেন। ১৪ই জুলাই তারিখে রাণী যে ‘পত্র’ লিখেছিলেন, তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল, সমগ্র জেলাতে ‘অরাজকতার রাজত্ব’ চলছে। প্রতাপশালী সামন্তেরা দুর্গগুলো অধিকার করে নিয়ে আশেপাশে ‘নির্যাতন’ এবং ‘লুণ্ঠনকার্য’ চালিয়ে যাচ্ছে। জেলার ‘নিরাপত্তা রক্ষা’ করা তাঁর ‘ক্ষমতার বাইরে’, কারণ এর জন্য ‘অর্থের প্রয়োজন’। এ অবস্থায় কোনো ‘মহাজন’ তাঁকে অর্থ ‘ঋণ’ দিতে রাজী হবে না। বর্তমান সময় পর্যন্ত তাঁর ‘ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয়’ করে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও লুটেরাদের হাত থেকে ‘নগর রক্ষা’ করে আসছেন। শহর এবং মফঃস্বলের ঘাঁটির অনেক কর্মচারিকে তিনি ‘আশ্রয়দান’ করেছেন, কিন্তু উপযুক্ত ‘সরকারি শক্তি’ এবং ‘অর্থের অভাবে’ তা দীর্ঘদিন রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং জেলার প্রকৃত অবস্থা লিখে তিনি জানিয়েছিলেন, বিশ্বাস মতো তাঁর ওপর যে ‘আদেশ’ জারী করা হবে সে অনুসারেই তিনি কাজ করবেন।
এ সরল সহজ পত্রের ভাষার মধ্যে কোনো রকমের ‘ঘোরপ্যাঁচ’ ছিলনা। রাণী স্পষ্টই স্বীকার করেছিলেন, তাঁকে ‘বিদ্রোহীদের সামরিক তহবিলে চাঁদা দিতে হয়েছে’। সেপাইদের সঙ্গে কোনো রকম ষড়যন্ত্রে যদি তিনি লিপ্ত থাকতেন, তাহলে তাঁদেরকে ‘ঝাঁসী’তে ‘অবস্থান করার জন্য প্ররোচিত’ করতেন।
‘মেজর আরস্কিন’ রাণীর ‘আন্তরিকতায়’ কোনো রকম ‘সন্দেহ’ করেননি। সেজন্য ‘মধ্যবর্তী সময়ে’ তাঁর হাতে ‘রাজ্যের শাসনভার’ ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে ‘পুলিশ নিয়োগ’ এবং ‘রাজস্ব আদায়ের নির্দেশ’ দান করেছিলেন। ভারতের ‘গভর্ণর জেনারেল’ ‘শর্তসাপেক্ষে’ মেজর আরস্কিনের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল, ‘রাণীর বিবৃতি’ যদি ‘মিথ্যা’ হয়, তাহলে রাণীকে ‘রেহাই’ দেওয়া হবে না। ইংরেজরা ঝাঁসীতে ৬০জন পুরুষ, নারী ও শিশু হত্যার ব্যাপারে চুপ থাকতে পারছিলেন না। কিন্তু ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকারের পক্ষে এ ব্যবস্থা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। সারা ভারত জুড়ে সেপাইরা তখন বিদ্রোহ করছিল।
ওদিকে ‘রাণীর শত্রুরা’ও বসে ছিলো না। ‘গঙ্গাধর রাও’য়ের মৃত্যুর পর ‘ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব রাও’ বার বার সিংহাসন দাবি করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, সেপাইরা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলে অবশেষে তাঁর ‘ক্ষমতা দখলের সুযোগ’ এসেছে। তিনি কিছু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে ঝাঁসী থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ‘কারেরা দুর্গ’ অধিকার করলেন। তারপর সেখান থেকে ‘পুলিশ’ এবং ‘রাজস্ব কর্মচারিদের’ তাড়িয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি নিকটবর্তী গ্রামসমূহে ‘গোলযোগ’ করতে থাকেন এবং নিজেকে ‘ঝাঁসীর মহারাজা’ বলে ‘ঘোষণা’ করেন। একসময়ে রাণীর সৈন্যরা তাঁকে কারেরা হতে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু তিনি ‘নরওয়ারের সিন্ধিয়া’র রাজত্বে ‘নিরাপদ আশ্রয়’ পেলেন। সেখানে তিনি ‘সৈন্য সংগ্রহ’ করে আবার লুটতরাজের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু এবারে রাণীর সৈন্যরা তাঁকে পাকড়াও করে ঝাঁসীর দুর্গে ‘বন্দী’ করে নিয়ে যায়।
‘জব্বলপুর বিভাগের কমিশনার’ রাণীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘ব্রিটিশ সৈন্য না আসা পর্যন্ত ঝাঁসীর শাসন এবং প্রতিরক্ষার ভার গ্রহণ করতে’। তিনি ‘অনুগতভাবে’ এ কর্তব্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখতে পেলেন বিদ্রোহী সেপাইরা নয়, ‘ব্রিটিশের অনুগত ধুন্দেলা’রাই তাঁর রাজ্য পূর্ব হতে পশ্চিমে আক্রমণ করেছে এবং দুর্গকে বিপন্ন করে তুলেছে। তিনি বারবার ‘সাহায্যের আহ্বান’ করে ব্যর্থ হলেন। এই ‘প্রতিভাময়ী রমণী’ কিছুতেই ‘ওরচা’ এবং ‘দাতিয়া’র হাতে পরাজয় মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করলেন, কামান তৈরি করালেন। তাঁর সৈন্যরা ‘মুরানীপুর’ এবং ‘বারওয়া সাগারে’ শত্রুদের দু’দুবার পরাজিত করল। ‘নাথে খান’ পরাজিত হল বটে, কিন্তু রাণীও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে অনেক ‘বিদ্রোহী সেপাই’ চাকুরি গ্রহণ করেছিল। তাঁর মিত্রদের মধ্যে ‘বনপুর’ এবং ‘শাহ্পুরের রাজা’ সশস্ত্র বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অধীন সামন্তেরা বিজয়ের স্বাদ পেয়ে ‘অধিকতর বড় যুদ্ধ করার বাসনা’ পোষণ করতে লাগলেন।
১৮৫৮ সালের ৮ই জানুয়ারি তারিখের একটি সংবাদে জানা যায় যে ‘জেল দারোগা করিম বখশ’ রাণীর কাছে লিখে পাঠিয়ে জানতে চান যে, তিনি ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজী আছেন কিনা? উত্তরে রাণী জানিয়েছিলেন – তিনি ইংরেজদের সঙ্গে ‘যুদ্ধ’ করবেন না, ইংরেজ সেনাবাহিনী এসে পৌঁছেলে তাঁর অধীনে যতগুলো জেলা আছে, সবগুলোর কর্তৃত্বভার তিনি ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেবেন। ২৬শে জানুয়ারি তারিখে খবর পাওয়া যায়, রাণী তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ‘মুরানীপুরে’ ‘ওরচার’ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছেন। তারপর তিনি ‘কমিশনারের কাছে’ একজন ‘প্রতিনিধি’ প্রেরণ করলেন, বললেন – যদি প্রতিনিধিকে সসম্মানে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে ‘যুদ্ধ’ করবেন না; পক্ষান্তরে ব্রিটিশ অফিসারেরা তাঁর সঙ্গে ‘বিরূপ ব্যবহার’ করলে তিনি যুদ্ধ করবেন। ‘বন্দুক’ এবং ‘বারুদ’ প্রস্তুত হতে লাগলো। ফেব্রুয়ারি মাসেও রাণী যুদ্ধ করতে ‘প্রস্তুত’ ছিলেন না। যদিও তাঁর ‘প্রস্তুতি চলছিল’। মার্চ মাসে তাঁর সভাসদদের মধ্যে ‘মতদ্বৈধতা’ দেখা দেয়। কিছু সংখ্যক সভাসদ ‘ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি’ করতে মত দেন এবং কিছু সংখ্যক সভাসদ রাণীকে ‘যুদ্ধ’ করে যাওয়ার জন্য ‘প্ররোচিত’ করেন।
জানা যায়, সেই সময় ‘শাহজাদা ফিরোজ শাহ্’ ঝাঁসীতে অবস্থান করছিলেন। আরেক সংবাদে জানা যায়, ‘তাঁতিয়া টোপী’ রাণীকে ইংরেজদের সঙ্গে ‘সন্ধি’ করতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু এ সকল সংবাদের কোনো ‘ঐতিহাসিক ভিত্তি’ নেই। জানুয়ারি মাসে তিনি ‘ব্রিটিশ উদাসীনতা’র কারণে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন, ফেব্রুয়ারি মাসে পরিস্থিতি অনুসারে ‘নিজের পথ অনুসরণ’ করেছিলেন, মার্চ মাসে কিছু কিছু সংবাদ ‘মারমুখী নীতি’ গ্রহণের জন্য রাণীকে প্ররোচিত করে। তিনি পুরনো ব্রিটিশ সেপাইদের সেনাদলে ভর্তি শুরু করেন। তাঁরা ছিল যুদ্ধের জন্য। শান্তির সময়ে তাঁরা অহেতুক অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে যাই হোক, তিনি অতি সাবধানতার সাথে ব্রিটিশ গতিবিধি ‘নিরীক্ষণ’ করে আসছিলেন। জানুয়ারিতে যে ‘প্রত্যাশা’ ছিলো, মার্চ মাসে তা ‘অবসিত’ হয়ে এলো। ততদিনে ‘স্যর হাফরোজ’ ঝাঁসীর দিকে রওনা দিয়েছেন। তাঁর হাবভাব ‘বন্ধুসুলভ’ বলে মনে হচ্ছিল না।
শুধু সামরিক বিভাগেই স্যার হাফরোজের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিলনা। তিনি কুটনীতিবিদ হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ২০ বছর চাকুরি করে তিনি ‘লেফটেন্যান্ট কর্ণেলের পদে’ উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি ‘ক্রিমিয়ার যুদ্ধে’ও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পুনা বিভাগের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। ‘বুন্দেলার সদার’দের নিরপেক্ষ বোধ করায় তিনি ‘সাগারে’ অভিযান করতে মনস্থ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা করেন। বিদ্রোহীরা ‘রাহাতগড়ে’ তাঁকে বাধা দেয়। ‘বনপুরের বুন্দেলা রাজা মর্দান সিং’ সেপাইদের সংগ্রামের প্রতি ‘সহানুভূতিসম্পন্ন’ ছিলেন না। কিন্তু তিনি দেখলেন যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলে তিনি ‘হৃতরাজ্য উদ্ধার’ করতে পারবেন এবং স্থানীয় ঠাকুরদের সহায়তায় ঐতিহাসিক দুর্গ অধিকার করতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ‘স্যর হাফরোজ’ সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করেও রাহাতগড়ের অবরোধ ভেদ করতে সক্ষম হলেন না। তারপর বিদ্রোহীরা ‘বীনার ববদিয়া’ নামক স্থানে চলে যায়। দৃঢ়চিত্তে আফগান এবং পাঠানদের অল্পসংখ্যক সৈন্য প্রাণপণ বিক্রমে দুর্গ প্রতিরক্ষা করেন। কিন্তু তাঁদের দলপতি যুদ্ধে প্রাণ হারান, আবার এদিকে বনপুরের রাজাও যুদ্ধে আহত হন। ফলে বিদ্রোহীরা সে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখে ‘স্যার হাফরোজ’ ‘সাগার’-এর কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন। ‘গারাকোটা’কে মুক্ত করে ‘স্যার হাফরোজ’ ‘ঝাঁসী’র দিকে অভিযান করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। কিন্তু যানবাহনের অভাবে তাঁর যাত্রা দু’দিনের জন্য ‘স্থগিত’ রাখতে হল। তাঁর ‘পরবর্তী কর্মসূচি’ গ্রহণ করার আগে ‘স্যার হাফরোজ’ সেনাবাহিনীর প্রত্যেক শাখার উন্নয়ন সাধন করেছিলেন। ‘স্যার হাফরোজ’ পেছনের দিক দিয়ে ‘চাখারী’ হয়ে ‘কল্পি’তে গিয়ে সেখান থেকে ‘ঝাঁসী’তে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কেননা ‘কল্পির রাজা’ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের একেবারে ‘গোঁড়া সমর্থক’। একা তাঁর সৈন্য বাহিনীর পক্ষে ঝাঁসীর দুর্গ দখল করা কষ্টসাধ্য হবে বলে ‘স্যার হাফরোজ’ মনে করেছিলেন। কিন্তু পেছনে আবার এ রকম শক্তিশালী শত্রু-দুর্গ রেখে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে তিনি মনে করেছিলেন। ২১শে মার্চ তারিখে ব্রিটিশ সৈন্য ‘ঝাঁসী’তে এসে উপনীত হয়। এ সময়ে স্যার হাফরোজের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন ‘ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্ট’।
‘ঝাঁসী’ থেকে কয়েক মাইল দূরে থাকতেই স্যার হাফরোজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল। এর আগে কানপুরের পরাজয় ‘তাতিয়া টোপী’কে নিরস্ত করতে পারেনি। তিনি পেছন দিক নিয়ে ক্ষুদ্র বুন্দেলা রাজ্যের ক্ষুদ্র রাজধানী আক্রমণ করে বসলেন। রাজা অসহায়ভাবে ব্রিটিশ সেনাপতির কাছে ‘সাহায্যের জন্য আবেদন’ জানালেন। সুতরাং হাফরোজ তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে প্রথমে বুন্দেলার রাজাকে রক্ষা করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু সেখানে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না বুঝে, অতঃপর তিনি ঝাঁসীর দিকে একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।
২২শে মার্চ তারিখে ঝাঁসী অবরোধ করা হয়। ২৫ তারিখে কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। ঝাঁসীর নগরবাসীরাও কামানের গোলা আর বন্দুকের গুলী দিয়ে শত্রুদের অভ্যর্থনা শুরু করল। মহিলারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সন্ধ্যাবেলা তাঁর সৈন্যদের ‘অনুপ্রাণিত’ করার জন্য রাণী নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। তিনি বাইরের সাহায্যের প্রত্যাশা করছিলেন। সেই সাহায্যের আসতে বেশি সময়ের দরকার হল না। ৩১শে মার্চ তারিখে ‘তাঁতিয়া টোপী’র পরিচালনাধীন ২০ হাজার সৈন্য ঝাঁসীতে এলো। ‘স্যার হাফরোজ’ কিছু সৈন্য নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ‘তাঁতিয়া টোপী’র সৈন্যবাহিনীকে হটিয়ে দিলেন।
‘তাঁতিয়া টোপী’কে পরাজিত করে ‘স্যার হাফরোজ’ সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁসী আক্রমণ করলেন। ‘তাঁতিয়া টোপী’র সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবনের ফলে রাণীর সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিলো কিনা বলা যায় না। ৩রা এপ্রিল তারিখে তাঁরা শত্রুর ওপর ‘প্রবল অগ্নিবৃষ্টি’ শুরু করলো। ‘ঘটি’, ‘বাটি’, ‘বঁটি’, ‘দা’, ‘কুড়াল’ হাতের কাছে যা পেলো শত্রুর প্রতি ছুঁড়ে মারতে লাগলো। অবশেষে নগরীর ফটক ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল এবং ব্রিটিশ সৈন্য দ্রুতবেগে ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করল। কিন্তু একটি ‘বিরাট পাথরখণ্ড’ ব্রিটিশ বাহিনীর প্রবেশের মুখে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আরেকটি দল, দুর্গ প্রাচীরের ছোট্ট একটি ফাটল দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে যায়। ফলে যুদ্ধ শহরের রাজপথে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্গ প্রতিরক্ষাকারীরা প্রতিটি স্থানে বীরবিক্রমে লড়ে যাচ্ছিল। বিনা যুদ্ধে এক পা অগ্রসর হবারও উপায় ছিলনা। শত্রুরা প্রতিটি কক্ষে হামলা চালায়। কিন্তু সঙ্গিনের মুখে তাঁদের পালিয়ে আসতে হয়। এত প্রতিরোধ সত্বেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সৈন্যের দখলে চলে আসে প্রাসাদ। তখনও রাণীর ৪০জন ‘দেহরক্ষী’ বীর বিক্রমে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় তাঁদের কিছু সংখ্যক একটি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে। কক্ষের দরজা বন্ধ করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে দগ্ধ হয়ে তাঁদের মৃত্যু ঘটে। পরের দিন প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে ‘ভস্মীভূত’ না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে যুদ্ধ চলেছিল। প্রত্যেক ‘ভারতীয়’কে, সে যুদ্ধ করুক বা না করুক ‘শত্রু’ বলে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। যাঁরা পালিয়ে যেতে ‘সক্ষম’ হল না তাঁরা কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে ‘আত্মহত্যা’ করেছিল।
ব্রিটিশ সৈন্যদের ‘প্রবল আক্রোশ’ ছিলো রাণীর উপরে। কিন্তু তিনি রাতের অন্ধকারে পুরুষের বেশে পালক পুত্রসহ পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর সঙ্গী ছিল একদল ‘আফগান রক্ষী’। ‘ওরচা প্রহরী’দের দৃষ্টিকে তাঁরা ফাঁকি দিয়েছিল। কিন্তু সকাল হবার পূর্বে তাঁরা আরেকটি ঘাঁটির সম্মুখীন হন। তাঁর রক্ষীবৃন্দসহ রাণী ‘কল্পি’র দিকে অশ্বারোহণে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ‘বাবা’ ‘মহরাপন্থ তসবে’ পথ হারিয়ে ফেলেন এবং ধৃত হন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঝাঁসীতে পাঠিয়ে দেওয়া হলে জোখনবাগে তাঁকে ‘শূলে’ চড়ানো হয়। অশ্বারোহণে রাণী একরাতে ২১ মাইল পথ অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ‘অন্তর্ধানের সংবাদ’ ব্রিটিশ সৈন্যদের কাছে রাত পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। সকালে খবর পাওয়া মাত্র ‘ক্যাপটেন ফর্বস’ এবং ‘লেফটেন্যান্ট ডকার’কে ‘৩১নং হাল্কা অশ্বারোহী বাহিনী’ এবং ‘১৪নং পল্টন’ সহ তাঁর পিছনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাণীর পলায়নের পথ সুগম করতে এই বাহিনীর সামনে প্রাচীরের মতন বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর সঙ্গী আফগান রক্ষীরা। ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে প্রবল ও অসম যুদ্ধে তাঁরা প্রাণ দেন। রাণী ছিলেন সুদক্ষা অশ্বারোহী। ব্রিটিশ অনুসরণকারীদের সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিটি, যিনি যুদ্ধ এড়িয়ে রাণীর কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছিলেন, তিনি রাণীর গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হন। রাণী নিরাপদে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।
‘ঝাঁসী’র পতন হয়। কিন্তু পেশোয়ার সৈন্যের সদর দফতর ‘কল্পি’ তখনো বিদ্রোহীদের হাতে ছিল। সেখানে বিদ্রোহী নেতাদের সভা বসেছিল। ‘রাও সাহেব’, ‘বান্দার নবাব’ এবং ‘ঝাঁসীর রাণী’ এক সঙ্গে সেই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। এরপরে ‘রাও সাহেব’, ‘বান্দার নবাব’ এবং ‘ঝাঁসীর রাণী’ একসঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু ২৩ তারিখের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বাধ্য হয়ে তাঁদেরকে ‘কল্পি’ও ছাড়তে হয়। ‘কল্পি’র পতনের পর বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ পুনরায় এক সভা আহ্বান করেছিলেন। সেখানে সেপাইদের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি।
শেষে ১৮৫৮ সালের ১৮ই জুন, ‘ব্রিগেডিয়ার স্মিথ’ যখন ‘কোটালকী সরাই’ থেকে গোয়ালীয়রের সেপাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন তখন ‘ঝাঁসীর রাণী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই’ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ প্রসঙ্গে দু’টি কাহিনী প্রচলিত আছে।
‘ম্যাকফারসান’ লিখে গিয়েছেন, ‘‘ফুলবাগ কামানের কাছে আমি দেখতে পেলাম ঝাঁসীর রাণী নিথর হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর শরীরে প্রাণ স্পন্দনের চিহ্ন নেই। তাঁর চাকর জানাল তিনি সেখানে বসে সুরা পান করছিলেন। নিকটে ছিলো চারশোর মতো অনিয়মিত সেপাই। ব্রিটিশ সৈন্য আসছে বলে যখন ডঙ্কা বাজিয়ে দেওয়া হল, পনেরো জন ছাড়া আর সকলেই পালিয়ে গেল। রাণীর ঘোড়া লাফ দিয়ে খাল অতিক্রম করতে পারল না। তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর মাথায় চোট লেগেছিলো। তারপরে ঘোড়া থেকে ঢলে পড়ে গেলেন এবং নিকটস্থ বাগানে তাঁকে দাহ করা হয়।’’
কিন্তু ‘স্যার রবার্ট হ্যামিল্টন’ এ প্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন তা একটু ভিন্নতর। তাঁর বর্ণনায় প্রবল যুদ্ধের পরে রাণী মাথায় আঘাত পেয়ে প্রাণ দেন এবং নিকটস্থ বাগানে তাঁকে দাহ করা হয়।
দুটো বর্ণনার কোনটা ঠিক তা আজও জানা যায়নি।
সে যাক, যেভাইে জীবনাবসান ঘটুক না কেন, তিনি প্রকৃত বিক্রমশালী বীরাঙ্গনার মতো মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ব্রিটিশ সৈন্য তাঁর মতো আর কাউকে অমন ‘ঘৃণা’ করেনি। ‘শৌর্যে-বীর্যে’, ‘ক্ষিপ্রতায়’ এ রকম উদ্দীপনা সঞ্চারী মহিলা পৃথিবীর ইতিহাসে অধিক দেখা যায় না।
(তথ্যসূত্র:
১- Rani Lakshmibai: The Valiant Queen of Jhanshi, Deepa Agarwal, Puffin Books.
২- সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আহমদ ছফা।
৩- ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, প্রমোদ সেনগুপ্ত, সুবর্ণরেখা।)
মতামত লেখকের ব্যক্তিগত