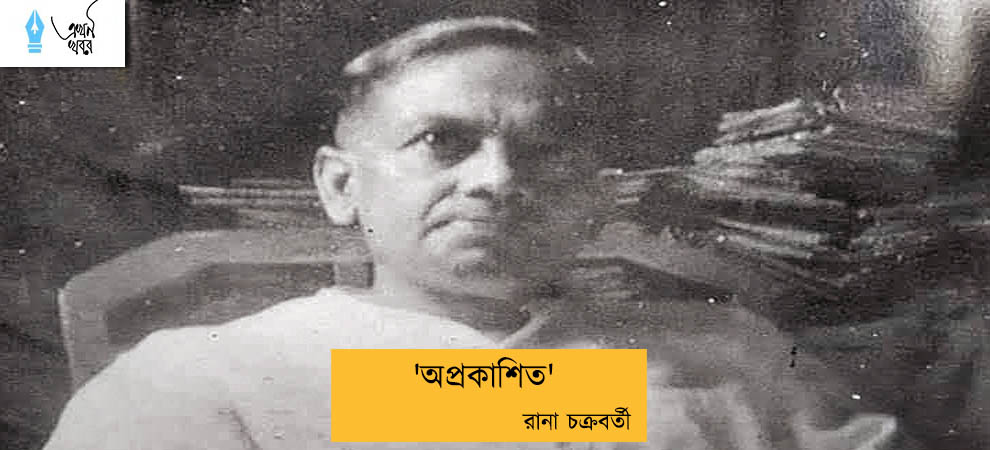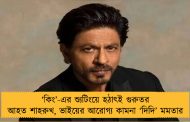তাঁর মৃত্যুর পরই উদ্ধার হয়েছে তাঁর অধিকাংশ রচনা। সে সব নিয়ে খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু দিন হল। তা হলে এতগুলি না ছাপা কবিতায় ভরা আস্ত একখানা খাতা কোথায় লুকিয়েছিল এত দিন? আর কী ভাবেই বা পাওয়া গেল তা?
বাঙালি পাঠকের কাছে সেই উৎস সন্ধানের সূত্র কিছু কম রোমাঞ্চকর নয়।
গৌতম মিত্র। পেশায় ব্যাঙ্ককর্মী। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে কলকাতার পথে পথে অমূল্য রতনের খোঁজে ছাই ওড়ানোই ছিল যাঁর একমাত্র কাজ। জীবনানন্দের ডাইরি ও অন্যান্য রচনা উদ্ধারের কাজ যখন পুরোদমে চলেছে, সেই সময় ভূমেন্দ্র গুহর পাশাপাশি গৌতম মিত্রও এই অসাধ্যসাধনে নাম লিখিয়েছিলেন। জীবনানন্দ সংক্রান্ত যেখানে যেটুকু সঙ্কেত বা সূত্র, সেখানেই ছুটে যাওয়া ছিল তাঁর কাজ।
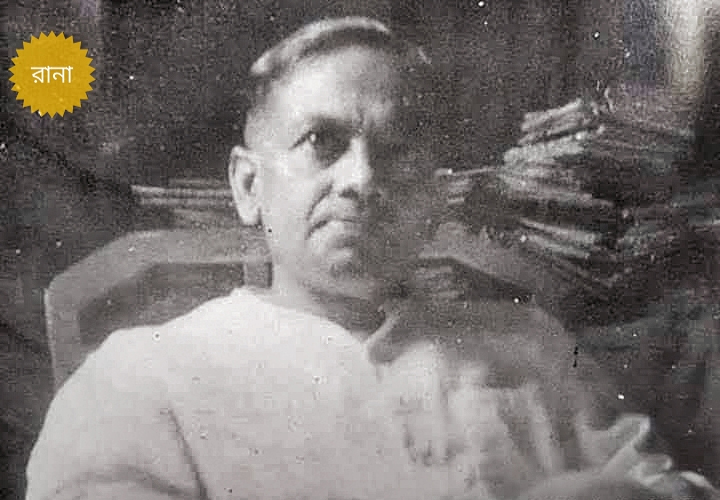
এই রকমই একটি সূত্রের নাম অশোকচন্দ্র গুপ্ত। জীবনানন্দ দাশ তাঁর ডাইরিতে বন্ধু হিসেবে বারবার উল্লেখ করেছেন এই মানুষটির। বরিশালের সর্বানন্দ ভবনে থাকাকালীন এই অশোক চন্দ্র গুপ্তের পরিবারের সঙ্গে জীবনানন্দের পরিবারের হৃদ্যতার কথাও তাঁর ডাইরিতে পাওয়া যায়। ১৯৪৬ সালে জীবনানন্দ পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে আসেন, তত দিনে অশোক চন্দ্র গুপ্তও সপরিবার কলকাতায়। এই শহরে এসেও তাঁদের বন্ধুত্ব ও যোগাযোগ ছিল অটুট। এমনিতে জীবনানন্দ যে খুবই মুখচোরা ও নির্জন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তা আজ সুবিদিত। এ হেন মানুষ যখন বারবার বন্ধু হিসেবে কারও উল্লেখ করেন, তখন তার গুরুত্ব অন্য রকম হয়ে দাঁড়ায়।
২০০১ নাগাদ গৌতমবাবু ক্রমাগত জাতীয় গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যাতায়াত করেছিলেন, জীবনানন্দ সংক্রান্ত আরও কিছু সূত্রের আশায়। কারণ জীবনানন্দের ডাইরি বলছিল, বহু অপ্রকাশিত লেখা এখনও আছে কোথাও। কিন্তু কোথায়?
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেই মিলল উত্তর। ব্রহ্মবাদী পত্রিকার একটি সংখ্যায় (যা এক সময় জীবনানন্দ দাশের বাবা সত্যানন্দ দাশ সম্পাদনা করতেন) পাওয়া গেল অশোক চন্দ্র গুপ্তের কন্যাসন্তান লাভের খবর। হয়তো কোনও হদিশ মিললেও মিলতে পারে, এই ভেবেই অশোকচন্দ্রের সেই কন্যাসন্তানের খোঁজে বেরোলেন গৌতমবাবু। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে ডোভার রোডের একটি বাড়িতে পাওয়া গেল তাঁকে। রত্না রায়, যাঁর বয়স তখন ষাট পেরিয়ে গিয়েছে। জীবনানন্দের স্মৃতি তাঁর কাছে স্পষ্ট। যেমন স্পষ্ট তাঁর বাবার সঙ্গে কবির বিরল হৃদ্যতা। সেই সখ্যের ভরসাতেই, জীবনানন্দর মৃত্যুর পর তাঁর গদ্য ও ডাইরিধর্মী অপ্রকাশিত লেখালেখি ভর্তি একটি ট্রাঙ্ক অশোকচন্দ্র গুপ্তের পরিবারের কাছে রেখে গিয়েছিলেন কবিকন্যা মঞ্জুশ্রী দাশ। পরে জীবনান্দের ভ্রাতুষ্পুত্র অমিতানন্দ দাশ সেই ট্রাঙ্ক থেকে লেখাগুলো উদ্ধার করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। জীবনানন্দ সংক্রান্ত আরও তথ্য ও স্মৃতির আশায় রত্নাদেবীর বাড়িতে যাতায়াত তৈরি হল গৌতমবাবুর, পাশাপাশি তৈরি হল বিশ্বাসযোগ্যতার এক সম্পর্কও। কেবলমাত্র সেই সম্পর্কের খাতিরেই রত্নাদেবী একদিন আড্ডার ছলে এমন এক কথা বললেন, বাংলা সাহিত্যের জগতে যা বিস্ফোরণের চাইতেও বেশি। জীবনানন্দ দাশের হস্তাক্ষরে লিখিত অপ্রকাশিত কবিতা ভর্তি একটি খাতা আছে রত্নাদেবীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে। তাঁর বক্তব্য ছিল, স্বয়ং জীবনানন্দ দাশ এই খাতাটি তাঁর পরিবারের হেফাজতে রেখেছিলেন। সেই থেকে সেই ভাবেই আছে।
এখানে প্রশ্ন ওঠে, স্বভাবে নির্জন সেই মানুষটি এক-খাতা কবিতা কেনই বা দিয়েছিলেন বন্ধুর হেফাজতে? তাঁর কাছে তাঁর লেখাই ছিল একমাত্র সম্পদ। সেই সম্পদ নিজের কাছে না রাখার কী কারণ থাকতে পারে?
এমন আরও প্রশ্ন নিশ্চয়ই ভিড় করে। কিন্তু এই সব প্রশ্নের উত্তর জানার উপায় হয়তো নেই। তবে সেই সম্পদ যে শেষমেশ পাঠককুলের হাতে পৌঁছেছিল সেটাই বড় কথা। পৌঁছেছিল কারণ শুধুমাত্র ভরসার খাতিরেই সেই খাতা গৌতম মিত্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন রত্নাদেবী। সেটা ২০০৪। এই মহাভাণ্ডার হস্তান্তরের খবর জানতেন কেবল তাঁরা দু’ জনেই। তার পর ১০ বছর শ্রীমিত্র অপেক্ষা করেছিলেন স্বত্ব আইনের খাতিরে। আইনি বাধা উঠে যাওয়ার পর খাতাটি নিয়ে তিনি হাজির হন সপ্তর্ষি প্রকাশনের দফতরে। যার ফল? কলকাতা বইমেলায় পাওয়া গিয়েছিল গ্রন্থ। নাম ‘অপ্রকাশিত’।
২৩শে জানুয়ারি ২০১৬ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার একটি প্রবন্ধে শ্রী গৌতম মিত্র নিজেই জানিয়েছিলেন তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা, নিম্নরূপে –
“একটি ট্রাঙ্ককে জীবনানন্দ দাশ বুকে করে আগলে বেড়িয়েছেন চিরটাকাল!
’৪৬-’৪৭ সালে যখন বরিশাল থেকে একেবারে স্থায়িভাবে কলকাতা চলে আসেন কবি, অনেক অমূল্য জিনিসপত্র ফেলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু সেই ট্রাঙ্কটি তিনি ছাড়েননি।
জীবনানন্দ সম্পর্কিত বহু লেখায়, সাক্ষাৎকারে ওই ট্রাঙ্কটির কথা পাওয়া যায়। অনেকেই বর্ণনা করেছেন একটি সাধারণ দৃশ্য।— কবি ট্রাঙ্কটি খুলে বসে আছেন। কাগজ বার করে এক মনে কী যেন দেখে চলেছেন। কেউ এলেই মুহূর্তে সে-সব আড়াল করছেন। এমনকী স্ত্রীকেও তাই।
কী ছিল সেই ট্রাঙ্কে?
বহু নথি, লেখালেখি থেকে যেটুকু জানা যায়, তা’ হল, প্রায় আড়াই হাজার কবিতার পাণ্ডুলিপি, একুশটি উপন্যাস, একশো আঠাশটি গল্প, আটাত্তরটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ-ব্যক্তিগত রচনা। প্রায় ছাপ্পান্নটি খাতায় ঠাসা প্রায় সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠার ‘লিটারারি নোটস’ নামাঙ্কিত ডায়েরিধর্মী রচনা। চিঠি প্রায় শ’য়েরও বেশি। শোনা যায়, এই পাণ্ডুলিপির জন্যই বারবার আত্মহত্যার পরিকল্পনা বাতিল করেছিলেন কবি।
এটুকু জানাই ছিল।
তাঁর কবিতা সংগ্রহের কাজে হাত দিয়ে কোথায় যেন একটা বড়সড় গরমিল খুঁজে পেলাম।
তখনই মনে হয়েছিল, জাতীয় গ্রন্থাগারে রাখা জীবনানন্দ দাশের পাণ্ডুলিপি একবার দেখে নেওয়া প্রয়োজন। অনুমতি মিলল গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৪৮টি খাতা দেখার। তাতে লেখা প্রতিটি কবিতার প্রথম লাইন প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে মনে হল, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কবিতা অপ্রকাশিত! এ বার সন্দেহ হল, এই ৪৮টি খাতার বাইরেও কবিতার পাণ্ডুলিপি আরও কোথাও নিশ্চয়ই থেকে গেছে। তার প্রধান কারণ, প্রকাশিত অনেক কবিতার পাণ্ডুলিপি ওই খাতাগুলির মধ্যে নেই।
বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারি কবিকন্যা মঞ্জুশ্রী দাশ অনেক খাতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এর পরেও তাঁর কাছে যাও’বা ছিল, তা রক্ষা করেছেন কোনও এক সহৃদয় মহিলা। সেগুলি তিনি আবার কবির ভাই অশোকানন্দ দাশের পুত্র অমিতানন্দ দাশকে যথাসময়ে ফিরিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই মহিলার পরিচয় জানা ছিল না।
জীবনানন্দ দাশের ডায়েরিতে জনৈক অশোক নামটি পাওয়া গেল। এই অশোক যে বন্ধুস্থানীয় কেউ, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি।
হঠাৎই ‘ব্রহ্মবাদী পত্রিকা’র একটি খবর আমার চোখে পড়ে যায়। পত্রিকাটি বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র। এখানেই জীবনানন্দের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন জীবনানন্দ দাশের বাবা সত্যানন্দ দাশ।
পত্রিকার সেই খবরটি লিখছে, ১৯ বৈশাখ ১১৩৯ বঙ্গাব্দে রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাশের তৃতীয় কন্যা সলিলার সঙ্গে বরিশালের ব্রাহ্মবন্ধু বিনয়ভূষণ গুপ্তের পুত্র অশোকচন্দ্রের শুভ বিবাহ।
এর পর বহু কষ্টে বিনয় গুপ্তের সেই পুত্রবধূর সঙ্গে জীবনানন্দ-পরিবারের একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া গেল। এও জানা গেল, বিনয়ভূষণ এবং তাঁর দুই ভাই নলিনীভূষণ ও ইন্দুভূষণের সঙ্গে দাশ-পরিবারের হৃদ্যতা ছিল। কবির ঠাকুরদা সর্বানন্দ দাশের মৃত্যুর পর দাশ পরিবারকে অকৃতদার নলিনীভূষণ নানা ভাবে সাহায্যও করেন।
শুরু হল খোঁজ। কিন্তু তখনও অশোকচন্দ্র গুপ্তর কোনও উত্তরাধিকারের খবর আমার কাছে ছিল না।
কথা চলতে লাগল কবির পরিবার বা তাঁদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা মানুষজনের সঙ্গে। আর তাতেই হদিশ মিলল অশোকচন্দ্র গুপ্তর কন্যা শ্রীমতী রত্না রায়ের। শোনা গেল, কবির মতোই প্রায় একই সময়ে অশোকচন্দ্র গুপ্তও সপরিবার বরিশাল থেকে চলে আসেন কলকাতায়। তাঁদের যোগাযোগ ছিল অটুট।
এক গোধূলিবেলায় হাজির হলাম শ্রীমতী রত্না রায়ের বাড়ি। ঝোলায় তাঁর বাবা-মায়ের বিবাহের খবর সংবলিত ‘ব্রহ্মবাদী’ পত্রিকার কপি। নানান কথার মাঝে রত্নাদেবী জানালেন, প্রাণে ধরে জীবনানন্দ দাশের কিছু খাতা তিনি কাউকে দিতে পারেননি। মঞ্জুশ্রী দাশের কিছু খামখেয়ালির কথাও তিনি বললেন। যে জন্য কবির বহু পাণ্ডুলিপি কোথায় যে হারিয়ে গেছে, কে জানে!
শুধুমাত্র কবির বরিশালের কথা শোনার আগ্রহে আমার যাতায়াত শুরু হল রত্নাদেবীর ডোভার লেনের বাড়িতে। তেমনই একদিন আবার কবির সেই খাতাগুলির প্রসঙ্গে উঠল। এর পর হঠাৎই দেখি, নিজের থেকে উঠে গিয়ে খাতাগুলি নিয়ে এলেন তিনি। আর জীবনানন্দের কবিতা উদ্ধারের কাজ হচ্ছে বলে এত দিন গচ্ছিত রাখা প্রাণভোমরাকে তুলে দিলেন তিনি আমার হাতে! সেই সংগ্রহ নিয়ে এবারে প্রকাশ পেতে চলেছে ‘অপ্রকাশিত২ জীবনানন্দ দাশ’ (সপ্তর্ষি প্রকাশন)।
রত্নাদেবী আজ আর পৃথিবীতে নেই। কিন্তু উদ্ধার-পর্বের সেই ক্লাইম্যাক্সের ছবিটা এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই। তাঁর সঙ্গে এক প্রৌঢ়ার জ্বলজ্বলে চোখের তারাগুলিও!”
তাঁর জীবনকালে জীবনানন্দের প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা দুশোর একটু বেশি, অথচ মৃত্যুর ষাট বছরে তোরঙ্গ থেকে উদ্ধার হয়েছে অসংখ্য অসূর্যম্পশ্যা কবিতা! পাতার পর পাতা থেকে সেই হস্তাক্ষর, সেই কণ্ঠস্বর, সেই শৈলী, সেই মানুষ আর তাঁর নির্জনতা ঝরে পড়ছে। তাঁর প্রিয় ইয়েটস-এর ভাষায় এও এক ‘সেকেন্ড কামিং’, ধর্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন জীবনানন্দের এক অভিনব ‘সম্ভবামি’। তবে এও সত্যি যে, কবির মরণোত্তর জীবনই ঢের বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ১৯৫৪-য় ২২শে অক্টোবর তাঁর অকাল প্রয়াণের পর। ১৯৪৮-এর মে-জুন মাসে রচিত তাঁর দুই উপন্যাস ‘মাল্যবান’ ও ‘সুতীর্থ’ প্রকাশনার আলো দেখল তাঁর মৃত্যুর পর। লেখার দু’বছরের মধ্যে এর একটি প্রকাশ পেলেও পেতে পারত, পায়নি। সেটা ১৯৫০-এ ‘পূর্বাশা’ সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা একটা চিঠিতে ধরা পড়েছে। কবি লিখছেন—
‘‘বেশি ঠেকে পড়েছি, সে জন্য বিরক্ত করতে হল আপনাকে। এখুনি চার-পাঁচশো টাকার দরকার; দয়া করে ব্যবস্থা করুন।
এই সঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি, পরে প্রবন্ধ ইত্যাদি (এখন কিছু লেখা নেই) পাঠাব। আমার একটি উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয়— ছদ্মনামে) পূর্বাশায় ছাপতে পারেন; দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি, আমার জীবনস্মৃতি আশ্বিন কিংবা কার্তিক থেকে পূর্বাশা’য় মাসে মাসে লিখব। সবই ভবিষ্যতে, কিন্তু টাকা এক্ষুনি চাই— আমাদের মতো দু-চারজন বিপদগ্রস্ত সাহিত্যিকের এ রকম দাবি গ্রাহ্য করবার মতো বিচার বিবেচনা অনেক দিন থেকে আপনারা দেখিয়ে আসছেন— সে জন্য গভীর ধন্যবাদ।’’
চিঠির ‘সবই ভবিষ্যতে’ কথাটা ব্যঞ্জনাময়। কত কিছুই যে লেখার পরিকল্পনা মাথায়, অথচ লেখা হয়ে গেছে এমন অজস্র কিছু সম্পর্কে কী নির্ভার (নাকি গুরুভার?) উদাসীনতা! তাঁর পাণ্ডুলিপির ছবি দেখলেই স্পষ্ট হয় ওঁর ওই অপরূপ মরমি পঙ্ক্তি সব কত সচেতন কাটাকুটি পেরিয়ে, প্রায় সীতার মতো অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে কবিতায় এসেছে; — তা হলে এত কিছুর পরও তারা কেন, কী ভাবে কুমারী, অন্তরালবর্তিনী রইল?
আমার কাছে অন্তত তুলনাটা আসে জগতের প্রিয় দার্শনিক ব্লেজ পাস্কাল-এর। তাঁর অমর কীর্তি ‘পঁজে’ (চিন্তা) বুকের মধ্যে নিয়ে যিনি কবরে গেলেন, এবং সেখান থেকে উদ্ধার হয়ে রচনাটি ফরাসি গদ্য ও সাহিত্যের শিরোমণি হয়ে থেকে গেল তদবধি।
এই কীর্তির পূর্বে, তাঁর জীবৎকালে, পাস্কালের অপর যে-কাজ ফরাসি গদ্য ও তর্কসাহিত্যকে শিকড় ধরে নাড়িয়ে দিয়েছিল সেই ‘লেত্র্ আ প্রোভিন্সিয়াল’-ও (প্রাদেশিক পত্রাবলি) তিনি ছেপেছিলেন বেনামে। অসহ্য শারীরিক কষ্টে কাটানো ওঁর মৃত্যুপূর্ব দিনগুলোর সঙ্গেও মিল পাই জীবনানন্দের শেষ দিনগুলোর। রোগচরিত্র ও আসন্ন মৃত্যুর কথা দার্শনিকের থেকে আড়াল রাখতেন বন্ধুবর্গ, ডাক্তারবৃন্দ। নিজের মৃত্যুর ছায়া, অভিলাষ ও পটভূমিও কি কবি জগতের থেকে আড়াল করার চেষ্টায় ছিলেন শেষ দিকে?
সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছেন: ‘‘আমার মনে হয় জীবনানন্দ ঠিক ট্রাম দুর্ঘটনায় মারা যাননি। যদিও এই কথাটাই সর্বত্র বলা হয়ে থাকে, তথাপি আমার ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন।’’
এই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতামত উল্লেখ করে জীবনানন্দের ছাত্র অরবিন্দ গুহ কবির স্মৃতিচারণায় লিখেছেন: ‘‘জীবনানন্দের মুখে শুনে তাঁর পারিবারিক ঘটনাই সঞ্জয় ভট্টাচার্য জেনেছেন, সে সব ঘটনা খুব সুখের নয়। স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিদিন জীবনানন্দের একটা দ্বন্দ্বের কথা সঞ্জয় ভট্টাচার্য অকপটে ব্যক্ত করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়েছেন যে জীবনানন্দ তার থেকে মুক্তি খুঁজছিলেন।’’
কবির গণনাতীত ভক্তের মধ্যে যাঁরা পারিবারিক এই ছবির আঁচ পাননি তাঁরাও ‘মহাপৃথিবী’ সঙ্কলনের ‘ফুটপাথে’ কবিতার এই সূচনা স্তবকের দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে পারেননি। কবি যেখানে তাঁর নিলয়যাত্রাকে প্রায় নিটোল অনুমানে এনেছেন:
‘‘ট্রামের লাইনের পথ ধরে হাঁটি: এখন গভীর রাত/কবেকার কোন্ সে জীবন যেন টিটকারি দিয়ে যায়/‘তুমি যেন রড ভাঙা ট্রাম এক— ডিপো নাই, মজুরির প্রয়োজন নাই/কখন এমন হয়ে হায়!/ আকাশে নক্ষত্রে পিছে অন্ধকারে/কবেকার কোন্ সে জীবন ডুবে যায়।’’
ট্রাম বা ট্রামলাইনও যে এক সময় রূপকালঙ্কার হয়ে ওঁর গদ্যকেও ভর করেছিল তাও ভক্তরা লক্ষ করছিলেন এমন সব বর্ণনায়:
‘‘শচী… প্রকাশের বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল; এই শীতের ভেতরেও প্রকাশের কপাল ঘামিয়ে উঠেছে— আঁচল দিয়ে আস্তে আস্তে স্বামীর কপাল মুছে ফেলে শচী দরজা জানালাগুলো সব খুলে দিল। বড় রাস্তাটার দিকের জানালাটার পাশে এসে রাতের কলকাতার দিকে একবার তাকাল সে— ট্রামলাইনগুলো খালি পড়ে আছে— রাস্তার সেই বিরাট হাঙরদের এখন ঘুমোবার সময়।’’ (গ্রাম ও শহরের গল্প)
এই যে ভক্তদের কথা বলছি, এঁদের একজন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যিনি উঠতি যৌবনে পুরনো বইয়ের দোকান থেকে চার আনায় এক কপি ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কিনে বোধ করেছিলেন কে যেন দু-চোখে ঘুসি মারল! লিখছেন—
‘‘আমি পাগলের মতন জীবনানন্দ দাশের ভক্ত হয়ে গেলাম। ভক্ত কিংবা ক্রীতদাসও বলা যেতে পারে।’’
এই ভক্ত কিংবা ক্রীতদাস কবির শেষ যাত্রার নাতিদীর্ঘ মিছিলে ছিলেন। লিখেছেন, ‘‘শবানুগমনে খুব বেশি লোক হয়নি। আমাদের অল্পবয়সি কাঁধ বেশ শক্ত, আমরা কয়েকজন কাঁধ দিয়েছিলাম পাল্লা করে। জীবনে একবারই মাত্র সেই কবির শরীর স্পর্শ করেছি, তখন নিস্পন্দ।’’
সেই শবযাত্রায় সাক্ষী অরবিন্দ গুহ নজর করেছিলেন যে, ‘‘শ্মশানের পথে পড়ল সেই জায়গাটা, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, ট্রামলাইনের সেই জায়গা জুড়ে সবুজ ঘাস— আশ্চর্য, শানবাঁধা কলকাতায় জীবনানন্দের জীবনের চরম দুর্ঘটনা এমন জায়গাতেই ঘটল যেখানে ঘাস, ঘাস— যে ঘাসের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রগাঢ়, প্রবল।
আর মৃত্যু হল যখন, কোন তারিখ? রাত্রি ১১টা ৩৫মি। ৫ কার্তিক।’’
এই কার্তিকের রাত্রির সংযোগটাও আশ্চর্য করেছিল অরবিন্দকে, যাঁর মামাবাড়ি ছিল বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলের কাছে। যে-ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্র ছিলেন জীবনানন্দ; পরে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপকও, অরবিন্দ লিখছেন:
‘‘লক্ষ্মীপুজোর নেমন্তন্ন থাকত মামাবাড়িতে। নেমন্তন্ন সেরে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যেত। কোজাগরি পূর্ণিমার রাত। একাধিকবার দেখেছি, স্কুলের মস্ত মাঠ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে, মন্তাজ মিঞার আস্তাবলের কয়েকটি ঘোড়া জ্যোৎস্নার মাঠে ঘাস খাচ্ছে। বহু কাল পরে জীবনানন্দের ‘ঘো়ড়া’ নামক একটি বিখ্যাত কবিতায় পড়েছি— ‘মহিনের ঘোড়াগুলি ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে/প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন— এখনও ঘাসের লোভে চরে/পৃথিবীর কিমাকার ডাইনোসর ’পরে।…‘ঘোড়া’ কবিতাটি পড়ে আমি অনেক দিন ভেবেছি— জীবনানন্দ কি কোনও দিন ওই জ্যোৎস্নার মাঠে স্বচক্ষে মন্তাজ মিঞার আস্তাবলের ঘোড়াদের ঘাস খেতে দেখেছেন?’’
অরবিন্দ ভাবেননি, তবে ভাবতেও পারতেন, শেষ আশ্বিনের ওই ভয়ানক সন্ধ্যার অপঘাতও কি জীবনানন্দ মনশ্চক্ষে দেখেছিলেন কখনও? কিংবা আধোঅচেতন অনুরাগে অনুভব করেছিলেন, যেমনটি লিখে গেছেন ‘ফুটপাথে’ কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে…
‘‘কোন্ দিকে যেতে হবে? নিস্তব্ধ শহর কিছু জানে নাকো/ সে শুধু বিছায়ে আছে/ বিশ্বাসীর বিধাতার মতো।/ কোলে তার মুখ রাখি— বিশ্বাস করিতে চাই, তবু মনে হয়/ শহরের পথ ছেড়ে কোনও দিকে হেঁটে যদি চলে যেত আমার হৃদয়’’…।
সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে তো লিখেইছিলেন , আরও অনেককেই মৌখিক ভাবে জানিয়েছিলেন জীবনানন্দ যে তিনি আত্মজীবনীতে হাত দিতে চান। তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য আরেকটু স্বাচ্ছন্দ্যকর হলেই।
সেটা আর হয়নি। এক, শরীর ঠিক জুতে এল না। আর দুই, হঠাৎ করে এক সন্ধ্যায় বালিগঞ্জগামী ট্রামটা এসে পড়ল গায়ের ওপর।
অথচ ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ তিনি নিয়মিত ‘লিটারারি নোটস’ নামে দিনলিপি লিখে গেছেন। লিখেছেন ইংরেজিতে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি গল্পের প্লটলাইন ধরে রাখতে। মাঝে মাঝে বাংলাও মিশে গেছে ক্রমশ ডায়েরি হয়ে ওঠা খাতাগুলোয়।
জীবনানন্দের ইংরেজিতে ডায়েরি লেখা নিয়ে যাঁরা কিছুটা চমকিত সেগুলো প্রকাশ্যে আসায় আরওই চমৎকৃত হয়েছিলেন আরেকটি তথ্যে। কবি ১৯১৬-য় কবিতা লেখা শুরু করেন ইংরেজিতে!
ডায়েরির ইংরেজির স্টাইলটাকে বলা যায় টেলিগ্রাফিক। গল্পের ভাবনার বাইরে যে দিনের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় তা বড়ই মর্মান্তিক, পড়তে পড়তে মনে ভেঙে যায়। কর্মহীন জীবনের দৈনন্দিন বিড়ম্বনার ধারাবিবরণী। সদ্য বিবাহিত জীবনে সুখের অভাবেরও ইঙ্গিত এসে পড়ছে থেকে থেকে। মনে হচ্ছে এ বিবাহ না হলেই ভাল ছিল। পথে-ঘাটে কোনও মেয়েকে দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে কোনও গ্রাম্য কিশোরীর মুখ এবং উন্মনা হচ্ছেন।
কবির কষ্টের ইঙ্গিত দিতে তিনটে ছোট্ট এন্ট্রির উল্লেখ করব। ২৭. ৭. ৩১-এর পাতায় লিখছেন: দুপুরটা কাটল চাকরির আবেদন লিখে লিখে ডাকে পাঠাতে, খেলা দেখে যে একটু আরাম স্বস্তি পাব তা আর কপালে নেই: জীবন থেকে বহু কিছুই উবে গেছে।
তার পর লিখছেন: ঢ্যাঁড়শই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে। একই সঙ্গে মাধুর্য ও পরিহাস।
লিখছেন: বেজায় গরম, ঘুমনো গেল না। একবারটি চায়ের দোকান হয়ে আসতে হবে, তবে তিন পয়সার বেশি খরচের মুরোদ নেই। অভাবে থেঁতলে দিচ্ছে, ভাবছি খবরের কাগজ রাখা বন্ধ করে দেব।
এছাড়া ‘পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকুরী’ পঙ্ক্তিটির রচয়িতা ৯.৮.৩১-এর রোজনামচায় তিক্ততা ঝরিয়ে লিখছেন: চাকরি নেই, লোকে প্রশ্ন করছে, ‘বসে আছ?’:
‘‘…on ‘বসে থাকা’— বেকার কখনও বসে থাকে না: they stand and run, throb and palpitate; it is only the well-placed who have the external charm of the easychair or cushions, sofas and bed for themselves.’’
শেষ বয়সে কবি যে-আত্মজীবনীর কথা ভাবছিলেন তাতে কি দিনলিপির এত শোকশোচনার পূর্ণ বয়ান থাকত? আমরা জানি না, অনুমানও করতে পারি না, তবু একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়, এত রক্তক্ষরণ যে-হৃদয়ের, তিনিই তো লিখে রেখে গিয়েছিলেন, ‘তার স্থির প্রেমিকের নিকট’ নামের কবিতায়—
‘‘বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই— আমি বলি না তা/কারও লাভ আছে— সকলেরই— হয়তা বা ঢের/ভাদ্রের জ্বলন্ত রৌদ্রে তবু আমি দূরতর সমুদ্রের জলে/পেয়েছি ধবল শব্দ— বাতাসতাড়িত পাখিদের।’’
কবির যে দুটি বিখ্যাত বই দিয়ে বাঙালি পাঠকের সাধারণত পরিচয় ঘটে ওঁর সঙ্গে সেই ‘বনলতা সেন’ বা ‘রূপসী বাংলা’ পড়ে তাদের ধারণায় আনাও কঠিন কবির ব্যক্তিজীবনের ওঠাপড়া। অথচ নিয়তি এমন যে, এক সময় ওঁর জীবনের সঙ্গেই মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ার প্রয়োজন হয় ওঁর কবিতা। শুধু কাব্যোপভোগের জন্যই নয়, এক আধ্যাত্মিক আরাম ও দার্শনিক সুকৃতি অর্জনের জন্য। শুধু ওঁর কবিতা পড়ে এক আশ্চর্য জীবনানন্দকে জানা হয়; আর ওঁর জীবন ও কবিতা পাশাপাশি ও মিলিয়ে পড়লে এক পরমাশ্চর্য জীবনানন্দকে আবিষ্কার করে ফেলা যায়। আর এখানে তুলনাটা খুব সহজেই এসে পড়ে ওঁর প্রিয় কবি জন কিটস্-এর।
প্রকৃতি, নির্জনতা, মৃত্যু ও অন্ধকারের প্রতি দু’জনেরই স্বভাবটান। কিন্তু নক্ষত্র, আকাশ, সমুদ্র, নাবিক ও অভিযান যে ভাবে বেঁধেছে দুই কবির দুই সেরা কবিতাকে তা কলেজের প্রথম বর্ষে আবিষ্কার করে যে-হিল্লোল জেগেছিল ভেতরে সে-রোমাঞ্চ আজও ছেড়ে যায়নি অর্ধশতাব্দী পরেও।
কিটসের কবিতা ‘‘On First Looking into Chapman’s Homer’’ একটি চতুর্দশপদী, জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’ দ্বাদশ পদে ধরা। প্রথমে কিটসের প্রথম চার লাইন:
‘‘Much have I travel’d in the realms of gold,/ And many goodly states and kingdoms seen;/Round many western islands have I been/Which bards in fealty to Apollo hold.’’
এর পর জীবনানন্দের প্রথম চার পঙ্ক্তি:
‘‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,/সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে/অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে/সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;’’
এর পর জীবনানন্দের শেষ ক’টি পঙ্ক্তি:
‘‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,/ মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতি দূর সমুদ্রের পর/হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা/সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর/ তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, ‘এত দিন কোথায় ছিলেন?’/ পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।’’
এ বার কিটসের সেই শেষ কটা অবিস্মরণীয় লাইন:
‘‘Then felt I like some watcher of the skies/When a new planet swims into his ken;/ Or like stout Cortez when with eagle eyes/ He star’d at the Pacific— and all his men/ look’d at each other with a wild surmise— /Silent, upon a peak in Darien.’’
আত্মজীবনী লেখা না হলেও নিজের বাবা ও মা’কে নিয়ে সুন্দর একটা প্রবন্ধ রেখে গেছেন জীবনানন্দ, যার শিরোনামাটিও সরল— ‘আমার মা বাবা’।
শুরুটাও সরল— ‘‘আমার মা শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী দাশ ১৩… সালে ২১ শে পৌষ বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাঝে মাঝে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার কথা লিখে রাখতেন মনে পড়ে। তার পরে কলেজে উঠেও তাঁকে কোনো কোনো সময় তাঁর নিজ জীবন ও নানা বিষয় সম্পর্কে ধারণা ভাবনা লিখে রাখতে দেখেছি। সে সব লেখা কোথায় তিনি রেখে দিয়েছিলেন— কিংবা নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছেন কিনা কিছুই জানি না। তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা ছাড়া অন্য কোনো লেখা আমাদের কারো কাছে নেই। এখন সে সব কবিতাও খুঁজে পাচ্ছি না।’’
এই মায়ের ওপর নির্ভরতার একটা মিষ্টি ছবি আছে ছাত্রাবস্থায় হার্ডিঞ্জ হস্টেলে থেকে ওঁকে লেখা জীবনানন্দের একটি চিঠিতে। লিখছেন:
‘‘Golden Treasuryটা পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম, পাঠাইয়া দিও। আমার Hostel ও Law College-এর টাকা এখনও আসিতেছে না কেন? তা ছাড়া বইর জন্য ৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।… Paradise Regained আমাদের পাঠ্য। আগে কিনি নাই। আজকাল তো পাওয়া যাইতেছে না। জিতেন মুখার্জ্জীর বইটা থাকিতে পারে। ভুবন যদি তাহার নিকট হইতে সেই বইটা এবং Scott-এর নভেলের তিনটা (Kenilworth, Old Morality, Talisman) লইয়া আসে তাহা হইলে ভাল হয়।’’
বাবা সম্পর্কে জীবনানন্দের বিচারটা এমন ছিল:
‘‘একমাত্র জ্ঞানযোগই যে বাবার অন্নিষ্ট ছিল সে কথা সত্য নয়; কিন্তু মধ্যবয়স পেরিয়েও অনেক দিন পর্যন্ত সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান এমনকি গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চ্চায় তাঁকে প্রগাঢ় হয়ে থাকতে দেখেছি মানুষের জীবন ও চরাচর সম্বন্ধে যত দূর সম্ভব একটা বিশুদ্ধ ধারণায় পৌঁছবার জন্যে, নিজের হিসেবে পৌঁছতে পেরেছিলেন তিনি। উচ্ছ্বাস দেখিনি কখনো তাঁর, কিন্তু জীবনে অন্তঃশীল আনন্দ স্বভাবতই ছিল— সব সময়ই প্রায়। কিন্তু গদ্য লেখা ছাড়া বাবা সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেননি, কিন্তু পাঠ করেছিলেন অনেক, আলোচনার প্রসারে ও গাঢ়তায় আমাদের ভাবতে শিখিয়েছিলেন— দৃষ্টি তিনিই খুলে দিয়েছিলেন।’’
নাতিদীর্ঘ এই রচনা থেকে জীবনানন্দের চিন্তা ও চলনের উৎসমুখ শনাক্ত করা অসুবিধের না। এই প্রবন্ধ এবং ‘লেখার কথা’, ‘কেন লিখি’, ‘কবিতা সম্পর্কে’ শীর্ষক রচনাত্রয়ী এবং ওঁর চিঠিপত্র, দিনলিপি ও কবিতার বইগুলো মিলিয়ে পড়লে কবির একটা আত্মজীবনী পড়া হয়ে ওঠে।
বোন সুচরিতা দাশের বিবরণে জানা যাচ্ছে কী ‘ভীষণতম হিংস্র দুর্দিন’ ঘনিয়ে আসায় সাধের বরিশাল ছাড়তে হয়েছিল কবিকে। কিন্তু তাতেও তাঁর ‘এষণাশক্তি, ভাবনাপ্রতিভা, mother wit’ (কথাগুলো কবির থেকেই নেওয়া) বিস্রস্ত হয়নি এতটুকু।
সুচরিতা লিখছেন: ‘‘বাইরে থেকে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা তাঁকে গম্ভীর নির্জন, স্বপ্নালোকবাসী বলেছেন, বলেছেন সর্বক্ষণ একটা অদৃশ্য বেষ্টনী তৈরি করে তাঁর নিজের চারিদিকে তিনি সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন। …
যে মানুষ অত গুরুগম্ভীর কবিতা লিখতেন, তিনি যে অমন চারিদিক উচ্চকিত করে প্রকম্পিত হাসি হাসতে পারতেন, বা অন্যকেও হাসিয়ে হাসিয়ে ক্লান্ত করে দিতে পারতেন, তা যেন না দেখলে বিশ্বাস করাই যায় না।’’
হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি খাতা! আর তাতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। সময় নষ্ট না করে বিশেষ দলও তৈরি করে ফেলেছিল কলকাতা পুলিশ। তার পর তন্নতন্ন করে খোঁজা শুরু হয়েছিল কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায়। শেষ পর্যন্ত এক পুরনো বইয়ের দোকান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল কয়েকটি খাতা। কিন্তু তা-ও সব ক’টা নয়! বইয়ের দোকানদারের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ পৌঁছে গিয়েছিল বইপাড়ারই এক মুদিখানার দোকানে। সেখানে গিয়ে দেখা গিয়েছিল, হারানো খাতার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে তৈরি ঠোঙায় সর্ষে বিক্রি করছেন ওই মুদিখানার দোকানদার! তিনি জানিয়েছিলেন, সাত কিলো ওজনের ওই রদ্দি কাগজপত্র তিনি কিনেছিলেন সাড়ে ১২ টাকায়! শেষ পর্যন্ত যেটুকু অক্ষত ছিল, উদ্ধার করা হয়েছিল তা। যিনি খাতা হারানোর অভিযোগ করেছিলেন, হারানো জিনিস উদ্ধারের খুশিতে পুলিশকর্তাকে নিজের বাবার লেখা একটি বই উপহার দিয়েছিলেন। বইয়ের নাম ‘রূপসী বাংলা’, কবির নাম জীবনানন্দ দাশ। বইয়ের উপরে লেখা ছিল, ‘কৃতজ্ঞতার সাথে মঞ্জুশ্রী দাশ।’ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ সাল।
৩৮ বছর আগের সেই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে তৎকালীন ডিসি ডিডি (২) ও প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন গবেষক ও সংবাদমাধ্যম কে জানিয়েছিলেন, ‘‘জীবনানন্দ দাশের প্রথম জীবনের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি খোয়া গিয়েছে বলে আমাদের জানিয়েছিলেন তাঁর মেয়ে মঞ্জুশ্রীদেবী। যত দূর মনে পড়ছে, তিনি মেচেদা থেকে লোকাল ট্রেনে ফিরছিলেন। ট্রেনের বসার সিটের তলায় রাখা সুটকেসেই জীবনানন্দের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ছিল। অনেক খাতা ছিল। যখন হাওড়া স্টেশনে নামেন, তখন দেখেন ওই সুটকেসটি নেই। সুটকেসচোর ভেবেছিল গয়না বা টাকাপয়সা আছে। কিন্তু সে সব কিছু না পেয়ে রদ্দি কাগজ হিসেবে বেচে দিয়েছিল। তবে হারানো পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ উদ্ধার করা গিয়েছিল। পুরোটা পাওয়া যায়নি!’’ জীবনানন্দের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির একটা অংশ বাক্স করে আর ফেরত আনা যায়নি। ফলে জানা যায়নি, চিরদিনের মতো হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপিতে আরও কী কী অলৌকিক-শব্দবিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল!
বুকজোড়া বরিশাল আর পায়ে কলকাতার উন্মুত্ত প্রান্তরের ঘ্রাণ। শহরের ‘অবিশ্বাসী’ ট্রামলাইন তাঁর দু’পা টেনে নেওয়ার আগে পর্যন্ত ওই দুই ভূখণ্ড কখনও একে অপরকে ছাপিয়ে, কখনও পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। জন্ম নিয়েছিল বাংলা কবিতার নির্জনতম, নিভৃত জগতের— জন্ম নিয়েছিল জীবনানন্দ-ভুবন। বাংলা ভাষার অলৌলিক-অপার্থিব শব্দসম্ভার, নির্জনতম শব্দেরা ব্যক্তিগত জীবনে চূড়ান্ত অসুখী, জীবনভর আর্থিক অনিশ্চয়তায় ভোগা, একের পর এক চাকরি ছাড়া, লোকের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে না পারা, সমালোচকদের আক্রমণে ধ্বস্ত এক মানুষকে মাধ্যম করে পেয়েছিল নিজেদের বিস্তার! কিন্তু কোথা থেকে জীবনানন্দ পেয়েছিলেন এই শব্দ সংকেত, এই অনন্ত শব্দস্নাত স্পর্শ? পারিবারিক দিক থেকে কবির সেই নির্জন জগতের সন্ধানে বেরোলে কিন্তু হোঁচটই খেতে হবে। জীবনানন্দের ঠাকুরদা সর্বানন্দ দাশগুপ্ত ছিলেন বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম মুখ। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে বৈদ্যত্বের চিহ্নস্বরূপ তিনি ‘গুপ্ত’ বর্জন করেছিলেন। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে অশ্বিনী দত্তকে হারিয়ে কমিশনারও হয়েছিলেন তিনি। জীবনানন্দের বাবা সত্যানন্দ দাশও ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের এক জন চিন্তক, প্রবন্ধ রচয়িতা, বক্তা, শিক্ষক। মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন সে সময়ের প্রখ্যাত কবি, যিনি রান্না করতে করতেও অনায়াসে কবিতা লিখতে পারতেন। এমনকি, জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ পুজোর আগে বিদ্যালয়ে আবৃত্তি করবেন বলে লিখে ফেলেছিলেন ‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে’র মতো মুখে মুখে ঘোরা কবিতা! জীবনানন্দের বাবা সত্যানন্দেরা ছিলেন সাত ভাই। জীবনানন্দেরা ছিলেন তিন ভাই-বোন। জীবনানন্দই ছিলেন বড়। ভাই অশোকানন্দ নয় বছর ও বোন সুচরিতা ষোল বছরের ছোট ছিলেন। সব মিলিয়ে একান্নবর্তী পরিবার। ফলে পারিবারিক ওই উষ্ণ আবহে জীবনানন্দ কী ভাবে ওই নির্জন ভূখণ্ডের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাতে বিস্ময়ই জাগে।
‘‘কাউকে দেখানোর জন্য নয়, নিজের জন্যই যেন লেখাগুলো লিখতেন। লিখে ট্রাঙ্কভর্তি করে রাখতেন। ছাপাতে দেওয়ার আগে ওখান থেকেই বার করে দিতেন। ছোটবোন সুচরিতা খুব স্নেহের পাত্রী ছিলেন তাঁর। কখনও কখনও তাঁর সামনে তিনি বার করতেন ওই ট্রাঙ্কের লেখা। বাকিরা সেই অর্থে কিছু জানতেনই না। তাঁর জীবদ্দশায় সব ক’টি কাব্যগ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা মিলিয়ে বড়জোর সাড়ে তিনশো লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি ট্রাঙ্কভর্তি সব লেখাই তো তাঁর মৃত্যুর পরে উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলো যেন একটা আলাদা জগৎ,’’ একদা রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে বসে এক সাংবাদিকের কাছে সাক্ষাৎকারে কথাগুলো বলছিলেন অশোকানন্দের পুত্র অমিতানন্দ দাশ। জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য, পুত্র সমরানন্দ, কন্যা মঞ্জুশ্রী অনেক আগেই প্রয়াত হয়েছেন। প্রসঙ্গত, দেশভাগের ক্ষত নিয়ে এ দেশে আসার পরে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের এই বাড়িতেই জীবনানন্দ কিছু দিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে ল্যান্সডাউন রোডের (বর্তমানে শরৎ বসু রোডের) এক ভাড়াবাড়িতে তিনি চলে যান। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের এই বাড়িতেই ট্রাম-দুর্ঘটনার দু’দিন আগে হন্তদন্ত হয়ে এসে জীবনানন্দ জানতে চেয়েছিলেন, সকলে ঠিক আছেন কি না। কারণ, রাস্তায় কার কাছ থেকে যেন শুনেছেন, পরিবারের কারও ট্রাম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সকলে ঠিক আছেন শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।
জ্যাঠামশাইয়ের ‘আলাদা জগৎ’-এর সঙ্গে অমিতানন্দের পরিচয় হয়েছিল ছেলেবেলাতেই। তখন তাঁর বয়স বড়জোর সাত। অশোকানন্দ কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকতেন। সেই সুবাদেই দিল্লিতে যাতায়াত ছিল অমিতানন্দদের। এক বার সপরিবার জীবনানন্দও দিল্লি গিয়েছিলেন। সেই সফরের স্মৃতি রোমন্থন করে অমিতানন্দ বলেছিলেন, ‘‘এক দিন পরিবারের সকলে মিলে ঘুরতে বেড়িয়েছি। মঞ্জুদির (কবিকন্যা) বয়স তখন বছর কুড়ি হবে। আমি বায়না করাতে মঞ্জুদি হাতের বালা বা গলার হার, কী যেন একটা খুলে আমাকে দিয়েছিল। জিনিসটা বেশ ভারী ও দামি ছিল। কিন্তু আমি সেটা কোনও ভাবে হারিয়ে ফেলি। তা নিয়ে মা (নলিনী দাশ) ও জেঠিমা খুব বকাবকি করছেন। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের সে সবে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। যেন এ সব ঘটনা নিয়ে তাঁর কোনও উৎসাহই নেই।’’ অমিতানন্দই জানালেন, জীবনানন্দের যে ছবিটি সমস্ত পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়, তা ওই দিল্লি-সফরের সময়েই তোলা। তুলেছিলেন অমিতানন্দের মা। ‘‘মায়ের তখনকার দিনের একটা বক্স-ক্যামেরা ছিল। তা দিয়েই পারিবারিক গ্রুপ ফোটো তোলা হয়েছিল। জ্যাঠামশাই ধুতির উপরে শার্ট পরতেন। কিন্তু পরে যখন ওই ফোটো ছাপা হয়েছে পত্রপত্রিকায়, সেটা কী ভাবে যেন মেকওভারে পাঞ্জাবি হয়ে গিয়েছে,’’ হেসেছিলেন অমিতানন্দ।
১৮৯৯ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ, ঘনঘন অসুস্থ হয়ে পড়া শিশু জীবনানন্দকে সারিয়ে তুলতে কুসুমকুমারীর লখনউ, আগ্রা-সহ নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, একটু বেশি বয়সেই বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রতিটি বার্ষিক পরীক্ষায় বাঁধাধরা পুরস্কার, তার পর ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯১৭ সালে আই.এ পাশ, ১৯১৯-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে স্নাতক ও পরে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর পাশ করে ১৯২৬ সালে চাকরি জীবনের সূত্রপাত সিটি কলেজে—জীবনের এই মাইলফলক ধরে এগোলে জীবনানন্দের নির্জন-ভূখণ্ডে পৌঁছনোটা প্রায় অসম্ভব! অলৌলিক-ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সন্ধানে বেরোলে পিছিয়ে যেতে হবে সেই ছোটবেলায়। যেখানে বগুড়া মোড়ের বিশাল জায়গা জুড়ে বাড়ি, সেই জমির ঝোপের মধ্যে হলুদ ছোপ পড়া আনারস ফল, কাঁঠালগাছ, আমগাছ, শিশির পড়ার টুপটাপ শব্দ, গভীর রাতে সুপুরি নিয়ে ইঁদুরের লড়াই, মাছ ধরা, ঠাকুমার গল্প, মফস্সলের নদী-খালের মতো বরিশালের সর্বব্যাপী প্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপকরণ, দৃশ্য, মুহূর্তের সঙ্গে ছোটবেলায় তাঁর যে অদৃশ্য, বিনিসুতোর বাঁধন তৈরি হয়েছে, সেই বাঁধন আজীবন তাঁর সঙ্গে চলেছে, সে তিনি যেখানেই যান না কেন! সেই সমস্ত দৃশ্যই হাট করে খুলে দিয়েছে তাঁর কল্পনার দরজা, যার মধ্যে পরবর্তী কালে অনায়াসে প্রবেশ করেছে পারস্য গালিচা, বিলুপ্ত নগরী, নীল সুপুরির বনেরা! বড়মামা ছাদে মাদুর পেতে আকাশের তারাদের চেনাচ্ছেন, জীবনানন্দ বিস্ফারিত চোখে দেখছেন সে সব অগুনতি নক্ষত্র, অসীম- অনন্ত মহাকাশকে, মামাবাড়ির ছাদের উপরের রাতের আকাশ যেন আজীবনের বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিচ্ছে ছোটবেলার জীবনানন্দের সঙ্গে, পরে সেই নক্ষত্রপুঞ্জই ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতার খাতায়। শব্দের পরে শব্দে, দূরতম নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আলো এসে পড়ছে যেন, আর তাতে ভেসে যাচ্ছে আকীর্ণ চরাচর! শুধু কি প্রকৃতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক, তারও তো হাতেখড়ি সেই বরিশালেই। যেখানে অবশ্যম্ভাবী ভাবে চলে আসেন ফকিরের মতো দরিদ্র চাষি বা সকালে প্রতিদিন বাড়িতে দুধ দিতে আসা প্রহ্লাদের মতো মানুষেরা। বর্ষাকালে উঠোনে বড় ঘাস জন্মেছে। সত্যানন্দ ফকিরকে ডেকেছেন সেই ঘাস কাটার জন্য। ফকির কাস্তে চালিয়েছেন আর তাতে কাতর হয়েছেন জীবনানন্দ। তখন ফকির তাঁকে বুঝিয়েছেন, ‘‘চিন্তা করবেন না দাদাবাবু। এর পরেই কচি, সবুজ, নতুন ঘাস হবে।’’ কে বলতে পারে, ‘আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে গেলাসে পান করি,’ এই লাইনটি লেখার সময়ে বাল্যকালের সেই মুহূর্ত তাঁর মনের উপরে ছাপ ফেলেনি। তখন ফকির ঘাস কাটতে কাটতে তাঁকে শোনাননি মাটির কথা, ফসলের কথা! বা বাড়িতে দুধ দিতে আসা প্রহ্লাদ দাঁড়িয়ে পড়েছেন, নড়ছেন না। জীবনানন্দ তখন ইংরেজিতে বা বাংলায় হয়তো কোনও কবিতা আবৃত্তি করছেন। পড়া শেষ হলে প্রহ্লাদ তাঁকে বলছেন, ‘আপনি বড় ভাল পড়েন দাদাবাবু।’ যদিও সে কবিতার অর্থ বুঝতে পারার কথা নয় প্রহ্লাদের, কিন্তু সেই শব্দধ্বনিই মুগ্ধ করেছিল তাঁর মতো মাটির কাছের মানুষকেও। মাটি-প্রকৃতি-মানবমনের সঙ্গে তাঁর যে সখ্য, সেই বন্ধুত্ব তাঁর আজীবনের সঙ্গী, সম্বল, সম্পদ। কিন্তু পরে যখন দেখেছেন তাঁর নিজস্ব মনন ক্ষেত্রের সঙ্গে বাইরের জগতের কোনও মিল নেই, তখন তিনি গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে, একটা বর্ম তৈরি করেছেন! অথচ এক বার সে বর্ম ভাঙতে পারলেই তিনি তাঁর কাছে সহজ মানুষ। অনেকে হয়তো বাড়িতে এসেছেন, বাথরুম ফাঁকা পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার বাথরুম কি ফাঁকা আছে?’ তাঁর সহাস্য উত্তর, ‘দিল্লির মসনদ কি কখনও ফাঁকা পড়ে থাকে!’ বা যখন সজনীকান্ত দাস তাঁর কবিতার ভাষার শ্লীলতা, অর্থ, বোধ নিয়ে শনিবারের চিঠিতে বেআব্রু আক্রমণে নেমেছেন, কখনও লিখেছেন, ‘গণ্ডারমারী কবিতা’ লিখেছেন জীবনানন্দ, আবার কখনও লিখেছেন, জীবনানন্দের লেখা ‘নির্জন পেঁচার মতো প্রাণ যদি অলৌলিক না হয় তা হলে সীতার পাতাল প্রবেশও অলৌলিক নয়।’ আর তাঁর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে আসরে নেমেছেন বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং। সজনীকান্ত-বুদ্ধদেবের পারস্পরিক কাব্য-দ্বৈরথের উত্তপ্ত আবহেও জীবনানন্দ স্মিত হেসে বলেছেন, ‘সজনীকান্তবাবু তো আমার ভালই প্রচার করছেন।’
আসলে বোধহয় জীবনানন্দ চাইতেন না তাঁর ভিতরের নির্জন স্থানটি কোনও ভাবে উপদ্রুত হোক, যেখানে আস্তে আস্তে জন্ম নিচ্ছে ‘ঝরা পালক’, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’, ‘বনলতা সেন’, ‘মহাপৃথিবী’, ‘রূপসী বাংলা’র কবিতারা। কিন্তু সেই নির্জন ভূমিই প্রথম টাল খেল সিটি কলেজে। কর্মজীবনের পাশাপাশি সাহিত্য পত্রপত্রিকায় লেখার শুরু মোটামুটি এই সময়েই। ১৯২৭ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ প্রকাশিত হল। শুরু বিতর্কেরও। তাঁর কবিতায় অশ্লীলতা আছে— এই অভিযোগে তাঁর সিটি কলেজের চাকরি যায়, এমন একটা বহুল প্রচারিত মত আছে। ‘‘আদৌ ব্যাপারটা তা নয়। কলেজে সরস্বতী পুজো নিয়ে একটা গোলমাল হয়েছিল। ছাত্ররা পুজো করতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্ম কলেজে কেন পুজো হবে, আপত্তি ছিল কলেজ কর্তৃপক্ষের,’’ বলছিলেন অমিতানন্দ। সেই সময়েই জীবনানন্দকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর মত কী? পুজো হলে ক্ষতি কোথায়, এমনই নিরাসক্ত জবাব দিয়েছিলেন তিনি! ব্রাহ্ম হিসেবে চাকরি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন কলেজের সপক্ষে কথা বলেননি, তাতেই অসন্তুষ্ট হন কর্তৃপক্ষ। তার পর কলেজের ছাত্র সংখ্যা কমে গেলে অনেক জুনিয়র অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁরও চাকরি গিয়েছিল, জানিয়েছিলেন অমিতানন্দ। আসলে ব্রাহ্ম-আবহে বড় হয়ে ওঠা জীবনানন্দ প্রথম দিকে ব্রাহ্ম সমাজ নিয়ে কবিতা, প্রবন্ধ লিখলেও পরে আর সেই জগতের কাছে ফেরত যাননি। কারণ, তত ক্ষণে জীবনানন্দের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল ধানসিড়ি নদী, নীল হাওয়ার সমুদ্র, শব্দহীন জ্যোৎস্নারা! আর জন্মেছিলেন বনলতা সেন। কিন্তু কে এই বনলতা সেন? অমিতানন্দ জানিয়েছিলেন, ‘‘আমরা যেটুকু শুনেছি তিনি জীবনানন্দের এক খুড়তুতো বোন ছিলেন। তাঁর প্রতি দুর্বল ছিলেন উনি। কিন্তু সম্পর্ক গড়ার সাহস পাননি। তাঁর ছায়াতেই তিনি বনলতা সেন লিখেছিলেন বলে পরিবারের বড়দের মুখে যতটুকু শুনেছি।’’ আবার জীবনানন্দের ডায়রিতে ‘ওয়াই’ বর্ণ সংকেতে এক নারীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। টীকায় সম্পাদক কবি-গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ জানিয়েছিলেন, এই ‘ওয়াই’ জীবনানন্দের খুড়তুতো বোন বুলুর (কমলা দাশগুপ্তের) বান্ধবী। বরিশালেই তাঁকে চিনতেন জীবনানন্দ। অন্তত ১৯৩১-৩২ পর্যন্ত তিনি অনেকখানি মন জুড়ে আছেন জীবনানন্দের। তিনিও বনলতা হতে পারেন। আসলে বনলতা কে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সব সময়েই মুচকি হেসেছেন জীবনানন্দ। কোনও উত্তর দেননি।
সামগ্রিক কর্মজীবনে পাঁচটিরও বেশি কলেজে কাজ করেছেন জীবনানন্দ। এ যেন এক বিপন্ন বিস্ময়, যা তাঁকে স্থিত হতে দেয়নি। যার সূত্রপাত সিটি কলেজে কাজ যাওয়ার পরপরই। কলকাতায় থাকতে এক দিকে তিনি সমসাময়িক বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-র চেয়ে বয়সে বড়। কিন্তু তখনও তাঁর কবিতা পত্র-পত্রিকা থেকে ফেরত আসে, নতুন কবিতা সংকলনে তাঁর নাম ছাপা হয় না। অন্য দিকে ব্যক্তিগত, আর্থিক জীবনেও অনিশ্চয়তা। ভাল না লাগায় ১৯২৯ সালে বাগেরহাট কলেজের চাকরি ছেড়ে দেন। সেখান থেকে দিল্লি। ১৯৩০ সালের মে মাস পর্যন্ত তিনি দিল্লিতে ছিলেন। তার পর বিয়ে করতে বরিশালে এসে আর দিল্লি যাননি। অমিতানন্দের কথায়, ‘‘বিয়ের কয়েক মাস আগে চাকরিটা ছেড়ে দিলেন হঠাৎ। তখন থেকেই তাঁর দাম্পত্য জীবনে সঙ্কট শুরু হয়। যা আর কখনও মেটেনি। জেঠিমা সুন্দরী ছিলেন, শিক্ষিতা ছিলেন, গানও ভাল গাইতেন। কিন্তু তিনি সেই এক্সপোজ়ারটা পাননি। দাম্পত্য জীবনে খামতি থাকার জন্য ছেলে-মেয়েকে খুব প্রশ্রয় দিতেন। ক্ষতিটা হয়তো পুষিয়ে দিতে চাইতেন।’’ অসুখী দাম্পত্য ফুটে উঠেছে তাঁর লেখা একাধিক উপন্যাসেও। অমিতানন্দের খুঁজে পাওয়া একটি ডায়রিতেও দেখা গেল সেই অস্থির জীবনের ছায়া। সেখানে লিখছেন এক জায়গায়, ‘বাড়িতে থাকতে রোজি সন্ধ্যার পর ভাবতাম একটু অন্ধকারে থাকা যাক—জ্যোৎস্না বা লম্ফের আলোতে—কিন্তু একটা না একটা কারণে রোজি আলো জ্বালতে হত—তারপর মেসে চলে গেলাম সেখানে roommateদের জন্য আলোর ব্যবস্থা না হলে চলত না—’ আবার আরেক জায়গায়, ‘চিরদিন দুঃখ ভোগ করে যাওয়াটাই তো জীবনের উদ্দেশ্য নয়…’
ব্যক্তিগত জীবনে ত্রস্ত ছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু কোথাও তাঁর একটা স্থির বিশ্বাসের ভরকেন্দ্রও ছিল! হয়তো সে বিশ্বাসে শাণিত তরবারির স্পর্ধা ছিল না। কিন্তু সে বিশ্বাস ছিল ফসলসম্ভবা মাটির মতো নরম অথচ ঋজু। না হলে তাঁর বিরুদ্ধে যখন লাগাতার ধূসর, পলায়নকারী মানসিকতা, দুর্বোধ্য, বিশেষণগুলি (নেতিবাচক অর্থেই) ক্রমাগত ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন কেন বলবেন, ‘‘আত্মঘাতী ক্লান্তি’ আমার কবিতার প্রধান আবহাওয়া নয়…’ অথবা ‘ক্যাম্পে’ কবিতার অশ্লীলতার অভিযোগ নিয়ে কেন লিখবেন, ‘যদি কোনো একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তা জীবনের— মানুষের-কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তার সুর।’ কর্মজীবন টালমাটাল হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি নির্দ্বিধায় বলবেন, ‘যে জিনিস যাদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সবই অসাড়তার নামান্তর নয় কি?’ এই উচ্চারণের জন্য তো স্পর্ধা লাগে, সাহসও। যেমন ভাবে বিশ্বাস লাগে এই সারসত্যটুকু বলতে, ‘সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।’ এই নিষ্কম্প বিশ্বাস তাঁর কলকাতার উপরেও ছিল। এমনিতে ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবন, ১৯৩৫ সালে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার আগে এবং আবার কলকাতায় ফেরা পর্যন্ত, এ শহরে তাঁর আবাস-মানচিত্রে ছিল কখনও মেস, কখনও অশোকানন্দের বাড়ি, কখনও ল্যান্সডাউনের ভাড়াবাড়ি। কর্মজীবনে টালমাটাল মুহূর্তে অন্য জায়গায় চাকরির সুযোগ হচ্ছিল, কিন্তু তবু তিনি যাচ্ছিলেন না বলে জানিয়েছিলেন অমিতানন্দ। তাঁর কথায়, ‘‘অসমে, পঞ্জাবে ও অন্যত্র চাকরি হলেও কলকাতা ছেড়ে যেতে রাজি ছিলেন না!’’ দেশভাগের পরে কলকাতায় এসে বন্ধু সঞ্জয় ভট্টাচার্যের চেষ্টায় ‘স্বরাজ’ নামে একটি নতুন দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগটি সম্পাদনার কাজ পেয়েছিলেন। ‘স্বরাজ’ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ১৯৫০ সাল নাগাদ কিছু দিন খড়্গপুর কলেজে কাজ করছিলেন। সেখান থেকে শহরে ফিরে কখনও বড়িশা কলেজ, ডায়মন্ড হারবারের ফকিরচাঁদ কলেজ, হাওড়া গার্লস কলেজে কাজ করেছেন। আর শহর ছেড়ে যাননি! এ শহরও তখন তাঁকে আস্তে আস্তে চিনছে। তত দিনে ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’, ‘বনলতা সেন’, ‘মহাপৃথিবী’, ‘সাতটি তারার তিমির’, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ প্রকাশিত হয়েছে (যদিও সব মিলিয়ে অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছে তখনও দেড় হাজারেরও বেশি কবিতা, উপন্যাস, গল্প)। স্বীকৃতি পাচ্ছেন তিনি, জুটেছে পুরস্কারও। তারও আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসায় আপ্লুত হয়েছেন তিনি, আর বুদ্ধদেব বসুর মতো যাঁরা ভাষাবিন্যাসে অচলায়তন ভাঙার সমর্থক, তাঁদের কাছে তিনি তো তখন রীতিমতো আবিষ্কার! তাই শহরের সমস্ত সাহিত্য আলোচনায়, কবিতাপাঠে তিনি আমন্ত্রিত।
কিন্তু তার পর সে দিন! ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর। আগের দিনই রেডিয়োয় ‘মহাজিজ্ঞাসা’ কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। তা নিয়ে সে দিন সকালে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। তার পর প্রতি দিনের মতো ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি থেকে বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই হাঁটা যে তাঁর অভ্যেস। ও পার বাংলায় বাল্যকালের সেই স্টিমারের জেটি। কিছুটা দূরে ঝাউয়ের সারি। লিচু, অজস্র ফুল-ফল সমারোহে বিশাল কম্পাউন্ড নিয়ে ব্রাউন সাহেবের কুঠি। সে সব পার হয়ে ব্রাহ্ম সমাজ সার্কিট হাউসের গির্জা, তা ছাড়িয়ে গেলে শ্মশানভূমি, লাশকাটা ঘর। সে সব পথ হাঁটতে হাঁটতে আকাশে মেঘ দেখে বালক জীবনানন্দ ভাইকে বলতেন, তিনি একটা মনপবনের নৌকা তৈরি করবেন। সে দিনও কি জীবনানন্দ আকাশে মেঘ দেখে মনপবনের নৌকার কথা ভাবছিলেন? না হলে কেন ট্রামের অবিরাম ঘণ্টা বাজানোর আওয়াজ, ট্রাম চালকের চিৎকার শুনতে পাবেন না তিনি! ট্রামের ধাক্কায় গুরুতর জখম জীবনানন্দকে রাস্তা থেকে তুলে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলেন অপরিচিতেরা। সেখানেই আট দিনের লড়াই।
মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ উক্তি ছিল, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপির রং সারাটা আকাশ জুড়ে’।
‘‘সেই ট্রামটি এখন আর নেই! এক সময়ে আগুন লেগেছিল। তাতেই পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল ট্রামটি। তবে কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে বনলতা নামে একটা হেরিটেজ ট্রাম চালু হয়েছে,’’ পরে সংবাদমাধ্যম কে জানিয়েছিলেন পরিবহণ দফতরের প্রাক্তন পদস্থ কর্তা। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, বহুল আলোচিত ওই ‘নকড ডাউন’-এর কোনও তথ্য এখন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর!
নেমেসিস? হবে হয়তো। না হলে কবির ‘ঘাতক’ ট্রাম নিজেই আগুনে কেন ভস্মীভূত হবে!
শহরের প্রাণঘাতী ট্রামলাইনে তাঁর পথ হাঁটা থেমেছিল, আবহমানের শব্দস্রোত থামেনি!
‘সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী’, কিন্তু হয়তো সেই আবহমানের খোঁজে বেরিয়েই জীবনানন্দ আর ফেরেননি! বাংলা কবিতার নির্জন চরাচর ধরে জীবনানন্দ হেঁটে গিয়েছেন দূরে, দূরতম দ্বীপে, একাকী, নিঃসঙ্গ অবস্থায়। তাঁর গা থেকে খসে খসে পড়েছে বাংলা কবিতার অবিশ্বাস্য সব লাইন, অসম্ভব সব শব্দ। তার পর সে সব শব্দ মিশে গিয়েছে আলপথে,
মাঠের ধারে, ধানসিড়ি নদীর কিনারে। আর তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন এ বাংলায়, দুই বাংলার বিস্তীর্ণ চরাচরে— মাটির ভিতর মাটি হয়ে, ফসলের ভিতর ফসল হয়ে, পাখির ভিতর পাখি হয়ে…
জীবনানন্দের যাবতীয় রচনার সাক্ষ্যে একটা ভয় কিন্তু থেকে যায়। তা হল আত্মজীবনীটা লিখে ফেললেও নিজের witty, কৌতুকপ্রিয় সত্তাটাকে সেখানে মেলে ধরতেন কিনা। এখানেও তুলনাটা এসে পড়ে অন্য নির্জন কবি কিটসের। যাঁর চরিতের জীবনোচ্ছল ছবিগুলোর জন্য নির্ভর করতে হয় সমসাময়িক ও জীবনীকারদের বৃত্তান্তে। আমাদের সৌভাগ্য জীবনানন্দের এরকম একজন ছিলেন অরবিন্দ গুহ, যিনি অগ্নিমিত্র নামে চমৎকার রসরচয়িতা হয়েছিলেন পরে। তাঁর বর্ণিত জীবনানন্দের কতিপয় রসিক ছবির একটি দিয়ে শেষ করব।—
‘‘সিনেমায় গান লেখার ব্যাপারে একদা জীবনানন্দ কিঞ্চিৎ আগ্রহী হয়েছেন, তিনি আমাকে এক দিন জিজ্ঞেস করলেন— সিনেমায় গান লিখলে নাকি অনেক টাকা পাওয়া যায়? তুমি কিছু জানো এ বিষয়ে? আমি জানি না এমন কোনো বিষয় জগতে নেই, আমি সর্বজ্ঞ— আমার নিজের মতে। সর্বজ্ঞের গলায় বললাম— হ্যাঁ, আমিও শুনেছি সিনেমায় গান লিখলে অনেক টাকা পাওয়া যায়। তিনি বললেন— আমি লিখতে পারি না? বললাম— নিশ্চয়ই পারেন। —আমাকে কী করতে হবে? —বাংলা সিনেমার পরিচালক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের খুব নামডাক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন? জীবনানন্দ বললেন— খুব ভালো, বললাম— তা হলে আর কী কথা? তাঁকে বলুন। উনি অনায়াসে একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। দিন কয়েক বাদে আবার রাসবিহারী এভিনিউতে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম— প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা করেছিলেন? জীবনানন্দ বললেন— না, এ বার করে ফেলব। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করেছি— সর্বজ্ঞের অনেক দায়। আবার রাসবিহারী এভিনিউতে দেখা। বললাম— প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে…। জীবনানন্দ বললেন— না, এখনও ঠিক হয়নি, কিন্ত এ বারে আর দেরি করব না। বললাম— থাক, এ ব্যাপারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন? জীবনানন্দ বললেন— খুব ভালো। আমি তুড়ি মেরে বললাম— তা হলে আর কথা নেই। ওঁকে বলুন সিনেমার ডিরেক্টর হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের চেয়ে ওঁর দাপট অনেক বেশি। তা ছাড়াও একটা কথা আছে। জীবনানন্দ আগ্রহী হলেন— কী কথা?বললাম— প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই সিনেমার গান লেখেন, কিন্তু শৈলজানন্দ নিজে সিনেমার গান লেখেন না। এই অবস্থায়… আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে জীবনানন্দ বললেন— বুঝেছি, আর বলতে হবে না। আমি শিগগিরই শৈলজাকে বলব। — ঠিক আছে।
দশ-বারো দিন বাদে আবার রাসবিহারী এভিনিউতে এক দিন। নির্ঘাত শৈলজানন্দের সঙ্গে কথা বলেছেন? জীবনানন্দ বললেন— না, তোমার সঙ্গে কথা আছে।
বলে আমাকে নিয়ে গেলেন ফুটপাথের এক পাশে। সেখানে সাবধানে গোপন কথা বললে আর কারও শোনার আশঙ্কা কম। বললেন— শৈলজার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলিনি কেন জান? বললাম— না। কেন? খুব হতাশভাবে বললেন— যদি শৈলজা আমার জন্য কোথাও একটা ব্যবস্থা করে দেয় তা হলেও আমি কেমন করে লিখব, ‘রাধে-এ-এ-এ ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়’। এখনো আমার মনে গেঁথে আছে চোখমুখের সকৌতুক ভঙ্গির সঙ্গে জীবননান্দের গলায়— রাধে-এ-এ-এ… বলা বাহুল্য হলেও বলা দরকার, ইহজন্মে সিনেমার গান লেখার সৌভাগ্য জীবনানন্দের হয়নি,’’
মৃত্যুশয্যায় এই জীবনানন্দকে দেখে অরবিন্দর মনে হয়েছিল যেন নীচের ঠোঁট কামড়ে দুরন্ত হাস্যস্রোতকে ঠোঁটের ওপারে বন্দি করে রেখেছেন। হয়তো খানিক আগেই সেই নিজস্ব হাসি হেসেছেন। নাকি একটু পরেই হেসে উঠবেন প্রচণ্ড শব্দে?
(তথ্যসূত্র:
১- অনন্য জীবনানন্দ: জীবনান্দ দাশের সাহিত্যিক জীবনী, ক্লিন্টন বি সিলি, প্রথমা প্রকাশন (২০১৮)।
২- আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার ও অন্যান্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিভাস (২০১৫)।
৩- জীবনানন্দ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দে’জ পাবলিশিং (১৯৮৯)।
৪- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪শে জানুয়ারি ২০১৫ সাল।
৫- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ সাল।
৬- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩শে জানুয়ারি ২০১৬ সাল।
৭- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩শে জানুয়ারি ২০১৬ সাল।)
মতামত লেখকের ব্যক্তিগত